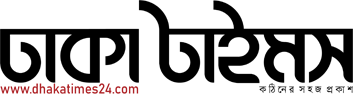আমার জীবনে চাহিদা বলে কিছু নেই-২
প্রকাশ | ২৬ জুন ২০১৭, ১১:৩৯ | আপডেট: ২৬ জুন ২০১৭, ১৪:৩৮

শিমূল ইউসুফ। অভিনয় জগতে অসামান্য দ্যুতি ছড়ানো এক নাম। বাংলা নাটকের প্রবাদ পুরুষ সেলিম আল দীন তাকে বলেছিলেন ‘একালের মঞ্চকুসুম’। ঢাকাটাইমস ও সাপ্তাহিক এই সময়ের সঙ্গে এক দীর্ঘ আলাপচারিতায় তার বেড়ে ওঠা, স্বাধীনতার সংগ্রাম ও সমসাময়িক সাংস্কৃতিক আবহ, মুক্তিযুদ্ধের সময়কার পারিবারিক নানা সংকট, নিজের ও স্বামী নাসির উদ্দিন ইউসুফের কর্ম, একাত্তর থেকে এ যাবৎকালের মঞ্চ ও চলচ্চিত্রের নানা বিষয় মেলে ধরেছেন। আজ দ্বিতীয় পর্ব। আলাপচারিতায় ছিলেন প্রধান প্রতিবেদক হাবিবুল্লাহ ফাহাদ।
আপনারা সবাই একসঙ্গে ছিলেন। সেই সময়কার কোনো স্মৃতি কি মনে পড়ে?
পিয়ামণির (ঝিনু আপার) বাবু হবে- আমি পেটে কান দিয়ে শোনার চেষ্টা করতাম বাবুটা আমার সঙ্গে কথা বলে কি না। বলত না। আমার ভাই দীনু একটা বানর পুষত। মা ও ভাইয়া ঠিক করলেন বানরটাকে চিড়িয়াখানায় দিয়ে আসবে; কারণ সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে ঝিনু যদি বানরের মুখ দেখে তাহলে সন্তানের চেহারা যদি বানরের মতো হয়? বানরের বিদায় হলো মিষ্টির (দীনু বিল্লাহ) অনেক চোখের জলের মধ্যে। শাওন এত সুন্দর হয়েছে যে আমার কন্যা এশা, শাওনের সৌর্ন্দযে মুগ্ধ হয়ে আধফোটা কথা বলা এশা, ওর নাম বলল ‘সুন্দর’। এখন আমরা সবাই শাওনকে ‘সুন্দর’ নামেই ডাকি।
ভাইয়া পিয়ামণিকে অনেক ভালোবাসতেন। সন্তানসম্ভবা অবস্থায় পিয়ামণি একদিন পাশের বাসা থেকে এক বোতল ঠা-া পানি এনে পান করছিল। তখন সব ঘরে ঘরেই ফ্রিজ ছিল, আমাদের ছিল না। ভাইয়া দুপুরে খেতে এসে এ দৃশ্য দেখলেন। তারপর সন্ধ্যায় একটা ফ্রিজ কিনে আনলেন। পিয়াকে আর অন্যের বাড়ি থেকে যেন ঠা-া পানি চেয়ে খেতে না হয়।
৬ আগস্ট শাওন হলো হলি ফ্যামিলি হাসপাতালে। রাত সাড়ে দশটার দিকে। ভাইয়া মায়ের পেছনে শিশুর মতো লুকিয়ে আছে আর বলছে, ‘মামণি আপনি আগে দ্যাখেন, আমার মতো কালো হয়নি তো? ঝিনুর মতো রং পেয়েছে কি না, আগে দ্যাখেন।’ মা শাওনকে দেখে ভাইয়াকে বলল, ‘ঝিনুর চেয়েও সুন্দর হয়েছে তোমার মেয়ে আলতু।’ মা ভাইয়াকে আদর করে আলতু ডাকতেন।
মেয়েকে ঘিরেও শহীদ আলতাফ মাহমুদের অনেক স্মৃতি আছে। আপনি বিভিন্ন সময় বলেছেন...
শাওন তখন দুই আড়াই বছরের হবে-পাশের বাড়ি জামগাছে জাম ধরেছে। জামগুলো ভালো করে পাকেনি কিন্তু শাওন খাবেই। বাড়ির মালিক বলেছিল, ‘জাম পাকলে খেয়ো’। ভাইয়া বাসায় ফিরে এসে দেখল শাওন জাম খাওয়ার জন্য বায়না করছে। ভাইয়া গাড়ি নিয়ে বাজারে গিয়ে গাড়ির বনেটে ভরে এক ঝুড়ি জাম নিয়ে হাজির। মা বলছিলেন, ‘এত জাম কেন আনলে আলতু, সব তো নষ্ট হবে। কটাই বা শাওন খাবে? ভাইয়া বলেছিলেন, ‘পাড়া-প্রতিবেশীর বাড়ি দিয়ে দেন, আমার মেয়ে জাম খেতে চেয়েছে, আমি তো আর আধাসের জাম নিয়ে আসতে পারি না- ওকে জামের ঝুড়ির ওপর বসিয়ে দেন, দেখি ও কত খেতে পারে’।
তিনি আপনাদের বড় ভাইয়ের মতোই পরিবারে মিশেছিলেন।
হ্যাঁ। খুব আপনজন ছিলেন। ভাইয়া বাজার করতে খুব ভালোবাসতেন। প্রায়ই আরিচা ঘাটে চলে যেতেন গাড়ি নিয়ে। নানা রকমের মাছ, সবজি বোঝাই করে নিয়ে আসতেন- তারপর বিলানো হতো বাড়ি বাড়ি। ভালো খেতে খুব ভালোবাসতেন তিনি। মায়ের হাতের চিংড়ি মাছের মালাইকারী খুব পছন্দের ছিল তার। তিনি চলে যাওয়ার পর মা আর কোনোদিন চিংড়ি মাছের মালাইকারী বাসায় রান্না করেননি। আমিও আর কোনোদিন এই ৩৪ বছরে একবারও ছুঁয়ে দেখিনি চিংড়ি মাছের মালাইকারী। মা শিং মাছ, মাগুর মাছ ও মুরগি খেতেন না। তবে ভাইয়ার জন্য খুব যতœ করে শিং মাছ ও মাগুর মাছ রান্না করতেন। মা খেতেন না বলে আমরা তিন বোনও ওই মাছগুলো খেতাম না। খাবার টেবিলে বসে ভাইয়া কয়েক দিন এ ব্যাপারটা লক্ষ করেছেন। তারপর একদিন দুপুরে আমরা সবাই খেতে বসেছি ভাইয়া মাকে বললেন, ‘মামণি আপনিও আমাদের সঙ্গে খেতে বসে যান অনেক বেলা হয়ে গেছে’। মা তখনও জানতেন না এরপর ভাইয়া কী করতে যাচ্ছেন। প্রথমইে ভাত বেড়ে দিলেন মা সবার পাতে। এরপর ভাইয়া শিং মাছের তরকারির বাটিটা নিয়ে বললেন, ‘মামণি আপনার থালাটা দেন আমি আপনাকে তরকারি বেড়ে দিচ্ছি’। মা যতই বলেন, ‘না আলতু তুমি আগে নাও আমরা পরে নেব।’ ভাইয়া ততই জেদ করে মাকে বলেন, ‘শোনেন মা, আমি জানি আপনি এ মাছ খান না, কিন্তু কেন বলেন? এত ভালো মাছ আপনি খান না বলে ঝিনু, মিনু, শিমূল ওরাও খায় না। এটা কি ঠিক? মুরগির কথা আজ বাদ দিলাম। আজকে আপনি যদি শিং মাছ না খান, তবে আমিও ভাত খাব না।’ মা, আমরা তিন বোন চুপ করে বসে আছি। তখন ভাইয়া নিজেই ভাত মেখে আমাদের সবার মুখে নলা তুলে দিল। মা এবং আমরা কোনোমতে পানি দিয়ে তাই গিললাম।
তার কাছে আপনি গান শিখেছেন বলছিলেন। শিক্ষক হিসেবে তিনি কেমন ছিলেন?
তিনি আমার পিতাসম, তিনি আমার শিক্ষক, আমার গুরু। সকালে যদি কোনোদিন গলা না সাধতাম, সেদিন ভাইয়ার সামনে যেতে পারতাম না ভয়ে। কেন রেওয়াজ করিনি বা কোনোদিন হয়তো স্কুলে যেতে দেরি হবে ভেবে তাড়াহুড়া করে রেওয়াজ শেষ করেছি। সেদিনও ভয় এই বুঝি দরজা খুলে এসে সামনে দাঁড়াবে। আর সুর থেকে বিচ্যুত হলে তো কথাই নেই। দড়াম করে দরজা খুলে বেরিয়ে এসে একবার শুধু বড় বড় চোখ দুটো আরও কঠিন এবং রাগ নিয়ে দাঁড়াতেন। আমার কণ্ঠ দিয়ে তখন আর কোনো আওয়াজই বের হতো না ভয়ে।
সেই মূর্তিতে তখন কোনো ক্ষমা থাকত না। কোনো আদর থাকত না। কঠিন দৃষ্টি। যারা তাকে কাছে থেকে দেখেছেন এবং জানেন তারা নিশ্চয়ই আমার অবস্থা বুঝতে পারবেন। আবার এমনও অনেক সময় গেছে তিনি ঘরে বসে সুর করছেন, আমি দরজার পাশেই ঘুরঘুর করছি। আমাকে ডেকেই জিজ্ঞাসা করছেন, ‘কেমন হলো বল তো?’ পুরো গানের সুর হয়ে গেলে মাকে বসিয়ে শোনাতেন। মাকেও জিজ্ঞাসা করতেন কেমন হলো মামণি? ‘মনে পড়ে’, ‘হাজার তারের বীণা’, ‘রাজপথ জনপথ’, ‘বাদল বরিষণে’- এই গীতনাট্যের সুর ও সংগীত পরিচালনা করার সময় আমি তার খুব কাছাকাছি ছিলাম।
অনেক গান প্রথমে আমিই তুলে রাখতাম। কারণ ভাইয়া সুর করে যখন মিউজিক কম্পোজ করতেন তখন মূল গানটা আমি গাইতাম। তিনি কর্ডগুলো বের করতেন। ‘এই ঝঞ্ঝা মোরা রুখবো’, ‘আমি মানুষরে ভাই স্পার্টাকাস’Ñ এই দুটো গণসংগীতের সুর করার সঙ্গে সঙ্গেই আমি গলায় তুলে নিয়েছিলাম।
তিনি বাদ্যযন্ত্র ভালো বাজাতে পারতেন বলে শুনেছি...
ভাইয়া যখন ঘরে বসে সুর করতেন তখন আমার মায়ের নির্দেশে পুরো বাড়ি পিনপতন নিস্তব্ধ থাকত। এমনকি ছোট্ট শাওনকেও আমরা আমাদের ঘরে নিয়ে এসে ঘুম পাড়াতাম। যদিও শাওন ছোটবেলা থেকেই খুব লক্ষ্মী ছিল। একদম কান্নাকাটি করত না। ভাইয়া যে কি ভালো সরোদ বাজাতে পারতেন, তা অনেকেরই অজানা। বেহালা, সরোদ, বাঁশি, গিটার, তবলা, পিয়ানো, যাইলোফোন, ভাইব্রোফোন, আরও কত রকমের পারকের্শন বাজাতে পারতেন। এ যন্ত্রগুলো তার সংগ্রহে ছিল। স্বাধীনতার পর কিছুই আমারা ফেরত পাইনি যাদের কাছে এগুলো ছিল। কিছু বাসা থেকেও লুট হয়েছে। পুরোনো লং প্লে-রেকর্ড সংগ্রহ করা তার নেশা ছিল। বিখ্যাত সব কম্পোজারদের কম্পোজিশন ছিল তার সংগ্রহে। শুধু তানপুরাটা হাদী ভাইয়ের কাছে আছে। তিনি সেটাকে যতœ করেন তার সন্তানের মতো। তবুও একবার স্পর্শ করে দেখতে ইচ্ছা করে নিজের হাতে। মন বলে ভাইয়ার লম্বা লম্বা আঙুলগুলো এখনো বোধহয় ওই তারগুলোকে ছুঁয়ে যায়।
অনেক মজার স্মৃতি আছে আপনার ভাইয়ার সঙ্গে। বিভিন্ন প্রসঙ্গে বলেছেন। তার কিছু কি এখন মনে পড়ছে?
আমার একটা কুকুর ছিল। ওকে আমি কমলাপুর বৌদ্ধমন্দির থেকে এনেছিলাম। ওর নাম ছিল ‘কিলার’। তার আবার অদ্ভুত অভ্যাস ছিল। সে কাকাবাবু (বিশুদ্ধনন্দ মহাথেরো), শুদ্ধানন্দ ভান্তে যখন আমাদের বাসায় আসতেন, তখন সারাক্ষণ ওনাদের সঙ্গে থাকত। ওনারা চলে গেলে আমার সেই কিলারও হলুদ কাপড়ের পেছনে পেছনে বৌদ্ধমন্দির চলে যেত। ও শেষবারের মতো চলে যায় ৭০-এর শেষের দিকে। আর ফিরে আসেনি। সেই কিলার যখন ঘুমাত, ভাইয়া আসা-যাওয়ার পথে ওর নাকে নস্যি গুঁজে দিত। ঘুমন্ত কিলারের নস্যির সুড়সুড়িতে হাঁচি দিতে দিতে জীবন বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম। ঘাসে নাক ঘষে তো সামনের দু’পা দিয়ে নাক চুলকিয়ে প্রচ- ভয় পেয়ে লাফালাফি শুরু করে দিত। সে যে কী বেকায়দা অবস্থা কিলারের! ভাইয়া এ দুষ্টমিগুলো শিশুর মতো উপভোগ করতেন।
একবার রাতের বেলা আমি আর মেঝমণি (মিনু বিল্লাহ) জানালার পাশে পড়ার টেবিলে পড়ছিলাম। আমাদের ঘরের সঙ্গেই বারান্দা। তারপর উঠোন। বারান্দার লাইট জ্বলছিল। কিন্তু কখন অফ করে দিয়েছে টের পাইনি। হঠাৎ জানালায় ঠক্ঠক্ শব্দ-অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। তবুও আলোআঁধারিতে দেখলাম একটা সাদা স্যান্ডো গেঞ্জি বারান্দা দিয়ে হাঁটছে। দেখেই আমরা দুজন ভয়ংকর-চিৎকার করি। আর বারান্দা থেকে হা-হা- হাসির শব্দ আসে। আসলে ভাইয়া লুঙ্গি কাছা মেরে স্যান্ডো গেঞ্জিটাকে হাঁটু অবধি টেনে এনে এমনভাবে হাঁটছিল যে মনে হচ্ছিল একটা মানুষহীন স্যান্ডো গেঞ্জি হাঁটছে অন্ধকারে।
মাঝেমধ্যে আমাদের ঘরের দরজার পর্দা ফাঁক করে শুধু মাথাটা বের করে উঁকি দিতেন। পুরো শরীরটা পর্দার মধ্যে ঢেকে সামনের দুটি দাঁত বের করে খরগোশের মতো একটা দুষ্টু চেহারা বানাতেন। তখন মনেই হতো না যে এই ভাইয়া সেই কঠিন শিক্ষক- যিনি একফোঁটা ভুলভ্রান্তি পছন্দ করতেন না। তাকে দেখে এমন অনেক কিছুই শিখিছি। যার কোনো মূল্য আমি আমার জীবন দিয়েও দিতে পারব না।
ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের সময়ে তিনি আপনাদের পাশে ছিলেন। সেই সময়কার কোনো কথা কি মনে আছে?
১৯৬৯-এ বুলবুল ললিতকলা একাডেমি থেকে ২০ ফেব্রুয়ারি রাতে অনুষ্ঠান হবে শহীদমিনারে। একসময় প্রচ- গোলমাল শুরু হলো। এনএসএফের গু-ারা অনুষ্ঠান প- করার জন্য ইট-পাটকেল ছুড়তে লাগল। বাফার অনেক নাচের মেয়েরাও ছিল সেদিন। ভাইয়া আমাকে ‘নাকের বদলে নরুন পেলাম টাক ডুমা ডুম ডুম’ এ গানটি শিখিয়েছিল গাইবার জন্য। হঠাৎ আমি বুঝতে পারলাম আমি শূন্যে ঝুলছি। ভাইয়া আমাকে চিলের মতো ছোঁ মেরে শহীদমিনারের পেছন দিকে নিয়ে গিয়ে ‘মারুফ মারুফ শিমূলকে ধর’ বলেই ওপর থেকে ছেড়ে দিলেন। নিচে বাফার মারুফ ভাই আমাকে ততক্ষণে ধরে নিয়েছেন। সেই অবস্থায় মেয়েদের সবাইকে মেডিকেল কলেজের ভেতরে রেখে আবার গেলেন হারমোনিয়াম তবলা আনতে শহীদমিনারে। কেমন করে ভুলব ভাইয়াকে।
গণ-আন্দোলনের সময় ঢাকায় ক্রিকেট খেলা হচ্ছিল। হঠাৎ স্টেডিয়ামে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়লে সেখানেও সব কিছুতে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। আমি আমার ভাইদের সঙ্গে খেলা দেখতে গিয়েছি। কোনোমতে স্টেডিয়াম থেকে বের হয়ে ভাইদের হাত ধরে দৌড়াচ্ছি। টায়ার জ্বলছে, বাস জ্বলছে, মানুষ যে যেদিকে পারছে দৌড়াচ্ছে- এর মধ্যে দেখি ভাইয়া রাস্তা দিয়ে উদ্্ভ্রান্তের মতো ছুটে আসছে। পরনে লুঙ্গি আর হাফহাতা সাদা শার্ট। আমাকে দেখে ভাইদের হাত থেকে আমাকে ছোঁ মেরে নিয়ে ভাইদের ওপর অসম্ভব রেগে গেল। কারণ তারা আমাকে এ বিপদের মধ্যে নিয়ে এসেছে। দেশের অবস্থা ভালো না সেটা সবাই জানে। যে কোনো সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। রাগে গজগজ করতে করতে আমার হাত ধরে হাঁটা দিলেন বাসার রাস্তায়। আমি সেই মহৎ মানুষটার আদর, স্নেহে, ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত।
শুনেছি শহীদ আলতাফ মাহমুদের তো আগরতলা চলে যাওয়ার কথা ছিল। তিনি গেলেন না কেন?
১৯৭১-এর আগস্টে মেজদা আর মেঝমণি (মিনু বিল্লাহ) শাহাদত ভাইয়ের সঙ্গে আগরতলা চলে যায়। ভাইয়ারও (আলতাফ মাহমুদ) যাওয়ার কথা। কিন্তু কিছু গানের রেকর্ডিং করা বাকি ছিল। তাই ঠিক হলো ৩ সেপ্টেম্বর যাবে। ওরা চলে যাওয়ার পর সবারই মন খারাপ বিশেষ করে মায়ের। ভাইয়া মাকে ব্যস্ত রাখার জন্য ঠিক করলেন যে, কাঁচা বেলের মোরম্বা বানাবেন। কাঁচা বেলের ওপরে অংশ কাটা যে কি ভীষণ কঠিন কাজ, সেদিন দেখলাম। খোলসটা খুবই শক্ত। ভাইয়া বেলের ভেতর থেকে শাঁস বের করে গোল গোল করে কেটে দিচ্ছিলেন। আর মাকে চিনির সিরা তৈরি করতে বললেন। বেল সিদ্ধ করে চিনির সিরায় তেজপাতা, এলাচ, দারুচিনি দিয়ে ঘন করে নামালেন। আমরা সবাই খেয়েছিলাম, ভীষণ স্বাদ হয়েছিল। বাকিটুকু রাখা ছিল ফ্রিজে।
তাকে তো ৩০ আগস্ট পাকিস্তানিরা ধরে নিয়েছিল...
হ্যাঁ। পাকিস্তানি আর্মিরা ওই রাতে ভাইয়াকে ধরে নিয়ে গেল। অস্ত্র রাখার দায়ে। আমার চার ভাই, নাসের ভাইরা দুই ভাই, আলভী মামা (আবুল বারাক আলভী) আরও অনেকে ধরা পড়লেন। সব মিলে ১১ জন হবে। ১ সেপ্টেম্বের সবাই ফিরে এলো। শুধু ভাইয়া আর ফিরে আসেনি। সেই বেলের মোরাব্বা মা কাউকে ধরতেও দিতেন না। ফেলতেও দিতেন না। ফ্রিজের ভেতরেও কালো পিঁপড়া ঘিরে ফেলেছিল। গোল গোল মোরাব্বাগুলোকে- যেমনিভাবে পাকিস্তানি আর্মিরা ঘিরে ফেলেছিল ভাইয়াকে।
পাকিস্তানি আর্মিরা কি খুব ভোরে রেইড (হানা) দিয়েছিল?
হ্যাঁ। ভোর সাড়ে পাঁচটা তখন। আমার মা তখন নামাজ শেষে কুরআন শরিফ পড়ছিলেন। আমি মায়ের পাশে খুব আস্তে আস্তে রেওয়াজ করছিলাম। যেন বাইরে আওয়াজ না যায়। হঠাৎ করে দেখি যে আমাদের পুরো বাড়িটা একেবারে আর্মি ঘিরে ফেলেছে। মনে হলো কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে সব ঘটে গেছে। ঘরে সাধারণ দরজা ছিল। চোর-ছ্যাচড় তো তখন খুব একটা ছিল না। তাই দরজাও বিশেষ করে বানানো হয়নি। আর্মিরা লাথি মেরে দরজা ভেঙে ফেলল। ঘরের ভেতর ঢুকল। একটাই প্রশ্ন ছিল, ‘আলতাফ মাহমুদ কন হে?’ ক্র্যাক প্লাটুন নাম শুনেছেন নিশ্চয়। ভাইয়া ওই প্লাটুনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। দুই ট্রাক আর্মস এসেছিল। সেটার জন্যই বাসা তল্লাশি করা হয়। যিনি দেখিয়ে দিয়েছিলেন তিনিও একজন মুক্তিযোদ্ধা। তিনি আর্মিদের সঙ্গে এসেছিলেন। তিনি টর্চার সহ্য করতে না পেরে সব বলে দিয়েছিলেন। তার নাম আব্দুস সামাদ।
আমার চার ভাইসহ আলতাফ মাহমুদ ভাই দোতলায় থাকতেন। পাশের বাসা থেকে দু’ভাই মোট এগারো জনকে ওরা ধরে নিয়ে যায়।
আলতাফ মাহমুদ ভাইকে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর আপনার বোন তার সন্তানের কী অবস্থা হয়েছিল?
আমরা তো স্বাভাবিকভাবেই ভেঙে পড়েছিলেন। কোলে তিন বছরের শাওন। বোনের বয়সও ২৩ বছর। পুরো পরিবারই মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিল। শুধু আলতাফ ভাই চলে যাওয়া না। দুটো জীবনের প্রশ্ন। আমার মা তো মারাই গেলেন আলতাফ ভাইয়ের কথা চিন্তা করে করে। মা ১৯৮৬ সালে মারা গেছেন। তিনি আর শোক নিতে পারছিলেন না। প্যারালাইসিস হয়ে গিয়েছিল। মায়ের বিশ্বাস ছিল আলতাফ ভাই ফিরে আসবেন। কোনো একদিন তাকে পাওয়া যাবে। মাকে দেখে আমাদেরও বিশ্বাস তৈরি হয়েছিল। আমরা ভেবেছিলাম তিনি আসবেন। এমনও অনেক মানুষ বলেছে করাচিতে নিয়ে গেছে। ক্যান্টনমেন্টে আটকা আছে। তারপর কারা হাসপাতালে আছে। যেখানেই শুনতাম ছুটে যেতাম। শেষে রায়েরবাজার বধ্যভূমি তন্ন তন্ন করে খোঁজা হয়েছে। ১৭ ও ১৮ ডিসেম্বর। দুদিন। কোনো খোঁজ মেলেনি।
আচ্ছা রায়েরবাজার বধ্যভূমির দৃশ্যটা কি আপনার মনে পড়ে?
ওই বিভীষিকাময় দৃশ্যের কথা আমি বলতে পারব না। আমি সেই স্মৃতি মনে করতে চাই না। এতটাই ভয়ংকর ছিল যে... (মাথা দুপাশে চেপে ধরে চোখ বন্ধ করলেন)। ওই বয়সে সেই বিভীষিকাময় পরিস্থিতি দেখা আমার সারা জীবনের একটা ক্ষতি। এই ক্ষতিটা ভেতরে হয়ে গেছে। আমি পারি না। ওই বীভৎস দৃশ্য আসলে মেনে নেওয়া যায় না।
২৫ মার্চ রাতে আপনারা ঢাকায় ছিলেন। তখনকার কথা কি মনে আছে?
একাত্তরে আমার বয়স তখন ১৪ বছর। আমরা ঢাকাতেই ছিলাম। ঢাকা ছেড়ে যায়নি কোথাও। আমাদের বাসা ছিল রাজারবাগ পুলিশ লাইনসের কাছে, ঠিক উল্টো দিকে। ওখানে আর্মিরা সারাক্ষণ থাকত। ২৫ মার্চ রাতে বেশকিছু বেড়ার ঘরে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হলো। রাস্তার ঠিক উল্টো দিকে আমাদের বাড়িটা ছিল। ওই রাতের ঘটনাগুলো একদম চোখের সামনে দেখা। আলতাফ ভাই ককটেল বানানোর জন্য দুই ড্রাম পেট্রল রেখেছিল। যখন আগুন দিল তখন ভয়ানক এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হলো। বেড়া ছিল। বিকটভাবে আগুন জ্বলছিল। বাতাসে আগুনটা আমাদের দিকে আসছিল। তাপে দাঁড়ানো যাচ্ছিল না। ওই সময়টায় যত লেপ, কাথা, কম্বল, জাজিম-টাজিম, তোষক ছিল সব ভিজিয়ে ওই পেট্রলের ড্রাম দুটোর ওপর দেওয়া হলো। ওইগুলা গরম হয়ে গেলে পুরা বাড়ি ব্লাস্ট হয়ে যাবে। ভয়াবহ বিস্ফোরণ হবে। আমরা সবাই মরব।
২৫ মার্চ আমাদের একটা ভয়ংকর পরিস্থিতির মুখে দাঁড় করিয়েছিল। আমি জীবনে প্রথম ওই দিন গুলির আওয়াজ শুনেছিলাম। তার আগে কোনো দিন গুলির আওয়াজ শুনিনি। মাকে বলেছিলাম, মা এটা কী? তখম মা আমাদের সবার মাথা চেপে ধরে খাটের তলায় ঢুকিয়ে দিয়ে বললেন, ‘গুলি হচ্ছে!’ তারপর তো শেল, মর্টার এটাওটা অনেক কিছুর শব্দই পেলাম। কিন্তু গুলির শব্দ ওই দিন প্রথম শুনি।
ঢাকায় তখন কারফিউ চলছি। এর মধ্যেই আপনারা এখানে ছিলেন?
কোথায় যাব? আমাদের যাওয়ার জায়গা ছিল না। তারপর ২৭ মার্চ যখন দুই ঘণ্টার জন্য কারফিউ ব্রেক করল। তখন আমরা চলে গেলাম কমলাপুর বৌদ্ধমন্দিরে। সেখানে দুদিন ছিলাম। তারপর আবার আমরা চলে এসেছি। দরজা-জানালা সব সময় কালো কাগজ দিয়ে আটকানো থাকত। ঘরে কেউ আছে, এটা যেন বাইরে থেকে বোঝা না যায়। ঢাকায় একদম বন্দি অবস্থায় ছিলাম। ব্লাকআউট ও কারফিউ যে কী জিনিস তখনকার প্রজন্ম অর্থাৎ আমরা ছাড়া মনে হয় এ প্রজন্ম বুঝতে পারবে না। তখন প্রতিটা বাড়িতে ভেন্টিলেটর ছিল। ভেন্টিলেটর দিয়ে যদি একটু আলো বাইরে যেত তাহলেই ওটা লক্ষ্য করে গুলি চালানো হতো। রাতের বেলা এত খারাপ অবস্থা ছিল। রাতে লাইট জ্বালাতাম খুব সাবধানে। লাইটের ওপর কাভার দিয়ে। আলো যেন মেঝেতে পড়ে, যেন না ছড়ায়। ভেন্টিলেটরগুলো কাগজ দিয়ে বন্ধ করা ছিল। মানে একদম মরে যাওয়ার মতো অবস্থা। তখন আমি ম্যাট্রিকও দিইনি। ম্যাট্রিকে আমি ৭২-এর ব্যাচ। তখন আমার সব দিক দিয়েই ক্ষতি হলো। যুদ্ধ চলাকালে ৯টি মাসে অনেক ক্ষতি হয়েছে।
পারিবারিকভাবে আপনার রাজনৈতিক সচেতনতা ছিল বেশ আগে থেকেই...
আলতাফ ভাইয়ের সঙ্গে অনেক অনুষ্ঠানে যাওয়ার সুযোগ হয়েছে তখনই। রাজনৈতিকভাবে জিনিসটা তখন ঠিক বুঝতাম না, তবে বুঝতাম কিছু একটা। সেটা হলো ৬৯-এর গণ-আন্দোলন থেকে। তখন ভাইয়ার সঙ্গে গণসংগীত গাওয়া, শেখা এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গণসংগীত করা। এগুলো তখন থেকে করা এবং পশ্চিম পাকিস্তান যে আমাদের কে শোষণ করছে, এসব কথা বড়দের কাছ থেকে শুনতে শুনতে একটা ঘৃণা চলে এসেছিল। তো সেই কারণে যখন ৭১-এ স্বাধীনতাযুদ্ধ হয়, তখন কিন্তু ততটা অবাক হইনি। আমি শুরু থেকেই এটার মধ্যে ছিলাম। আমাদের কিন্তু একটা প্রস্তুতি পর্ব চলছিল। তখন সেটা বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজ গঠন করে আলতাফ ভাইয়েরা করেছিলেন। হাসান ইমাম থেকে শুরু করে, বাংলাদেশে চলচ্চিত্র শিল্পীদের মধ্যে জাহিদুর রহিম, ওয়াহিদুল হক, ঢাকা ইউনিভার্সিটির প্রফেসররা, তারপর আমরা যারা সংগীতশিল্পী, আমি এবং আমার মতো ছোটরাও অনেকে ছিল। মাহমুদুন্নবী, আরও অনেকে ছিলেন। এরা কিন্তু প্রত্যেকে একটি জায়গায় একত্রিত হয়েছিল। সেই জায়গাটার নাম দিয়েছিল বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজ। সেখানে কিন্তু আমার কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছে এবং আমার নতুন নতুন গান শেখার সৌভাগ্য হয়েছে। সমরদা, শুখেন্দু চক্রবর্তী তখন কিন্তু তারাই নতুন নতুন গান করতেন। গণসংগীতের নতুন নতুন গান করতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তুলে নিয়ে আমরা অনুষ্ঠান করতাম। এগুলো নিয়ে ৬৯ থেকে ভেতরে একটা আলোড়ন তৈরি হয়েছিল। একাত্তরের যুদ্ধটা এবং আমাদের একটা স্ট্রাগল করতে হবে সেটা আমরা বুঝে গেছি।
একাত্তরের ৭ মার্চ আপনি ঢাকাতেই ছিলেন। তখন কী দেখেছিলেন?
আলতাফ ভাই বঙ্গবন্ধুর জনসভায় গিয়েছিলেন। আমি তো ভাইয়ার লেজ ছিলাম। তিনি যেখানে যেতেন সঙ্গে যেতাম। আমিও সেদিন গেলাম তার সঙ্গে। আলতাফ ভাইয়ের গাড়িটা ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউটের সামনে পার্ক করা ছিল। আমি তো একটু লম্বা-চওড়া হয়ে উঠছি। উনি ভেতরে গিয়েছিলেন আর আমি গাড়ির ছাদে উঠে ভাষণ শোনার চেষ্টা করছিলাম। তারপর ঐখান থেকে হইহুল্লোড় করতে করতে বাসায় চলে আসা। তবে বঙ্গবন্ধুকে ওইভাবে দেখতে পারিনি। তার কণ্ঠস্বর শুনেছি।
যুদ্ধকালীন সময়ে বন্দিদশায় ছিলেন বলছিলেন। একেবারেই বের হওয়ার সুযোগ পেতেন না?
বের হয়েছি খুব কম। যুদ্ধের সময় পুরো ঢাকায় তো কারফিউ কারফিউ অবস্থায় ছিল। রাতে তো প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬টা থেকে ভোর ৫টা পর্যন্ত কারফিউ থাকত। আর জরুরি অবস্থা হলে তখন আবার চেঞ্জ করত। সকাল ১০টা থেকে ১২টা। বা ২টা থেকে সারা রাত। আলতাফ ভাইকে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর যতটা বের হয়েছি তার আগে ওইভাবে হয়নি। আলতাফ ভাইকে খোঁজার জন্য মায়ের সঙ্গে আমাকে সব জায়গায় যেতে হতো। আমার বড় বোন তো তখন একদম তরুণী। ২৩ বছর বয়স। তো আমি মায়ের সঙ্গে সঙ্গে থাকতাম ভাইদের কোথাও বের হতে দিত না মা। কারণ আমার ভাইরাও তো ধরা পড়েছিল। ওদের শারীরিক অবস্থা খুব খারাপ ছিল। পাকিস্তানি আর্মিরা ওদের অনেক টর্চার করেছে।
১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানিরা আত্মসমর্পণ করল। তখন ঢাকার পরিবেশ কেমন ছিল? মনে আছে?
প্রথম দিকে কেউ বিশ্বাস করেনি। লোকজন বের হয়নি। অনেক দিন কারফিউ থাকার পরে হঠাৎ করে লোকজন বের হয়নি। লোকজন বের হয়েছে ৪টার পর। একজন-দুজন করে। কারণ তখনও ওরা গুলিগালা করছিল। লাস্ট মোমেন্ট পর্যন্ত ওরা গোলাগুলি করেছে। ১৬ ডিসেম্বরে স্যারেন্ডার করেছে রেসকোর্সে। কিন্তু আশপাশে যারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল তারা তখনও মানুষ মেরে গেছে। কাজেই হঠাৎ করে করে কেউ বের হয়নি। আর আমাদের তো বের হওয়ার প্রশ্নই ছিল না। কেউ কিন্তু আমরা ভয়ে বের হয়নি। এমন ভাবে গোলাগুলি হচ্ছিল যে, এটা পাকিস্তানি আর্মি না বাংলাদেশি মুক্তিযোদ্ধা এটা বুঝতে পারছিলাম না। আমরা খবর পেয়েছি চারটার দিকে। একজন মুক্তিযোদ্ধা এসে খবর দিয়েছিল যে দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে। তখনো আত্মসমর্পণের কাগজে স্বাক্ষর হয়নি। তবে নিয়ে গেছে সবাইকে। ততক্ষণে সবাই, যারা মতিঝিলের দিকে বিশ্বাস করেছিল যে দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে, তারা কিছু বের হয়েছিল। তাদের মাঝেও কিছু মানুষ কিন্তু ১৬ ডিসেম্বর মারা গেছে। শুধু আমার মনে আছে, আমরা তখন বাসাটা চেঞ্জ করেছিলাম। আমরা মগবাজারের ভেতরে চলে গিয়েছিলাম। কারণ এই বাসাটা থেকে ভাইয়াকে ধরে নিয়ে যাওয়ার পরে দুই-তিনবার রেইড (হানা) চালিয়েছিল।
মগবাজার ওয়্যারলেস যেখানে ওখান থেক যখন পাকিস্তানি আর্মিরা বেল্ট খুলে, ক্যাপ-ট্যাপ খুলে, ওদের মেজর কেউ ওদের লাইন ধরে নিয়ে যাচ্ছেÑতখন ওদেরকে দেখেছি যে ওরা হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে। তারপরে রেডিও টেলিভিশনে খবর আসতে লাগল আর হেলিকপ্টার থেকে লিফলেট ফেলা হচ্ছিল। সেই লিফলেট দেখে বুঝলাম যে দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে। আমরা সব ছাদে চলে গেলাম। গিয়ে লিফলেট কুড়ানো শুরু করলাম।
হেলিকপ্টার থেকে ছড়িয়ে দেওয়া লিফলেটে কী লেখা ছিল?
বার্তা ছিল যে, বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে গেছে। আপনারা সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে আসুন। এটা লেখা ছিল।
আলতাফ মাহমুদ ছাড়াও আপনি অনেক ওস্তাদের কাছে গান শিখেছেন। তাদের সম্পর্কে শুনতে চাই।
একদম ছোটবেলায় যার কাছে গান শিখেছি তিনি নারায়ণগঞ্জ থেকে আসতেন। ওস্তাদ হেলাল উদ্দীন। তারপর গান শিখেছি পিসি গোমেজ ওস্তাদজির কাছে। এছাড়া ফুল মোহাম্মদ ওস্তাদজি, ইমামুদ্দিন ওস্তাদজি, তারপর আব্দুল লতিফ, শেখ ওসমান রহমান, রনীল কুশারী দাশ, শুখেনু চক্রবর্তী। এ রকম সব বড় বড় মানুষ, যারা গান পছন্দ করতেন। তাদের কাছ থেকে আমার গান শেখা। ভাগ্য যদি বলি, আমার কোনো ওস্তাদ আমার কাছ থেকে টাকা নেননি। বরং উল্টো আমাকে তানপুরা, হারমোনিয়াম উপহার দিয়েছেন। তারা খুশি হয়ে আমাকে এগুলো দিতেন।
স্কুলজীবনে কোথায় পড়েছেন?
আমি স্কুলে যাওয়া শুরু করেছি ৬২ সাল থেকে। বাবা মারা যাওয়ার পরপর। আমার স্কুল ছিল মতিঝিলে। সেন্টাল গভর্মেন্ট গার্লস স্কুল। ওখান থেকে হেঁটে স্কুলে যেতাম। হেঁটে আসতাম। তখন তো ঝামেলা ছিল না ঢাকা শহরে। মাথা গুনে লোক পাওয়া যেত। তো এখানেই আমার ম্যাট্রিক। তারপর ঢাকা ইউনিভার্সিটি।
স্কুলজীবনের কোনো স্মৃতি কি মনে আছে?
স্কুলে যেটা হতো কি, আমাকে প্রায় হাফ স্কুল করতে হতো। কারণ বিকালবেলায় প্রোগ্রাম থাকত। হয় টেলিভিশনে, না হয় রেডিওতে। প্রোগ্রাম থাকলে আমাকে হাফ করতে হতো। কারণ ওই সময় তো সরাসরি প্রচার করতো। যেতে হতো একটু আগে। এই হাফ স্কুলটার জন্য আমাকে আবেদন দিতে হতো। মাঝে মাঝে প্রায় বকা শুনতাম।
আপনি টেলিভিশন প্রোগ্রাম করা শুরু করলেন কোন বয়স থেকে?
যখন টেলিভিশন হয়েছে, প্রথম দিন থেকেই। ১৯৬৪ সালে।
আপনার স্কুলজীবনের বন্ধু বা সহপাঠী তারা কি কেউ এখনো সাংস্কৃতিক অঙ্গনের সঙ্গে যুক্ত আছেন?
না। আমার সহপাঠীরা নেই। এই পরিম-লে তারা নেই। কিন্তু বাইরে যারা রেডিও, টেলিভিশনে বন্ধু ছিলেন সবাই মোটামুটি আছেন।
আপনি ইন্টারমিডিয়েটে কোথায় পড়লেন?
আসলে আমি সেভাবে ইন্টারমিডিয়েট পড়িনি। চারুকলায় পড়েছি দুই বছর। মানে আর্ট কলেজে। সেখান থেকে ইন্টারমিডিয়েট দিয়ে দিয়েছিলাম। পরে ইউনিভার্সিটিতে ঢুকে গেছি।
একদিকে সংগীতচর্চা অন্যদিকে আর্ট, কোন বিষয়টাকে আপনি প্রাধান্য দিয়েছেন?
অবশ্যই গানটা আমার প্রথম অগ্রাধিকার ছিল। আর্ট কলেজে পড়েছি এ কারণে। আমি তো ‘কচিকাঁচার মেলা’ করতাম। সেখান থেকে পেইন্টিংয়ের একটা নেশা ছিল। তখন তো শাহাদত চৌধুরী ভাইয়েরা আছেন। রফিকুন্নবী ভাইয়েরা আছেন। সবচেয়ে বড় কথা জয়নুল আবেদীন স্যার আছেন। আমার মনে হতো এই জায়গাটা আমার জন্য খুব কমফর্টেবল। পরিচিত মানুষ আছে, সবাই আছে। এমনি আমি আর্ট কলেজে পরীক্ষা দিয়েছিলাম। পরে দেখি নির্বাচিত হয়ে গেছি। এবং ভালো পজিশনে আছি। থার্ড না ফোর্থ হয়েছিলাম।
জয়নুল আবেদিন স্যারের সঙ্গে কোনো স্মৃতি যদি বলতে চান।
তিনি আমার গান খুব পছন্দ করতেন। আমি তো তখন খুব ছোট। তিনি তার জিনিসপত্র কাউকে ধরতে দিতেন না। কিন্তু আমাকে তিনি নিজের হাতে করা দুটো পুতুল দিয়েছিলেন। আমার গানে এত খুশি হয়েছিলেন যে, তিনি আমাকে কোলে করে নিয়ে মাটির পুতুল দুটি হাতে দিয়েছিলেন।
সাপ্তাহিক ‘বিচিত্রা’ সম্পাদক শাহাদত চৌধুরীর কথা বলছিলেন। তিনি কি তখন আর্ট কলেজে ছিলেন?
তিনি তখন আর্ট কলেজ থেকে পাস করে বের হয়েছেন। তিনি যেতেন। শিক্ষক ছিলেন না কখনো। আসা-যাওয়া করতেন। আলভী মামা (আবুল বারাক আলভী)Ñএরা কিন্তু সবাই ‘কচিকাঁচার মেলা’ করতেন। রফিকুন্নবী ভাই। মানে এ ব্যাচটাই ‘কচিকাঁচার মেলা’ করত। তারা আমার বড় ভাইয়ের বয়সী ছিলেন।
সাংস্কৃতিক পরিম-লে বেড়ে ওঠা। গান করতেন শৈশব থেকে। পরে থিয়েটারে যোগ দিলেন। অভিনয়ের চর্চা কি আগেই ছিল?
ছোটবেলা থেকেই তো টেলিভিশন, রেডিওতে নাটক করতাম। স্ক্রিপ্ট দেখে রেডিওতে নাটক করতাম। ওখানে সবচেয়ে সুবিধা হলো, রেডিওতে প্রোগ্রাম করলে বাচ্চা হোক, বড় হোক, ছোট হোক উচ্চারণটা খুব দেখা হতো। যেহেতু এটা শুধু শ্রবণ। কাজেই উচ্চারণ স্পষ্ট না হলে, উচ্চারণ ভুল হলে রনীল কুশারী স্যার আমাদের উচ্চারণ ঠিক করে দিতেন। সেভাবে রেডিওতে উচ্চারণটা ও এক্সপ্রেশনটা করতে হতো। আমাকে একটা মাইক্রোফোনে কিন্তু এক্সপ্রেশনও জানাতে হবে। তাই সেইগুলোর একটা ট্রেনিং হয়ে গেছে রেডিওতে ছোটবেলায়। আর যখন টেলিভিশনে এলাম, তখন এটা তো দেখার জিনিস। টেলিভিশনে দেখাতে হলে আমাকে এক্সপোজারটা আরেকটু বাড়াতে হবে। অভিনয়টা দেখাতে হবে। এই ট্রেনিংটা আমরা পেলাম মোস্তাফা মনোয়ার স্যারের কাছ থেকে। তো উনি দেখালেন একজন অভিনেতা বা একজন শিল্পী শুধু গান গাইছে; শুধু গান গাইলেই হবে না। মানে বাচ্চাদের অনুষ্ঠানের কথা বলছি। তাকে অভিনয় জানতে হবে, নাচ জানতে হবে। আবৃত্তি করতে হবে। এ জায়গাগুলো আমাদের মোস্তফা ভাই শেখালেন। আমি তার সঙ্গে ছোটবেলায় পাপেট শোও করেছি।
ওই সময় পাপেট শোটা কেমন ছিল, বলবেন?
তখন বাঘামিনি বলে একটা সিরিজ ছিল। সেই সিরিজটাতে নিজেরাই পাপেট করতাম টেলিভিশনে। আর নিজেরাই কণ্ঠ দিতাম। ওটা মোস্তফা মনোয়ার স্যারের অধীনে করতাম।
আপনার পড়াশোনা, সংস্কৃতিকচর্চা বা শিল্পীজীবন এই দুটো তো সমান্তরালে চলেছে। কখনো কি এ নিয়ে দোটানায় পড়তে হয়েছে?
না-না। এটা কখনই হয়নি। আসলে আমরা খুব বাধ্য ছিলাম। মুরব্বিদের কথায় বাধ্য আর কি। মা বলতেন গান এবং পড়ালেখা দুটো একসঙ্গে চালাতে হবে। আমরা তিন বোন। মা বলতেন আমার তিনটা মেয়ে ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে এমএ পাস করবে। মায়ের সেই কথা আমরা রেখেছি। ওই যে মেনে নেওয়ার ব্যাপারটা। মুরব্বিদের কথা সেটা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি। সবাই মনে হয় তাই করত আমাদের সময়।
আপনার ভাই-বোনের কথা বললেন। তাদের নাম তো জানা হলো না।
আমাদের সবার বড় ভাই রুহুল আমল বিল্লাহ। তিনি মারা গেছেন। মেজো ভাই ফকরুল আলম বিল্লাহ। তিনিও নেই। তার পরের ভাই খায়রুল আলম বিল্লাহ, তারপর নওফেল আলম বিল্লাহ। সবার ছোট ভাই মঞ্জুরুল আলম বিল্লাহ। ওকে কিন্তু নিলু বিল্লাহ নামে সবাই চেনে। ও গান গায়। বড় বোন সারা আরা মাহমুদ, মেজো বোন মিনু হক তার পরে তো আমি। আমার মায়ের নাম আমিনা বিল্লাহ। আর বাবা মেহেদি আলম বিল্লাহ।
পারিবারিক প্রসঙ্গে কিছু জানতে চাই। বিয়ে করলেন কবে? বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ চুকিয়ে?
না। তার আগেই হয়েছে। আমি যখন সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি তখন বিয়ে হয়।
বিয়ের আগে থেকে বাচ্চু ভাইয়ার (নাসির উদ্দীন ইউসুফ বাচ্চু) সঙ্গে চেনাজানা ছিল?
হ্যাঁ ছিল (হাসলেন)।
পরিচয়টা কীভাবে হয়েছিল?
ওই যে একাত্তর থেকে! এমনিতে জানতাম বাচ্চু কমান্ডার হিসেবে বিরাট মুক্তিযোদ্ধা। যদিও আগে কখনো দেখিনি। তবে যুদ্ধের সময় তার নাম খুব শুনতাম। শুনতাম যে তিনি গেরিলা যোদ্ধা। ওই সময়ে তো এগুলোর খবর রাখতামই। মুক্তিযুদ্ধের কথা। যারা মুক্তিযোদ্ধা, যারা মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে জড়িত। ওই সময় বাচ্চুর ভাইদেরও ধরে নিয়ে গিয়েছিল। তখন সংবাদপত্রে একটা বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় যে, ‘বাচ্চু তুমি ফিরে আসো। তোমার মা শয্যাশায়ী।’ তখন আমি আমার মাকে বলেছিলাম, দেখো মা একজন মুক্তিযুদ্ধে চলে গেছেন। তাকে ফিরে আসতে বিজ্ঞাপন দিয়েছে। সেকি আর আসবে? সে তো যুদ্ধ করতে গেছে। সেই নাসির উদ্দীন ইউসুফ বাচ্চুর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হলো আর্ট কলেজে। ও একদিন গিয়েছিলেন। তখন আমাদের আর্টিস্ট শাহাবুদ্দিন ভাই কাছে বাচ্চুর অনেক গল্প শুনেছি। তিনি তখন পাস করে গেছেন। তারা একসঙ্গেই ছিল। এটা ১৯৭৩ সালের কথা।
যুদ্ধের সময় বাচ্চুর নেতৃত্বাধীন গেরিলা বাহিনী ঢাকা উত্তরে ছিল। ওইখানে শাহাবুদ্দিন ভাই বাচ্চুর অধীনে ছিলেন। অনেক যুদ্ধের গল্প আমরা শাহাবুদ্দিন ভাইয়ের কাছে বসে শুনতাম। খুব বলত, ‘বাচ্চু কমান্ডার’, ‘বাচ্চু কমান্ডার’। আমি একদিন বললাম, শাহাবুদ্দিন ভাই তোমার কমান্ডারকে একদিন দেখাইয়ো তো। পরে তিনি একদিন নিয়ে আসলেন। আমি দেখে খুব হতাশ। তখন বাচ্চু একদম লিকলিকে। লম্বা, লিকলিকে, পাতলা। চুল বড় বড়। আমি বললাম, এটা তোমার কমান্ডার? এত বড় মুক্তিযোদ্ধা? তিনি বললেন, ‘হ্যাঁ’। আমি বললাম, আচ্ছা, তো তোমরা গল্প কর। আমি আসি। আমার এখন ক্লাসে যেতে হবে। ওই প্রথম বাচ্চুকে দেখে প্রথম হতাশ হওয়া। হা...হা...হা।
তারপর আবার কবে দেখা হলো?
ঢাকা থিয়েটারে এসে দেখলাম চুয়াত্তরে। বাচ্চু নির্দেশক। ওখানে কাজ করছে। সেলিম আল দীনের সঙ্গে পরিচয় হলো। দলটাকে খুব ভালো লেগে গেল। সবাই মুক্তিযোদ্ধা। রাইসুল ইসলাম আসাদ থেকে শুরু করে সবাই মুক্তিযোদ্ধা। মনে হলো, এটা আমার জন্য একটা কমফর্টেবল জায়গা। আমি এখানে কাজ করতে পারব। তারপর ঢাকা থিয়েটার করা শুরু হলো। বছর দুই-তিন পরে আমার সঙ্গে বাচ্চুর একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং (বোঝাপড়া) হলো। বিয়েটা হলো ১৯৭৯ সালে।
নজরুলসংগীত গাইতেন। এ আগ্রহটা কীভাবে জন্মাল?
নজরুলসংগীত বলতে গেলে আমি বেসিক্যালি ক্লাসিক্যাল শিখতাম। আমি যা শিখেছি মনে হতো সেটা নজরুলসংগীতে অ্যাপ্লাই করতে পারব। রবীন্দ্রসংগীত তো একটা বাঁধাধরা নিয়মে চলে। আমার কিন্তু পছন্দ রবীন্দ্রসংগীত। গাওয়ার জন্য গাইতাম নজরুলসংগীত। এখানে গায়কীর ব্যাপারে স্বাধীনতা ছিল। সেই জায়গা থেকে পছন্দ ছিল নজরুলসংগীত।
আপনি বলছিলেন, ৭৩ সালে বাচ্চু ভাইয়ের সঙ্গে পরিচয়। বিয়ে হয়েছে ৭৯-এ তাই তো?
হ্যাঁ। তিয়াত্তরে দেখেছিলাম। চুয়াত্তরে ঢাকা থিয়েটারে ভালোভাবে পরিচয় হয়।
তত দিনে আপনি ঢাকা বিশ^বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে গিয়েছিলেন?
না। ৭৪ না ৭৫ ঠিক মনে নেই। তবে সম্ভবত ৭৫-এ ঢাকা বিশ^বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলাম।
যখন ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে মেরে ফেলা হলো, তখন তো ঢাকার পরিবেশ আবার অন্য রকম হয়ে গিয়েছিল...
হুম। ওই একাত্তরের মতো। কেউ ভয়ে ঘর থেকে বের হয়নি।
বলছিলেন বাচ্চু (নাসির উদ্দীন বাচ্চু) ভাইকে প্রথম দেখে হতাশ হয়েছিলেন। গল্পে শোনা সাহসী গেরিলা যোদ্ধার সঙ্গে মেলাতে পারছিলেন না। পরে তাকে ভালো লাগল কীভাবে?
আসলে মানুষের ব্যক্তিত্ব। ব্যক্তিত্ব মানুষকে টানে বেশি মনে হয়। আমাকে মনে হয় ব্যক্তিত্বই টানে বেশি। আমার নিজের ভেতরেই একটা ইচ্ছে ছিল। ইচ্ছে মানে কি আমি ভেবেই নিয়েছিলাম, আমি মুক্তিযোদ্ধা ছাড়া কাউকে বিয়ে করব না। ওই যে ব্যক্তিত্বের কথা বললাম। সেটা আমাকে টেনেছিল। আর সবচেয়ে যেটা বড় বাস্তব ছিল- নির্লোভ একটা মানুষ। মানে কোনো কিছুর চাহিদা ছিল না। কোনো কিছুর প্রয়োজন এটা-ওটা এসব কিছুর চাহিদা ছিল না। জীবন যেভাবে যাচ্ছে, সেভাবেই যাচ্ছে। মানে খুব সাধারণ একটা মানুষ ছিল বাচ্চু। কিন্তু অসাধারণ। সে কারণে মনে হয় আমার খুব ভালো লেগেছিল। হা হা হা।
আপনাদের মধ্যে প্রথম প্রপোজটা কে করেছিলেন?
আমি করেছিলাম। আমরা তখন তুই-তোকারি করতাম। একদিন বললাম, আমি তোকেই বিয়ে করব, আর কাউকে করব না।
সেটা কি তিনি সানন্দে গ্রহণ করেছিলেন?
না-না। মোটেই নয়। তিনি একেবারে স্বাভাবিক ছিলেন। কোনো পরিবর্তনই দেখিনি। অবাকও হয়নি। বরং আমাকে বলেছে, ‘পরে বলব’। আসলে আমাকে পরীক্ষা করেছিল আমি কতটা বিশ্বস্ত। তিন-চার মাস ভাবার জন্য সময় নিয়েছিল। ও আসলে ঢাকা থিয়েটারের প্রতি আমার ডেডিকেশন দেখতে চেয়েছে, দেখতে চেয়েছে আমি কতটুকু কমিটেড। এদিকে আমি কিন্তু ৩ মাস মনপ্রাণ দিয়ে দলের জন্য কাজ করেছি। ব্যাপারটা খুবই ব্যক্তিগত ও মজার। নাসির উদ্দীন ইউসুফকে বিয়ে করার জন্য এই আমার ত্যাগ স্বীকার। আমি ছোট্ট মানুষ, ২১ বছর বয়স তখন-কতটুকুই-বা বুঝি। তবে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দিয়ে বুঝেছিলাম এ লোকটাই আমার জন্য। মানুষ তো কখনো কখনো ভুল করে, আমি এ ব্যাপারে ভুল করিনি।
তিনি ওই সময় থিয়েটারের পাশাপাশি কিছু করতেন?
টেলিভিশনে চাকরি করতেন। বিটিভিতে।
আপনি তো যুদ্ধকালীন বা পরে বেশ কিছুদিন টেলিভিশনে কাজ করেননি...
না, তেমন একটা করা হয়নি। নয় মাস আমার রেডিওতেও যাওয়াই হয়নি।
থিয়েটারে এসে কীভাবে শুরু করলেন?
অভিনয় দিয়ে শুরু করেছিলাম।
আপনার সমসাময়িক ওই সময় কারা ছিলেন?
আমার সমসাময়িক ছিলেন আফজাল হোসেন, রাইসুল ইসলাম আসাদ, পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায়, নায়লা আজাদ নূপুর এ এরকম আরো অনেকে।
প্রথম স্টেজ পারফর্ম কোথায় ছিল?
চট্টগ্রামে। আসলে আমার মঞ্চে আসাটা হঠাৎ করে। আমার দুই ভাই এবং মিনু হক (নৃত্যশিল্পী) তখন ঢাকা থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। (চলবে)......