রোকেয়া হায়দার
তাঁর সঙ্গে কুড়ি মিনিটের আলাপ
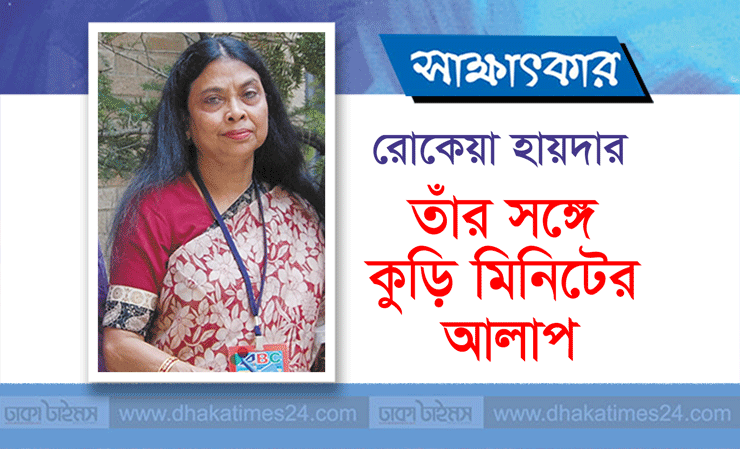
জীবনের ৩৭ বছর পার করেছেন ভয়েস অব আমেরিকায়। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক এ সংবাদমাধ্যমে তিনি এখন বাংলা বিভাগের প্রধান। প্রায় চার দশকের এই যাত্রাকে সংবর্ধিত করতে এক হয়েছিলেন গুণগ্রাহীরা। সুদূর হার্ডসন নদীর দেশ থেকে ভেসে আসা কণ্ঠের জাদুতে যারা মোহিত, সেই শ্রোতা-ভক্তরা জড়ো হয়েছিলেন ঢাকায়। রোকেয়া হায়দার তখন বিভুঁই ছেড়ে দেশের মাটিতে। গত ১১ অক্টোবর জাতীয় প্রেসক্লাবে ভিআইপি লাউঞ্জের ওই অনুষ্ঠান ছিল কেবল রোকেয়াময়। আর কোনো কথা নেই। নেই কোনো ভাষা। মাইক্রোফোনটি তখন শ্রোতাদের হাতে। যার মন্ত্রমুগ্ধ কণ্ঠের ভালোবাসায় জড়িয়ে ছিলেন, তিনি তখন শ্রোতার আসনে। তারপর শ্রোতাদের সামনে তিনি। সেই স্নিগ্ধ বচন। অমৃতসম। এত দিন যাকে বেতারে শুনেছেন, সেই মানুষটি ঠায় দাঁড়িয়ে চোখের সমুখে!
আর সবার মতো মুগ্ধতা আমার অন্তস্তলেও। রয়েছে একটি বিশেষ উদ্দেশ্যও। তার সঙ্গে একান্ত আলাপের। সময় দেওয়া ছিল এক দিন আগেই। একের পর এক অনুষ্ঠানে ক্লান্ত হয়ে পড়েন তিনি। মাথায় প্রচণ্ড ব্যথা হচ্ছে জানিয়ে বাতিল করেছিলেন আগের দিনের সাক্ষাতের নির্ধারিত সময়। পরদিন সময় দিতে পারবেন, এমনটারও নিশ্চয়তা ছিল না। শর্ত ছিল অনুষ্ঠানের শেষে যদি সময় থাকে, কথা বলবেন। সেই অপেক্ষায় দীর্ঘ সময়। কখন সুযোগ হয়। অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিকতা শেষ হলেও রেশ রয়ে গেল। রোকেয়া হায়দারকে ঘিরে রইলেন তার শ্রোতারা। কথা বলা তো দূরে থাক, কাছে যাওয়ার সুযোগ নেই। নাছোড়বান্দা আমি। ঘুরঘুর করছি পেছন পেছন। ভয়েস অব আমেরিকার উত্তরাঞ্চল প্রতিনিধি বন্ধুবর সাংবাদিক প্রতীক ওমরের সহযোগিতায় অবশেষে পেলাম তাকে। লাউঞ্জের এক কোণে চেয়ার টেনে বসতে বসতে বললেন, ‘একেবারেই সময় নেই হাতে। বেশি কথা বলতে পারব না। এত মানুষ তাদের তো সময় দিতে হবে।’
এখানে এসেও রেহাই পেলেন না। একজন চেয়ারের পাশে এসে হাঁটু গেড়ে বসে বললেন, ‘একটা ছবি নেব আপা?’ তিনি অমত করলেন না। বলতে বলতে আরও দুজন পেছনে দাঁড়িয়ে পোজ দিলেন। বললেন, ‘দেখলেন তো কী অবস্থা। এত এত মানুষ রেখে আলাদা কথা বলা যায়?’
মুঠোফোনের রেকর্ডারটি অন করে বললাম, ‘খুব বেশি সময় নেব না, পাঁচ মিনিট।’ কেউ একজন দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি তার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে কুশল বিনিময় শেষে বললেন, ‘বলুন কী জানতে চান?’
বললাম, আপনি তো যশোরের মেয়ে। ওখানে বাবার বাড়ি। কিন্তু আপনার শৈশব কেটেছে কলকাতায়। দিনগুলো কেমন ছিল?
ব্যস্ততার জানালা পেরিয়ে একটু বাইরে উঁকি দেওয়ার ফুরসত পেলেন যেন। স্নিগ্ধ হেসে রোকেয়া হায়দার বললেন, কলকাতায় আমার জন্ম। সেন্ট জোনস স্কুলে পড়াশোনা করেছি। ১৬ বছর বয়স পর্যন্ত ওখানেই ছিলাম। ঢাকায় এসে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছি। তারপর ইডেন কলেজ। এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ছোটবেলায় আমাদের বাসায় আমার নানা থাকতেন। তখন কলকাতার আকাশবাণীতে গিয়ে কবিতা আবৃত্তি করতাম।
তখন আপনার বয়স কত? তখন বয়স ছিল পাঁচ কি ছয় বছর। কোনো কোনো সময় বাচ্চাদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশ নিতাম। তারপর আবৃত্তি নিয়মিত করব বা পেশা হিসেবে নেব, এ রকম ইচ্ছা ছিল না। পরে ঢাকায় এসে স্টুডেন্ট প্রোগ্রাম করতাম ঢাকা বেতারে। অনেক পরে অর্থাৎ ষাটের দশকে আমি বাংলাদেশ রেডিওতে কাজ করেছি, যেটা চট্টগ্রামে ছিল। সেখানে আমি অনুষ্ঠান উপস্থাপনা বা নাটকে অংশগ্রহণ করেছি। তখনো রেডিও পাকিস্তানই ছিল। ১৯৬৮ কি ’৬৯ সালে স্থানীয় সংবাদ পড়া শুরু করি চট্টগ্রাম বেতারে। ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশনে কাজ করি।

১৯৭১ সালে আপনি ঢাকায় ছিলেন? না, আমি চট্টগ্রামে ছিলাম।
আপনি ছিলেন কলকাতায়, পরে ঢাকায় এসেছেন, ওই সময় কলকাতার সঙ্গে ঢাকার সামাজিক পরিবেশ-প্রতিবেশ কেমন ছিল? আমাদের জন্য খুব কষ্টদায়ক ছিল। আমরা কয়েকজন বোন ছিলাম। ঢাকা ছিল খুব রক্ষণশীল আর কলকাতা একেবারেই ভিন্ন। কলকাতা থেকে ঢাকায় এসে মানিয়ে নেওয়াটা আমাদের বোনদের জন্য কষ্টকর ছিল। তারপরও যেহেতু আমরা মুসলিম পরিবারের কন্যাসন্তান, সুতরাং আমাদেরকে মানিয়ে চলতেই হয়েছে। ঢাকায় তখন অনেক গাছ ছিল। এখন যেমন রাতের বেলায় মেয়েরা একা চলতে ভয় পায়, তখন এতটা ছিল না। পরিবেশটা অনেক সুন্দর ছিল। বিশেষ করে রমনা এলাকাটা সত্যিই খুব সুন্দর ছিল। সারি সারি কৃষ্ণচূড়াগাছ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ইডেন কলেজ, শহীদ মিনারÑসবকিছু মিলিয়ে সৌন্দর্যটা ছিল অন্য রকম। এখন আর তেমনটা নেই।
ঢাকায় তোপখানা রোডে থাকতেন তখন? হ্যাঁ, আমার বাবার বাড়ি ছিল ৩৩ তোপখানা রোডে। যশোর হাউস। এখন যেটা মেহেরবা প্লাজা। আব্বার পৈতৃক বাড়ি যশোরে, কিন্তু আমরা কখনো যশোরে থাকিনি। তখন কলকাতার জীবনটা ছিল ঢাকার তুলনায় অনেক ব্যস্ত।
আপনার বাবা কী করতেন? বাবা ব্যবসায়ী ছিলেন। মা গৃহিণী। আমরা নয়জন ভাইবোন ছিলাম। বড় বোন সংগীতশিল্পী ছিলেন সুফিয়া আমিন। তিনি মারা গেছেন ২০০০ সালে। বাবা আমাদের একেবারে ছেলেদের মতো সুযোগ-সুবিধা দিয়ে বড় করেছেন। আমরা চাইলে ব্যারিস্টার, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার সবই হতে পারতাম। লেখাপড়া থেকে কেউ পিছিয়ে ছিলাম না। ছেলে হোক, মেয়ে হোক পড়াশোনাটা করতেই হবে। মোটামুটি আমরা সবাই বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত পড়াশোনা করেছি। বাবা ছিলেন উদারমনা মানুষ। মেয়েদের কোনো কাজেই তিনি বাধা দিতেন না। আমরা নিজেরা নৌকা, সাইকেল ইত্যাদি চালাতে শিখেছি। নাচ-গান সবই ছিল আমাদের পরিবারে।
তখন ঢাকার শিক্ষার পরিবেশ কেমন ছিল? তখনো নাচ হতো, গান হতো। ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে স্কুলে পড়াশোনা করত। ছেলেমেয়েদের একসঙ্গে মেলামেশায় সংকীর্ণতাবোধ তখনকার ঢাকায় ছিল না। কলকাতাতে তো প্রশ্নই ওঠে না।
এই সাক্ষাৎকার যখন নিচ্ছি তখন দেশে আলোচনার কেন্দ্রে বুয়েট শিক্ষার্থী আবরার হত্যা। বিষয়টিতে তিনি নিজেও উদ্বিগ্ন। এ নিয়ে কথা বলতে চাইলে অমত করলেন না। বললাম, আপনি তো ইডেন কলেজে পড়েছেন। তখনকার ছাত্ররাজনীতি কেমন ছিল? তখনকার ছাত্ররাজনীতিতে এখনকার মতো বীভৎসতা, নোংরামি ছিল না। ২১শে ফেব্রুয়ারিতে আমাদের সবাইকে যেতে হতো শহীদ মিনারে। ভোররাতে নগ্ন পায়ে যেতাম ফুল দিতে। ছেলেমেয়ে মিলেই যেতাম। কোনো অসুবিধা হতো না। এখন ছাত্ররাজনীতি জঘন্য একটা রূপ নিয়েছে। বিশেষ করে বুয়েটের ছাত্র আবরার ফাহাদ হত্যার পর আমি আতঙ্কিত হচ্ছি যে, এটা তো আমার ছেলেও হতে পারত।

এটা কিন্তু নতুন নয়। ২০০২ সালে বুয়েটে সাবিকুন নাহার সনি নামের এক ছাত্রী মারা গিয়েছিলেন ছাত্রদের কোন্দলে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৬২ সালের অধ্যাদেশে বলা আছে বুয়েটে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ। তারপরও এগুলো ঘটছে। ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ করা হয়। কিন্তু কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে তৎপর হন না বা মনোযোগই দেন না। আমি শুনেছি, কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ গেলেও তারা অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেন না। এই সুযোগে দুর্বৃত্তরা অবাধে তাদের জঘন্য কার্যকলাপগুলো চালিয়ে যায়।
এক পক্ষ বলছে ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করা হোক, আরেক পক্ষ বলছে, না। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, গণতান্ত্রিক দেশে ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করা যায় না। তবে বুয়েট কর্তৃপক্ষ চাইলে বন্ধ করতে পারে। আপনি বিষয়টিকে কীভাবে দেখেন? ছাত্ররাজনীতি মানে কিন্তু স্বেচ্ছাচারিতা নয়। যে কামরার ভেতর আবরারের ওপর বর্বরতা চালানো হয়েছে, সেখানে কোনো বইপত্র নেই। অথচ সেখানে ছাত্ররা থাকছে। অনেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে অবৈধভাবে। ছাত্রত্ব পেরিয়ে গেছে, তবু হলে থাকছে। এটা তো ঠিক নয়।
মূল প্রসঙ্গে ফিরতে চাই। আপনার সঙ্গে আলাপের উদ্দেশ্য ছিল আপনার ভেতরের মানুষটাকে এবং আপনার পরিবার সম্পর্কে জানা। বাবা সম্পর্কে তো বলেছেন। এবার মাকে নিয়ে যদি কিছু বলেন। মা আমাদের অনেক যত্ন করে লালন-পালন করেছেন। পরিবারে বাবা যে সিদ্ধান্তটা নিতেন, সেটা কিন্তু মাকে অনুসরণ করেই নিতেন। যেমন কলকাতায় আমরা ফ্রক পরে ঘুরতাম। ঢাকায় এসে সালোয়ার-কামিজ পরতে শুরু করলাম। এটি ছিল আম্মারই নির্দেশে। আব্বা ব্যবসায়ী হওয়ার কারণে অধিকাংশ সময়ই দেশের বাইরে থাকতেন। আম্মাই আমাদের দেখাশোনা করতেন।
আপনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছেন রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে। সেটা কি আপনার নিজের সিদ্ধান্ত ছিল, নাকি চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে? না না, ওটা নিজের সিদ্ধান্তেই পড়েছি। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হব, এ রকম চিন্তা ছিল না। আমার খুব অল্প বয়সে বিয়ে হয়েছে। আমার ইচ্ছাতেই আমি বিয়ে করেছিলাম, হাইস্কুলে থাকতে। তখন সারাক্ষণ পড়াশোনা নিয়ে থাকব, সে সুযোগটাও ছিল না। কারণ, আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হই, তখন আমার ছেলে দুই বছরের। তাই ইচ্ছা ছিল যত তাড়াতাড়ি পারি গ্র্যাজুয়েশন শেষ করব। মাস্টার্স করব। এ জন্যই আসলে সহজ বিষয় নিয়ে পড়া।
নিজের ইচ্ছাতেই কম বয়সে বিয়ে করেছিলেন বলছিলেন। পছন্দ কি আপনারই ছিল? হ্যাঁ, বিয়েটা আমার পছন্দেই করেছি (রোকেয়া হায়দার হেসে জবাব দিলেন)।
আপনাদের প্রথম পরিচয় হয়েছিল কীভাবে? তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল আমার স্কুলের পাশে। ভিকারুননিসা স্কুলে একটি ফাংশন করে বের হচ্ছি সেজেগুজে। খুব আনন্দের সঙ্গে চলছি। তখন এত রেস্ট্রিকশন মানার প্রবণতা ছিল না। হায়দার তখন ওখানে ঘুরছিলেন। দেখে ভালো লাগায় এসে নাম জানতে চাইলেন। তারপর প্রায়ই স্কুলের আশপাশে ঘোরাফেরা করতেন। এভাবেই পরিচয় হলো। ভালো লাগল, তাই হয়ে গেল।
এখন তো কাউকে ভালো লাগলে ছেলেমেয়েরা ফোন নম্বর জোগাড় করে। খুদেবার্তা চালাচালি হয়। তখন আপনাদের যোগাযোগটা কীভাবে হতো? তখন তো আর এগুলো ছিল না।
চিঠি বিনিময় হতো না? হ্যাঁ, চিঠি বিনিময় হতো। খুব বেশি না। অত সময় কোথায়? পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হতো।
শুভ পরিণয়টা কত দিন পরে হলো? দেড় থেকে দুই বছর পর।
প্রণয়ের প্রস্তাবটা কে দিয়েছিল আগে? অবশ্যই হায়দার আগে দিয়েছিল।
সাংবাদিকতায় কীভাবে এলেন? সাংবাদিক হব, এটা তো চিন্তাই করিনি। আমি রেডিওতে ড্রামা করি। স্বাধীনতাযুদ্ধের পর ঢাকায় যখন ফিরে আসি, তখন যেহেতু আমার রেডিও-টেলিভিশনে কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে, তাই খবর পড়া শুরু করেছিলাম। তারপর পেশা হিসেবে নিয়েছি। সাংবাদিক হতে পেরেছি কি না, জানি না।
যুদ্ধের সময় আপনি চট্টগ্রামে ছিলেন, ১৬ ডিসেম্বরের পর ঢাকায় এসেছেন। যুদ্ধকালীন চট্টগ্রামের অবস্থাটা কী ছিল? চট্টগ্রামের একটা বিধ্বস্ত অবস্থা ছিল তখন। কোথাও আগুন জ্বলছে। দুই তরফেরই খুনোখুনি হচ্ছে। পাকিস্তান সেনাবাহিনী অভিযান চালাচ্ছে। চট্টগ্রামে তখন যারা বাঙালি ছিল, তাদের মধ্যে অনেকেই অনেকভাবে বর্বরতার শিকার হচ্ছেন। তারাও কিন্তু অবাঙালিদের মারছেন, এমনও ছিল। ঘরদোর জ্বালিয়ে দিচ্ছিল। রেলওয়ে কলোনির একটি অংশ ছিল পাহাড়তলীতে। সেখানে সারা রাত আগুন জ্বলত। অস্থিরতার মধ্যে এভাবেই কেটেছে তখনকার সময়। আমি কিন্তু ১৯৭১ সালের কথা বেশি বলতে চাই না।
আপনারা চট্টগ্রামের কোন এলাকায় ছিলেন তখন? আমি চট্টগ্রামের খুলশীতে ছিলাম।
ভিন্ন প্রসঙ্গে যাই। ভয়েস অব আমেরিকায় যুক্ত হলেন কীভাবে? আমি অনুষ্ঠান করতাম এখান (ঢাকা) থেকে। ভয়েস অব আমেরিকার (ভিওএ) জন্য কিছু রেকর্র্ডিং করতাম। ১৯৭৮ সাল থেকেই চলছিল। তখন আমি বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বেতারে। তখন ভিওএ’র জন্য কিছু কিছু রেকর্ড করে পাঠাতাম। তার ১৯৭৮ কি ’৭৯ সালের দিকে খবর এলো চাকরির আবেদন করার। তারপর পরীক্ষা দিলাম। পাস করলাম। ১৯৮১ সালের অক্টোবর মাসে যুক্তরাষ্ট্রে চলে গেলাম।
আমরা যেমন এখন ভিডিও বা ভয়েস ই-মেইল বিভিন্ন জায়গায় পাঠাতে পারি, তখন পাঠানোর প্রযুক্তিটা কী ছিল? ঢাকায় ভিওএ’র একটা স্টুডিও ছিল। ১৪ নম্বর তোপখানা রোডে। সেখানেই রেকর্ড হতো। আমি গিয়ে পড়ে আসতাম। ওরা পাঠিয়ে দিত।
আপনি বিশ্বের অনেক ক্ষমতাবান ও সমাদৃত মানুষের ইন্টারভিউ নিয়েছেন। মাদার তেরেসার সঙ্গেও আপনার ভালো সম্পর্ক ছিল। ওনার সঙ্গে আপনার পরিচয় কীভাবে? আমি ঢাকায় থাকতে কারিতাসে কাজ করতাম। ১৯৭৪ সালের মাঝামাঝি থেকে ১৯৮১ পর্যন্ত আমি কারিতাস বাংলাদেশে কাজ করেছি। এখানে শিশুদের জন্য মাদার তেরেসার অর্থায়নে কাজ হতো। তিনি এখানে এসেছিলেন নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর। ছোটবেলায় কলকাতায় এই সম্মেলনেও তাকে দেখেছিলাম। তখন আমার বয়স পাঁচ কি ছয় বছর। সেইভাবে ওনাকে জানতাম, চিনতাম। ১৯৮৭ সালে তিনি যখন ওয়াশিংটনে গেলেন, তখন আমি তার সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম।
ড. মুহাম্মদ ইউনূস, কৈলাস সত্যার্থীর সাক্ষাৎকার নিয়েছেন... হ্যাঁ, তারা নোবেল পাওয়ার পর সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম।
বাংলাদেশের গণমাধ্যমকে কীভাবে মূল্যায়ন করবেন? বাংলাদেশের গণমাধ্যম পুরো নিরপেক্ষ নয়। কিছু বিধিনিষেধ নিশ্চয়ই আছে। আবার প্রেস ফ্রিডম যেটাকে বলে, সেটা আমি দেখেছি আছে, আবার নেই। সবার মধ্যেই একটা বিষয় কাজ করে, এই খবরটি দেওয়া যাবে কি না? তারা সেটাকে ওজন করে দেখে যে, এটা দিলে আমার কোনো সমস্যা হবে কি না। এটা কিন্তু আমাদের ভয়েস অব আমেরিকায় একেবারেই নেই। যদিও এটা সরকারি অর্থে চলে। বাংলাদেশে আছে অবাধ স্বাধীনতা। সবাই অনেক কথা বলতে পারে। তারপরও বেশি দলীয়করণ হয়ে গেছে। হয় আমাকে বিরোধী দলের হতে হবে, নয় সরকারি দলের হতে হবে। এটা ঠিক না। আমি হয়তো এখানে থাকলে এটা করতে পারতাম না।
উন্নত দেশ বা উন্নয়নশীল দেশের সঙ্গে আমাদের গণমাধ্যমের স্বাধীনতার বিষয়টিকে তুলনা করতে বললে কী বলবেন? যেখানে গণতন্ত্র থাকে, সেখানে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা থাকা উচিত। দুঃখজনক হলেও বলতে হয়, গণমাধ্যমের স্বাধীনতাটা আসলে নেই। অনেক দেশেই নেই। বাংলাদেশেও এখনো অনেক চিন্তা করেই গণমাধ্যম কথা বলে। গণমাধ্যমের স্বাধীনতাটা কিন্তু মূল্যবান জিনিস, গণতন্ত্রমনা সাংবাদিকদের জন্য। এটা রক্ষা করার দায়িত্ব সরকারের। এটা নিশ্চিত করা উচিত। যেটা সচরাচর হয় না।
এখন তো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের জয়জয়কার। অনেক সময় আমরা যোগাযোগমাধ্যম ও গণমাধ্যমকে এক করে ফেলছি। আবার একটি আরেকটির পরিপূরক হিসেবেও কাজ করছে। অবশ্যই।
প্রশ্ন হচ্ছে, অনেকে বলেন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ফলে গণমাধ্যমের গুরুত্ব কমেছে। আপনি কীভাবে দেখেন? ঠিক তা নয়। প্রিন্ট মিডিয়া আর ইলেকট্রনিক মিডিয়া, দুটোই থাকবে। তবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম কিন্তু সব কিছুকে ছাপিয়ে যাচ্ছে। আমি চট করে একটা কিছু বলে দিতে পারি, ছড়িয়ে দিতে পারি। তথ্য সরবরাহ আপনি আর বন্ধ রাখতে পারেন না। যত যা-ই করুক, এ মুহূর্তে আমি বলতে পারি, জাতিসংঘের সামনে বাংলাদেশের দুটো দলের মধ্যে মারামারি হয়েছিল। এই তথ্য কোথাও যেত না, যদি ফেসবুক না থাকত।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের গ্রহণযোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন আছে... কিছুটা প্রশ্ন তো আছেই। কে কীভাবে দেখছে, এটা তার ব্যাপার। কিন্তু আমার মনে হয়, চিত্রটা দেখলে বোঝা যায়। তথ্যকে বিকৃত করতে চায় অনেকে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমকে অনেকটা বিকৃত করা যায়। যারা এর সঠিক ব্যবহার জানে, তারা ঠিকই ধরে নিতে পারবে ভুলত্রুটিটা কোথায়।
আপনারা যখন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থেকে কোনো সংবাদ জানতে পারেন, তখন এর সত্যতা কীভাবে যাচাই করেন? আমাদের যাচাই-বাছাই করার জন্য নির্দিষ্ট নির্দেশিকা আছে। এত দিনের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি, দুটি বা তিনটি সোর্স থেকে খবরের সত্যতা যাচাই করেই আমরা প্রচার করি।
প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতেই উঠে গেলেন। বললেন, ‘আর এক মিনিটও না। অনেক সময় হলো। লোকজন অপেক্ষা করছে।’ ঘড়িতে তাকিয়ে দেখি কুড়ি মিনিট হতে চলল। বললাম, শেষ একটি প্রশ্ন, সাংবাদিক হওয়ার জন্য কোনটা বেশি প্রয়োজন বলে মনে করেন? শ্রোতাদের মধ্যে হারিয়ে যেতে যেতে বললেন, সততা ও নিষ্ঠা।
সংবাদটি শেয়ার করুন
গণমাধ্যম বিভাগের সর্বাধিক পঠিত
গণমাধ্যম এর সর্বশেষ

সাংবাদিক নেতা রমিজ খানের ইন্তেকাল, বিএফইউজের শোক

ঈদের ছুটি না পাওয়া গণমাধ্যমকর্মীদের যথাযথ সুযোগ-সুবিধা প্রদানের দাবি বিএফইউজের

প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ ও প্রতিবেদকের বক্তব্য

নড়াইল জেলা সাংবাদিক ইউনিটি-ঢাকার নতুন কমিটি গঠন

সাংবাদিক মিনার মাহমুদের ১২তম মৃত্যুবার্ষিকী আজ

সাংবাদিক সাব্বিরের ওপর নৃশংস হামলায় ঢাকাস্থ গাজীপুর সাংবাদিক ফোরামের নিন্দা

বাংলানিউজকর্মী মিথুনের ক্যানসার চিকিৎসায় এগিয়ে এলো বসুন্ধরা ফাউন্ডেশন

আজ ভোরের পাতা সম্পাদকের পিতার চতুর্থ মৃত্যুবার্ষিকী

সাংবাদিক মোহসিন কবিরকে মারধরের ঘটনায় ডিআরইউর প্রতিবাদ





































