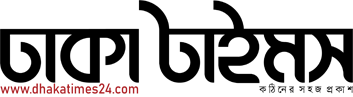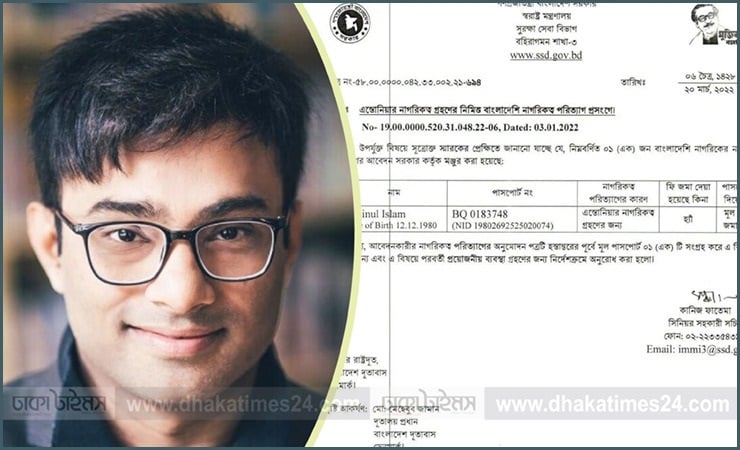ফিরে দেখা ২০২৩: আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সংকটের বছর

বিদায়ী বছর ২০২৩ সাল ছিলো আন্তর্জাতিক রাজনীতির সংকটের বছর। গত দুই দশকে এমন গুরুত্বর সমন্বিত সংকট বিশ্ববাসী আর দেখেনি। যা আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, বাণিজ্য, সামরিক ও বৈশ্বিক খাদ্য নিরাপত্তাকে হুমকির মুখে ফেলেছে। এর আগে চলতি শতকের প্রথম দশকের শেষ প্রান্তিকে মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকাজুড়ে আরব বসন্ত শুরু হলে এমন সংকট দেখেছিল পৃথিবী। কিন্তু আরব—আফ্রিকা সংকটে বিশ্বকে যতটা প্রভাবিত না করেছে তার থেকে কয়েকগুণ বেশি প্রভাবিত করেছে রাশিয়া—ইউক্রেন যুদ্ধ এবং বছরের শেষ প্রান্তিকে এসে শুরু হওয়া হামাস—ইসরায়েলে সংঘাত। এই দুই যুদ্ধকে ঘিরে আন্তজার্তিক পরাশক্তিগুলো ছাড়াও পৃথিবীর সব দেশ দ্বিপক্ষীয় আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও নিজ দেশের খাদ্য নিরাপত্তা এমনকি সামরিক—রাজনৈতিক নিরাপত্তা নিয়েও টানাপোড়েনের মধ্যে পড়ে। বিশেষত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ, চীন, রাশিয়া, ভারত ও মধ্যপ্রাচ্য সরাসরি এই যুদ্ধের কোনো না কোনো পক্ষে দৃশ্যমান ভূমিকায় থেকে সংকট বাড়িয়েছে। এছাড়া তাইওয়ান দ্বন্দ্ব, ভারতের মনিপুর সংকট, শিখ নেতাদের হত্যা ও হত্যাচেষ্টা, আফ্রিকায় দফায় দফায় সামরিক বিদ্রোহ আন্তজার্তিক সম্পর্ককে প্রভাবিত করেছে। তৈরি করেছে নানামুখী সংকট ও বৈরিতা। এসব ঘটনায় চোখ বুলিয়ে দেখে নেয়া যাক বিদায়ী বছরে আন্তর্জাতিক রাজনীতি, বাণিজ্য, নিরাপত্তা ও সম্পর্ক কতটুকু সংকটের মুখোমুখি হয়েছে এবং কেন, কীভাবে হয়েছে।
রাশিয়া—ইউক্রেন যুদ্ধ: সংকটে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক
রাশিয়া ও ইউক্রেন যুদ্ধের শুরুটা হয়েছিলো মূলত ২০১৩ সালে। ওই বছরের নভেম্বরে রাশিয়াপন্থী ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্ট ভিক্টর ইয়ানুকোভিচ ইউরোপকে পাশ কাটিয়ে রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে পশ্চিম ইউক্রেনে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। যা ইউরো বিপ্লব হিসেবে চিহ্নিত। রাজধানীর কিয়েভে সরকার বিরোধী বিক্ষোভে ৭৭ জন প্রাণ হারানোর পর ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) পক্ষ থেকে পোল্যান্ড, জার্মানি ও ফ্রান্সের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের মধ্যস্ততায় সরকার ও বিরোধী দলের সমঝোতা হয়। সমঝোতার প্রেক্ষিতে প্রেসিডেন্ট ইয়ানুকোভিচ মতা ছেড়ে নতুন নির্বাচনের ঘোষণা দেন। এখান থেকেই মূলত সংঘাতের শুরু। এই ঘটনার পর ইউক্রেনের তিন গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল ক্রিমিয়া, দনবাস অঞ্চলের লুহানস্ক ও দোনেস্ক নিজেদের স্বাধীন ঘোষণা করে। ২০১৪ সালের মার্চে রুশপন্থী বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সঙ্গে যোগ দিয়ে ক্রিমিয়া উপদ্বীপ সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে নেয় রাশিয়া। এরপর গণভোটের মাধ্যমে ক্রিমিয়া রাশিয়ার অন্তর্ভূক্ত হয়। তখনই ধারণা করা হয় লুহানস্ক ও দোনেস্কের ভাগ্যে তাই ঘটবে যা ক্রিমিয়ায় ঘটেছে। প্রাথমিকভাবে মিনস্ক চুক্তির মাধ্যমে সেই ধাক্কা মোকাবিলা করে ইউক্রেন। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন পক্ষ; বিশেষ করে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সহায়তায় পূর্ব ইউক্রেনের বিবাদমান পক্ষগুলোর সঙ্গে চুক্তিতে পৌঁছে কিয়েভ। রাশিয়াও ওই চুক্তিতে সই করে। ২০১৫ সালের ফ্রেবুয়ারিতে বেলারুশের রাজধানী মিনস্কে স্বারিত চুক্তির অন্যতম প্রধানতম শর্ত ছিল—পূর্ব ইউক্রেন থেকে সামরিক স্থাপনা, সামরিক সরঞ্জাম ও ভাড়াটে সেনাদের সরিয়ে নেওয়া, বিচ্ছিন্নতাবাদী অঞ্চলগুলোকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া, নিজস্ব পুলিশ বাহিনী গঠনে অনুমতি, স্থানীয় প্রসিকিউটর ও বিচারক নিয়োগ করার ক্ষমতা প্রদান এবং স্থানীয় নির্বাচনের জন্য বিদ্রোহী নেতাদের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করে সমাধানে পৌঁছার চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। কিন্তু চুক্তি বাস্তবায়ন না হওয়ায় পূর্ব ইউক্রেনে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ বাড়তে থাকে। অন্যদিকে ইউরোপীয় ও পশ্চিমা মিত্রদের সামরিক জোট ন্যাটোতে যোগ দেওয়ার চেষ্টায় ইউক্রেনের এগিয়ে চলা শঙ্কিত করে তোলে পুতিনকে। মস্কোর নাকের ডগায় ন্যাটোভুক্ত একটি দেশ যুক্ত হলে তা যে, পশ্চিমাদের ডিঙ্গিয়ে চলা পুতিনের রাশিয়ার নিরাপত্তার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সেজন্য রাশিয়াও উপযুক্ত সময় ও সুযোগ খুঁজছিলো ইউক্রেনকে কীভাবে দুর্বল করা যায়, ন্যাটো থেকে ফেরানো যায়, নিজের নিরাপত্তা আরও সুরক্ষিত করা যায়। ইউক্রেন থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চাওয়া স্বঘোষিত গণপ্রজাতন্ত্রী দোনেৎস্ক ও গণপ্রজাতন্ত্রী লুহানস্ককে ২০২২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের ঘোষণা দেন পুতিন। এই দুটি অঞ্চলই রাশিয়াপন্থী বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রণে। এই সুযোগটাই নিয়েছেন পুতিন। একই সঙ্গে বহিঃরাষ্ট্রে ইউক্রেনের আধিপত্য ও রুশ জাতিগত সংখ্যালঘু (স্বাধীন দোনেস্ক ও লুহানস্কে সংখ্যাগুরু) নাগরিকদের ওপর হামলা ও নির্যাতনে অভিযোগে ইউক্রেনের কেন্দ্রীয় সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করে রুশ সামরিক বাহিনী। সেই শুরু... যা এখনো অবধি চলছে। টানা এক বছর লড়াই চালিয়ে যাওয়ার পর চলতি বছর ইউক্রেনে বড় বড় সফলতা অর্জন করে রাশিয়া। এরমধ্যে নিজ প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর সঙ্গে ভাড়াটে যোদ্ধাদল ভাগনার প্রধানের দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে এলে কিছুটা বিব্রত অবস্থায় পড়লেও পুতিনের ঘুরে দাঁড়াতে সময় লাগেনি। এমনকি শেষ পর্যন্ত ভাগনার প্রধানের ভাগ্যে নির্মম মৃত্যু এসে ধরা দেয়। একই সঙ্গে ইউক্রেন, যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে লড়াই করে টিকে থাকতে হচ্ছে পুতিনকে। ক্রমাগত হামলা, লড়াই, খুনোখুনি ইউরোপের নিরাপত্তাকে হুমকির মুখে ফেলেছে। ইউরোপকে বাঁচানোর পশ্চিমা নেতৃত্বাধীন সামরিক জোটে যোগদানে ইউরোপের বাকী দেশগুলো মধ্যে প্রতিযোগীতা শুরু হয়ে গেছে পুতিনের রাশিয়ার ভয়ে। অন্যদিকে রাশিয়ার দাবি দেশটির সীমান্তবর্তী কোনো ইউরোপীয় দেশকে যেন ন্যাটোভুক্ত করা না হয়। এরপক্ষে রাশিয়ার শক্তিশালী যুক্তিও রয়েছে। রাশিয়ার সীমান্তে ন্যাটোভুক্ত দেশ থাকলে সেখানে অস্ত্র ও সৈন্য সমাবেশ করে যেকোনো সময় রাশিয়ার বিরুদ্ধে সম্মিলিত আগ্রাসন চালানো সহজ হবে বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা। সেজন্যই কিয়েভের ন্যাটোভুক্তিকে আপত্তির চোখে দেশে মস্কো। দুই দেশের বা রাশিয়ার বিপরীতে ইউরোপ ও পশ্চিমাদের এই টানাপোড়েন ভুগিয়ে চলছে পৃথিবীর অন্যান্য দেশকেও। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের গতি ঠিক রাখতে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হয়েছে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে। বিশেষ বাংলাদেশের মতো দেশগুলোকে ভারি বেগ পোহাতে হচ্ছে ইউক্রেন—রাশিয়ার যুদ্ধের তালে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ঠিক রাখতে। উঠতি শক্তিধর ভারত সরকারও প্রথম প্রথম পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞাকে এড়িয়ে রাশিয়ার সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য সম্পর্ক এগিয়ে নিলেও পশ্চিমাদের সঙ্গেও সমানতালে ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা করে গেছে। বাংলাদেশ রাশিয়ার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা এখন স্বীকৃত বিষয়। এরমধ্যেও বাংলাদেশকে জাতিসংঘে একাধিক প্রস্তাবে ইউক্রেন ইস্যুতে রাশিয়ার বিরুদ্ধে ভোট দিতে হয়েছে। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক রক্ষায় স্বাধীনতার পর ইউক্রেন—রাশিয়া ইস্যুতেই বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে বলে মনে করছেন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষকরা। এছাড়াও বিশ্বব্যাপী এই যুদ্ধের অর্থনৈতিক প্রভাব মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে মানুষের জীবনযাপনকে। করোনা মহামারীর ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই ইউক্রেন—রায়িশার যুদ্ধ বিশ^ব্যাপী খাদ্য ঘাটতি তৈরি করে। পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম শস্য রপ্তানির দেশ ইউক্রেন। অপরদিকে রাশিয়াও বিশ^ব্যাপী খাদ্য রপ্তানির শীর্ষ দেশগুলোর অন্যতম। এছাড়া খাদ্য উৎপাদনের অন্যতম প্রধান কাঁচামাল সার রপ্তানিতে রাশিয়া শীর্ষে। পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞার কারণে যা স্থবির হয়ে পড়ে। রাশিয়াও পাল্টা পদক্ষেপ হিসেবে কৃষ্ণ সাগর দিয়ে ইউক্রেনের খাদ্য রপ্তানি বাধাগ্রস্ত করে। এর ফলে সবচেয়ে বেশি বিপাকে পড়ে ইউরোপের দেশ স্পেন, ইতালি নেদারল্যান্ডসসহ অনেক দেশ। এছাড়া মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকা চরম খাদ্য সংকটে পড়ে যায়। যুদ্ধের শুরুর দিকে ইউক্রেনের দুই কোটি টন খাদ্যশস্য আটকে পড়েছিল কৃষ্ণ সাগরে। ফলে মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকার যেসব দেশ ইউক্রেন থেকে আমদানি করা খাদ্যের ওপর নির্ভর করে, সেসব দেশে চরম খাদ্যাভাব দেখা দেয়। জাতিসংঘের হিসাবে বিশ্বের ৩৮টি দেশে চার কোটি ৪০ লাখ মানুষ জরুরি অবস্থাকালীন ক্ষুধার মুখোমুখি হয়েছে। এছাড়া বিশ্বব্যাপী খাদ্যের দাম গড়ে ৩০ শতাংশ পর্যন্ত বেড়ে যায়। মূল্যস্ফীত ছাড়িয়ে যায় অতীতের সব রেকর্ড। পরবতীর্তে তুর্কিয়ে ও জাতিসংঘের মধ্যস্ততায় ইউক্রেন—রাশিয়ার শস্য রপ্তানি চুক্তি হলে কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আসে খাদ্য মূল্যস্ফীতি। কিন্তু পশ্চিমাদের ক্রমাগত রাশিয়ার বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান এবং ইউক্রেনকে অস্ত্র, বোমা ও অর্থ দিয়ে সহায়তার কারণে কয়েক দফা বাড়ানোর পর রাশিয়ার আর সেই চুক্তির মেয়াদ বাড়ায়নি। ফলে মূল্যস্ফীতির লাগাম টেনে ধরা যায়নি। যা চলতি বছরেও বিদ্যমান ছিল। আগামী বছরেও কমার সম্ভাবনা ক্ষীণ। বিশ্বব্যাপী খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় পড়লেও জার্মানসহ ইউরোপের অনেক দেশ রাশিয়ার ওপর জ্বালানি নির্ভরতার কারণে অনেক বেশি সংকটে পড়ে। তাদের সংকট হয় চতুর্মুখী। একদিকে জোটগত অবস্থান ইউক্রেনের পক্ষে অন্যদিকে নিজ দেশের শিল্প ও মূল্যস্ফীতি ঠিক রাখতে রাশিয়ার সাথে বাণিজ্য সম্পর্ক রক্ষা করা; উভয় সংকটের মুখে পড়ে ইউরোপের অনেক দেশ। যার ফলে পশ্চিমাদের নিষেধাজ্ঞার অনেকটাই মানেনি খোদ সহযোগী ইউরোপীয় দেশগুলো। এমনকি বাধ্য হয়েছে পুতিনের বাতলে দেওয়া পদ্ধতিতে লেনদেন করতে। ফলে কোনঠাসা করার লক্ষ্যে দেওয়া নিষেধাজ্ঞাই রাশিয়ার অর্থনীতি আরও চাঙ্গা করে। ডলারের বিপরীতে রুবলের দাম ওঠে সর্বকালের সবোর্চ্চ মাত্রায়। অন্যদিকে তেল উৎপাদনকারী দেশগুলোর জোট ওপেক এর সহায়তায় রাশিয়া তেল উৎপাদন কমিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের তেল ভান্ডারও খালি করে দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র বারবার তেল উৎপাদন বৃদ্ধিতে তাগাদা দিলেও কেউ তাদের আহ্বানে সাড়া দেয়নি। মধ্যপ্রাচ্যে দীর্ঘদিনের বড় মিত্র সৌদি আরবকেও রাজি করাতে পারেনি বাইডেন প্রশাসন। ফলে বৈশ্বিক ঘাটতির কারণে বিশ^ব্যাপী জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধিও মূল্যস্ফীতি বাড়াতে বড় ভূমিকা রেখেছে। এমনকি ইউরোপের মূল্যস্ফীতির প্রধান কারণ রাশিয়া থেকে জ্বালানি প্রাপ্তির অনিশ্চয়তা।
তাইওয়ান: তলানিতে বেইজিং—ওয়াশিংটনের সম্পর্ক
এখনকার আধুনিক চীন প্রতিষ্ঠা হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায়। বর্তমান কমিউনিস্ট পাটি তৎকালীন হান রাজবংশীয় সরকার হটিয়ে চীনের মূল ভূখণ্ডের ক্ষমতা দখল করে। ক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ হয়ে তখনকার স্বীকৃত বৈধ সরকার দক্ষিণ চীন সাগরের তাইওয়ানে পালিয়ে যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জয়লাভের পর পরাজিত জাপানের কাছ থেকে এই দ্বীপের মালিকানা পেয়েছিলো চীনারা। দেশটিতে দীর্ঘদিনের গৃহযুদ্ধের কবলে পড়ে ক্ষমতা হারিয়ে হান সরকার তাইপে শহরে তৎকালীন ‘চীন প্রজাতন্ত্র’ সরকারের রাজধানী স্থাপন করে।
আন্তর্জাতিকভাবে এই সরকারই পুনরায় বৈধতা এবং স্বীকৃতি লাভ করে। কিন্তু বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর রাশিয়ার সঙ্গে মিত্র শক্তি তথা পশ্চিমাদের দূরত্ব তৈরি হলে গণচীন তথা কমিউনিস্ট পাটি প্রতিষ্ঠিত গণপ্রজাতন্ত্রী চীন সরকারকে স্বীকৃতি দেয়। মার্কিনিদের প্রত্যক্ষ মদদে ১৯৭১ সালে জাতিসংঘের স্বীকৃতি এবং নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যপদ লাভ করে। এই স্বীকৃতির পর তাইপে সরকার পুরো চীনের পরিবর্তে তাইওয়ানের নিয়ন্ত্রণকারী কতৃর্পক্ষ হয়ে ওঠে। এর আগ পর্যন্ত উভয় সরকারই নিজেদেরকে সম্পূর্ণ চীনের বৈধ রাজনৈতিক সরকার দাবি করে আসছিল। কিন্তু পশ্চিমাদের কাছে মূল ভূখণ্ডের বিশাল জনগোষ্ঠীর নেতৃত্ব দখলকারীরা কৌশলগত কারণে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এরপরই মূলত তাইওয়ানের পরিবর্তে চীনের উত্থান ঘটে। কিন্তু আধুনিক চীনের কমিউনিস্ট সরকার আস্তে আস্তে তার আসল রূপে ফিরতে শুরু করে। নানান বিষয়ে পশ্চিমাদের সঙ্গে বাদানুবাদ ও সংঘষে জড়িয়ে পড়ে। যেই রাশিয়ার মোকাবিলায় গণচীনকে স্বীকৃতি দেওয়ার পৃষ্ঠপোষকতা মার্কিনরা করেছিলো সেই রাশিয়াই এখন চীনের প্রধান মিত্র। চীনের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শত্রুতার প্রধান কারণ তাইওয়ান ভূখণ্ড। কৌশলগত কারণে গণচীনকে স্বীকৃতি দিলেও তাইপে সরকার ও তাইওয়ান ভূখণ্ডকে দেওয়া সব ধরনের সহযোগিতা অব্যাহত রেখেছে যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু চীন সরকার তাইওয়ানকে নিজেদের একটি প্রদেশ দাবি করে, যদিও সেখানে তাদের কোনো কর্তৃত্ব নেই। অন্যদিকে কূটনৈতিকভাবে যুক্তরাষ্ট্র একনীতিতে সমর্থন জানালেও তাইওয়ানে চীনের বাড়াবাড়িকে সমর্থন করে না। যার ফলে এই নিয়ে দুই দেশের সম্পর্কের টানাপোড়েন চলছে কয়েক দশক ধরে। চীন মূলত প্রশান্ত মহাসাগরে আমেরিকার উপস্থিতি নিয়ে শঙ্কিত। সাগরের বুকে চীনের গা ঘেঁষে বিষফোঁড়ার মতো হয়ে দাঁড়িয়ে আাছে স্বশাসিত তাইওয়ান। চীনের সমুদ্র উপকূল থেকে ১৮০ কিলোমিটার দূরত্বের আংশিক স্বীকৃত ছোট্ট এই দেশটি কৌশলগত কারণে উভয় দেশের কাছেই গুরুত্বপূর্ণ। ইউক্রেনে রাশিয়ার অযৌক্তির দাবির দূরবর্তী ভিত্তি থাকলেও তাইওয়ানকে চীনের অংশ মনে করার পেছনে চীনাদের ঐতিহাসিক শক্তিশালী যুক্তি নেই। তথাপিও বিশ্বব্যাপী সেমি কন্ডাক্টর চিপস উৎপাদনে অর্ধেক বাজার দখলে রাখা মাত্র ৩৫ হাজার বর্গকিলোমিটারের ভূখণ্ডের নিয়ন্ত্রণ নিয়েই চীনের উদ্বেগ বেশি। কেননা মৌলিকভাবে যুক্তরাষ্ট্র এক চীন নীতিতে এখনো পর্যন্ত অটল থাকলেও তাইওয়ানে চীনের হস্তপে সমর্থন করে না। গোপনে তাইওয়ানকে অস্ত্র থেকে শুরু করে নানাভাবে সহযোগিতা করে আসছে। সর্বশেষ গত আগস্টে প্যারাগুয়ে সফরকালে তাইওয়ানের ভাইস প্রেসিডেন্ট উইলিয়াম লাই দুই দফা যুক্তরাষ্ট্রে যাত্রা বিরতি করেন। এর আগে এপ্রিলে একই কায়দায় মধ্য আমেরিকা সফরকালে যুক্তরাষ্ট্রে মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদের স্পিকার কেভিন ম্যাকার্থির সঙ্গে বৈঠক করেন তাইপে প্রেসিডেন্ট। গুয়াতেমালা সফরকালে তিনিও যুক্তরাষ্ট্রে দুইদফা যাত্রাবিরতি নেন।
যা চীন ভালোভাবে নেয়নি। দুইটি ঘটনাকেই চীন উসকানিমূলক আখ্যা দিয়ে দফায় দফায় দণি চীন সাগরে তাইওয়ান প্রণালিতে সামরিক মহড়া দিয়ে উত্তেজনা তৈরি করে। এমনকি সেসময় সীমান্তে পিপলস লিবারেশন আর্মির (পিএলএ) কমান্ড পরিদর্শনে গিয়ে দেশটির সেনাবাহিনীকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিতে বলেন চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। এর আগে গত বছরের আগস্টের শুরুতে আকস্মিকভাবে তাইওয়ান সফরে যান যুক্তরাষ্ট্রের নিম্ন—কক্ষের (হাউস অফ রিপ্রেজেনটেটিভ) স্পিকার ন্যান্সি পেলোসি। বৈঠক করেন দেশটির প্রেসিডেন্ট সাই ইং ওয়েন এর সঙ্গে। যেটা ছিলো গত দুই যুগেরও বেশি সময়ের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পযার্য়ের কোনো কর্মকতার্র তাইপে সফর।
এই সবগুলো ঘটনা চীন—যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ককে ইতিহাসের সবচেয়ে তলানিতে পৌঁছে দেয়। বিদায়ী বছরেই চীনের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক সহযোগিতামূলক একটি চুক্তি হওয়ার কথা ছিলো। বছরের মাঝামাঝি দফায় দফায় প্রকাশ্যে—গোপনে বেইজিং সফর করেন মার্কিন অর্থমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী। কিন্তু তাইওয়ানের দুই শীর্ষ নেতার অনির্ধারিত যুক্তরাষ্ট্র সফর সবকিছু ভেস্তে দেয়। যা আধুনিত চীন প্রতিষ্ঠার পর যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সবচেয়ে বৈরি সম্পর্ক তৈরি করে। এই সময়ে চীন সরকার রাশিয়ার সঙ্গে যৌথভাবে চীন সাগরের তাইওয়ান প্রণালিতে দফায় দফায় সামরিক মহড়া দিয়ে উত্তেজনা তৈরি করে। শঙ্কা তৈরি করে এই বুঝি আরেকটি যুদ্ধ শুরু হবে। সেটা হলে নিশ্চিত আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এখনকার চেয়েও খারাপ অবস্থায় পৌঁছাতো। তাইওয়ান আন্তর্জাতিকভাবে ব্যাপক বা আনুষ্ঠানিক স্বীকৃত না হলেও অনেক দেশ অরাষ্ট্রীয়ভাবে তাইওয়ানের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক রাখে। বাংলাদেশের সঙ্গেও দেশটির বাণিজ্য সম্পর্ক রয়েছে। আন্তর্জাতিক যেসব সংস্থায় চীন নেই সেসব সংস্থায় রাষ্ট্র হিসেবে তাইওয়ান সদস্য। অন্যগুলোতে অরাষ্ট্রীয়ভাবে রয়েছে তাইওয়ানের অবস্থান। এমন অবস্থায় তাইওয়ানে আরেকটি যুদ্ধ শুরু হলে গোটা বিশ্ব সরাসরি বিভক্ত হয়ে যেতো কোনো সন্দেহ নেই। এক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়া তথা বাংলাদেশের মতো দেশগুলো বেশি সংকটে পড়ে যেতো। যদিও সেই অবস্থা থেকে কিছুটা পরিত্রাণ পাওয়া গেছে। গত নভেম্বরে ওয়াশিংটনে ‘বাইডেন—শি’র আলোচিত বৈঠকে পুনরায় সামরিক যোগাযোগ চুক্তি সইয়ের ব্যাপারে দুই নেতা একমত হয়েছেন। যেটাকে বাইডেন ইতিহাসের সবচেয়ে ফলপ্রসু বৈঠক আখ্যা দিয়েছেন।
আফ্রিকা সংকট: ইউক্রেন থেকে নজর সরানোর চেষ্টা?
তাইওয়ান সংকট চলাকালীন হঠাৎ করেই রাজনৈতিক দৃষ্টি চলে যায় আফ্রিকায়। জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহে মধ্য—পশ্চিম আফ্রিকার দেশ নাইজারে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক সরকার ভেঙে মতা দখল করে দেশটির সামরিক বাহিনী। অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেন দেশটির প্রেসিডেন্সিয়াল গার্ডের প্রধান জেনারেল আব্দুর রহমান তিয়ানি। তিনি নিজেকে দেশটির অন্তর্বতীর্কালীন প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করেন। মতা দখলের পর সামরিক বাহিনীর সমর্থকরা নাইজার ও রাশিয়ার পতাকা হাতে নিয়ে আনন্দ উদযাপন করেছে। অভ্যুত্থান কার্যকলাপে স্পষ্টতই বুঝা যায় রাশিয়ার পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতায় এই অভ্যুত্থান ঘটেছে। এমনকি নাইজার সামরিক সরকার রাশিয়ার ভাড়াটে যোদ্ধাদল ভাগনারের সহযোগিতা কামনা করে। যারা আগে থেকেই মালি ও বুরকিনা ফাসোতে সামরিক সরকারের সহযোগি হয়ে যুদ্ধে লিপ্ত। এমন অবস্থায় আফ্রিকা মহাদেশের পশ্চিমাঞ্চলীয় জোট ‘দ্য ইকোনমিক কমিউনিটি অব ওয়েস্ট আফ্রিকান স্টেটস’ (ইসিওডব্লিউএএস বা ইকোওয়াস) এক জরুরি শীর্ষ সম্মেলন করে বাজুমকে এক সপ্তাহের মধ্যে পুনর্বহাল করার দাবি জানায়। অন্যথায় ব্লকটি সাংবিধানিক শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে সামরিক পদেপের হুমকি দেয়। কিন্তু নাইজারের সাধারণ মানুষ খুব সম্ভবত এই অভ্যুত্থানে খুশিই হয়েছিলো। যুগের পর যুগ ধরে আফ্রিকার দেশগুলোকে চুষে খাচ্ছি ইউরোপের পরাশক্তিগুলো। নাইজারের মূল্যবান খনিজ সম্পদে ফ্রান্স সরকার একচেটিয়া বাণিজ্য চালিয়ে আসছে দেশটির স্বার্থের বিরুদ্ধে থেকে। গণতান্ত্রিক সরকার সে বিষয়ে শক্তিশালী ভূমিকায় তখনো যেতে পারেনি। সামরিক সরকার এসেই ফ্রান্সের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণা দেয়। এতে করে সামরিক সরকারের জনপ্রিয়তা বেড়ে যায়। তবে পশ্চিমা শক্তিও বসে থাকেনি। নানান নিষেধাজ্ঞা ও সহযোগিতা সম্পর্ক স্থগিত করতে থাকে তারা। এরই মধ্যে শুরু হয় ফিলিস্তিন সংকট।
ফিলিস্তিন: সংকটে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক মানবিকতাবোধ
মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন আধিপত্যবাদের কৌশলের অংশ হিসেবে ইসারায়েলের সঙ্গে যখন সৌদি আরব শান্তিচুক্তির দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যায়, ঠিক সেই মুহূর্তে তেল আবিবে মুহুর্মুহু রকেট হামলা চালায় গাজার নেতৃত্বে থাকা হামাস সরকারের সশস্ত্র শাখা। ফিলিস্তিন স্বাধীনতার প্রশ্নে গোটা বিশ্ব এখন দ্বিধাবিভক্ত। তুর্কিয়ে প্রেসিডেন্ট এ নিয়ে খুব আক্ষেপ করেন। গোটা বিশ্ববাসী আজকে দুয়েকটি দেশের কাছে জিম্মি। জাতিসংঘে তাদের (যুক্তরাষ্ট্র) একটি ভোট পৃথিবীর সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশের প্রতিনিধিত্বকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিচ্ছে। প্রতিমুহূর্ত মৃত্যুর মিছিলে যুক্ত হচ্ছে শত শত মানুষ। কোনো পরিসংখ্যানই শেষ কথা হচ্ছে কয়েক মিনিটের জন্যও। সর্বশেষ মোট মৃত্যুর হিসাবকেও যুদ্ধদিনের হিসাবে ভাগ করি, তাহলে দেখা যায় প্রতিদিন গড়ে ২৬০ মানুষকে হত্যা করছে দখলদার পাশবিক ইসরায়েলি বাহিনী। ফিলিস্তিনিদের মৃত্যুতে বিশ্বব্যাপী মানবতার চাষ করা পশ্চিমাদের বিবেকবোধ জেগে ওঠে না। আরব বিশ্ব, মুসলিম বিশ্ব আগের যে কোনো সময়ের তুলনায় ঐক্যবদ্ধ হলেও দৃশ্যমান কোনো সফলতা আনতে পারছে না দুয়েকটি দেশের কারণে। পশ্চিমা বলয়ের বিরোধী রাষ্ট্রগুলো ফিলিস্তিনের পক্ষে কথা বললেও তাদের মিত্রদেশগুলো মানবতার পক্ষে খুব একটা আওয়াজ তুলছে না। যে কারণে নিজ দেশে প্রতিবাদের মুখে পড়লেও ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর যুদ্ধাংদেহী মনোভাব কমছেই না। বাড়িয়ে তুলছে পৃথিবীব্যাপী মানবিকতা, নিরাপত্তা, বাণিজ্য, ও রাজনৈতিক সম্পর্কের জটিলতা।
ভারত—কানাডার তিক্ততা: বৈরিতার ছাপ বাইডেন প্রশাসনেও
গত জুনে কানাডা ভারতীয় নাগরিক হরদীপ সিং নিজ্জার হত্যার শিকার হন। কানাডার প্রধানমন্ত্রী নিজ দেশের পার্লামেন্টে এই ঘটনার জন্য সরাসরি ভারত সরকারকে দায়ী করেন। এ নিয়ে চলতে থাকে দুই দেশের তুমুল বাক্য বিনিময়। এক পর্যায়ে উভয় দেশ পরস্পরের রাষ্ট্রদূত হাইকমিশন কর্মকর্তাকে প্রত্যাহারের নির্দেশ দেয়। একই সঙ্গে নিজ দেশের কর্মকর্তাকে দেশে ফিরিয়ে নেয়। মোটকথা কানাডা—ভারত পারস্পরিক কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে। ভারত অস্বীকার করলেও কানাডা সরকার বলছে ওই হত্যাকাণ্ডে ভারত সরকার রাষ্ট্রীয়ভাবে দায়ী। অন্যদিকে ভারত বলছে, নিজ্জার খালিস্তানপন্থী বিচ্ছিন্নতাবাদী সন্ত্রাসী। তাকে আশ্রয় দেয়া কানাডার পক্ষে অনৈতিক। তবে ভারত সরকার তাকে হত্যা করেনি। এই যখন অবস্থা তখন প্রকাশ পায় আরও মারাত্মক ঘটনা। খোদ মার্কিন প্রশাসন জানায়, যুক্তরাষ্ট্রে শিখ নেতা গুরপতওয়ান্ত সিং পান্নুকে হত্যাচেষ্টা করা হয়েছে। এই হত্যাচেষ্টাকারী একজন ভারতীয় সরকারের কর্মকর্তা। অন্যদিকে পান্নু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক। যার কারণে এই ঘটনায় বাইডেন প্রশাসন শক্ত অবস্থানে আছে। ধারণা করা হচ্ছে বাংলাদেশে আসন্ন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ভূরাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ভারতকে এই মুহূর্তে বেশি ঘাটাচ্ছে না বাইডেন প্রশাসন। কিন্তু নাখোশ যে হয়েছে সেটা স্পষ্ট। ভারতের আসন্ন জাতীয় দিবসে বাইডেনকে অতিথি করেছিলেন মোদি। আসার কথাও ছিলো। কিন্তু সম্প্রতি সেই আমন্ত্রণ বাতিল করেছেন জো বাইডেন। যদিও ভারত সরকার বলছে, বিদেশের মাটিতে কোনো নাগরিককে হত্যাচেষ্টা করা ভারত সরকারের নীতি পরিপন্থী। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা দপ্তর বলছে, হত্যাচেষ্টাকারী ব্যক্তি ঘটনার আগে পরে দীর্ঘ সময় ধরেই ভারত সরকারের বেতন ও সুবিধাভোগী। এতেই প্রমাণ হয়, সরকার এই ঘটনায় প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। মূলত এই শিখ নেতারা ভারতে পাঞ্জাব অঞ্চলে নিজেদের জন্য স্বাধীন খালিস্তান রাষ্ট্রের আন্দোলন করেন। বাইডেন প্রশাসনের সঙ্গে ভারত সরকার কূটনৈতিক সম্পর্ক ঠিক কতটা উষ্ণ রাখতে পেরেছে তা পুরোপুরি বলা না গেলেও ভারত যে, চাপে আছে সেটা স্পষ্ট হয়েছে কানাডায় এক ভারতীয় নাগরিক হত্যার শিকার হওয়ার পরপরই। আরও বেশি চাপে ফেলেছে দ্বিতীয় ঘটনায় যুক্তরাষ্ট্রে অপর নাগরিককে হত্যাচেষ্টার ঘটনার পর। কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্র উভয় ঘটনার জন্য সরাসরি ভারত সরকারকে দায়ী করছে। অস্ট্রেলিয়ার মতো মার্কিন মিত্র দেশগুলাও উভয় ঘটনা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে বলে পৃথকভাবে জানিয়েছে। এছাড়াও ভারতে মনিপুর দাঙ্গা, মিয়ানমারে চলমান গৃহযুদ্ধ, চীনের উইঘুর, আফ্রিকার নানাদেশের সংঘাত—সংঘর্ষ নানান হিসাব—নিকাষে বিদায়ী বছরকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের জন্য সংকটের বছর হিসাবে দাঁড় করিয়েছে। যদিও বছরের মাঝামাঝি কিছুটা আশা জাগিয়েছিলো চীনের মধ্যস্ততায় ইরান—সৌদি আরবের সম্পর্ক স্থাপন। এটা মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টার অংশ হিসেবে ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিস্ঠার একমাত্র পথ স্বাধীন ফিলিস্তিন প্রতিষ্ঠা, এর কোনো বিকল্প নেই। যেমনটা বলছিলেন তুর্কিয়ে প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়্যিপ এরদোগান। ইসরায়েল যতদিন স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের অঙ্গীকার মেনে না নিবে ততদিন মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি ফিরবে না। আর মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি না ফিরলে বৈশি^কভাবে তা সংকটের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। যেটা ইতোমধ্যে দৃশ্যমান হয়ে গেছে। আরব ও মুসলিম বিশ্ব যদি বাধা বিপত্তি কাটিয়ে উঠতে পারে তাহলে মধ্যপ্রাচ্যে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হওয়ার যথেষ্ঠ সম্ভবনা এখনো রয়েছে। আমরা আশাবাদী হতে চাই। পৃথিবীর পরাশক্তিধর দেশগুলো নেতাদের সুমতি হোক। বিশেষ কোথাও গিয়ে তাদের মানবতাবোধ ও নৈতিকতার যেন মৃত্যু না ঘটে। জেগে উঠুক বিশ্ব মানবতা। বাঁচুক গাজাবাসী। অধিকার ফিরে পাক ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী বৈধ ভূমি মালিকরা।
(ঢাকাটাইমস/৩১ডিসেম্বর)
 ঢাকা টাইমস অনলাইন এর সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিডটি ফলো করুন
ঢাকা টাইমস অনলাইন এর সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিডটি ফলো করুন
মন্তব্য করুন