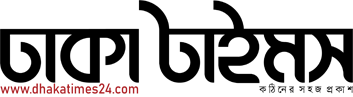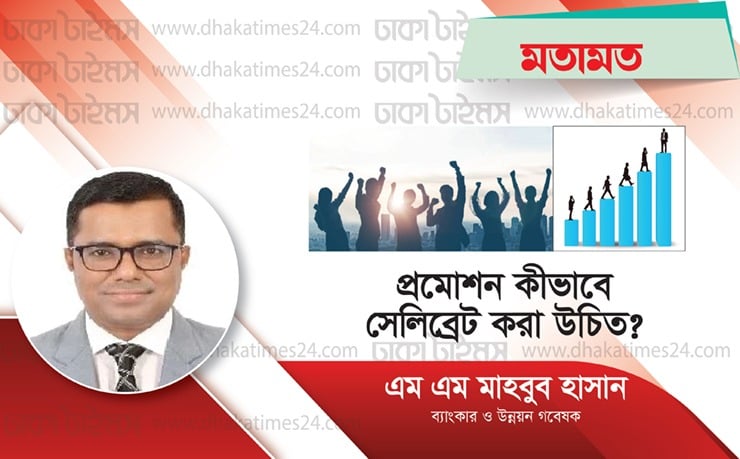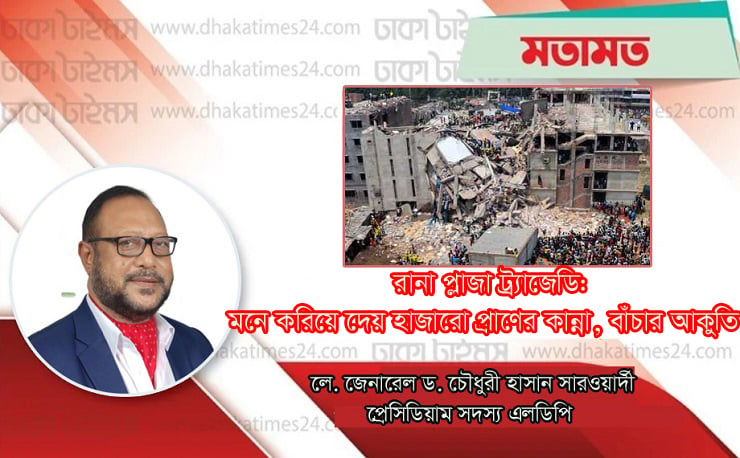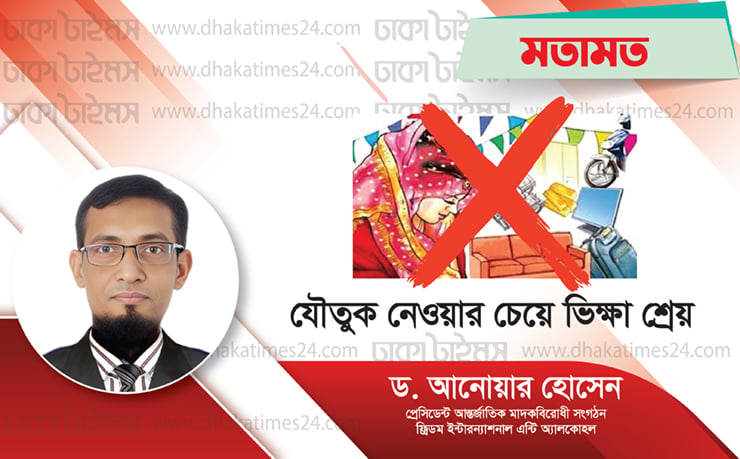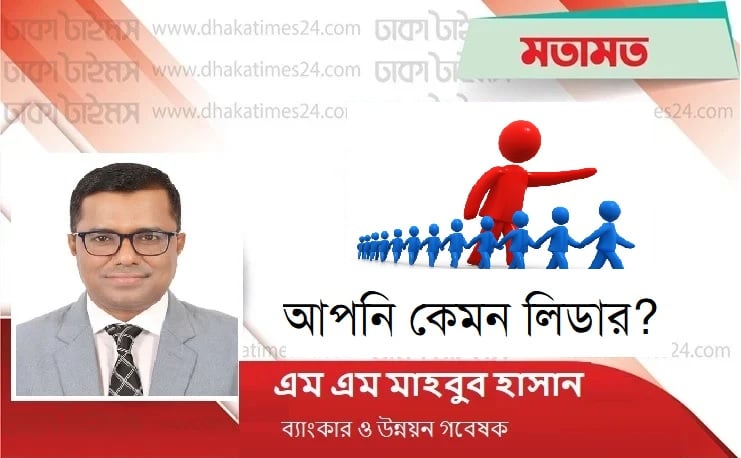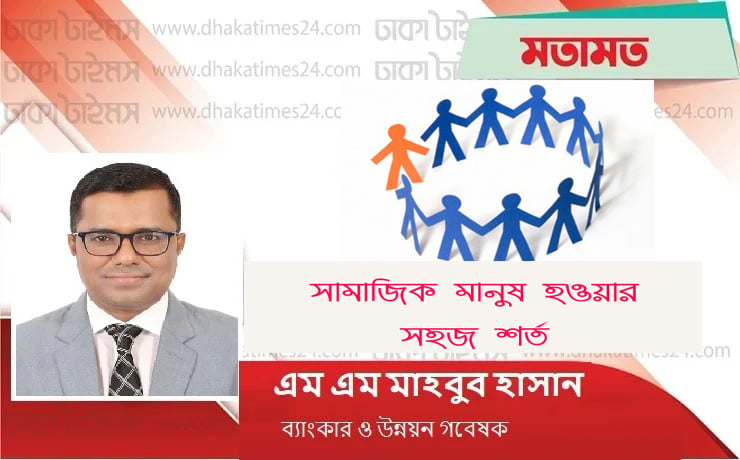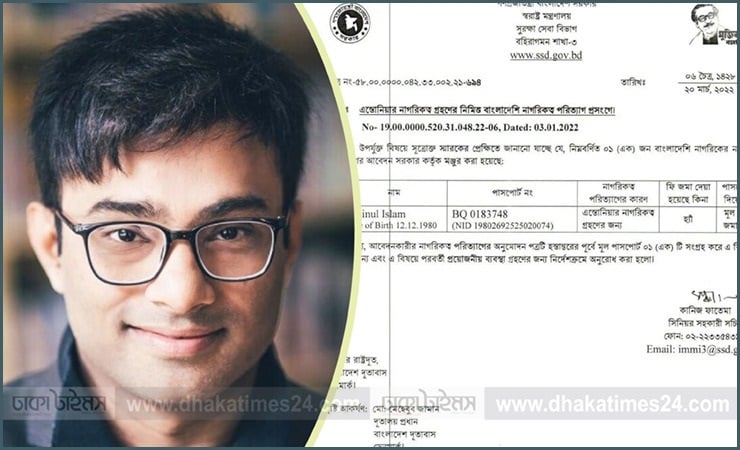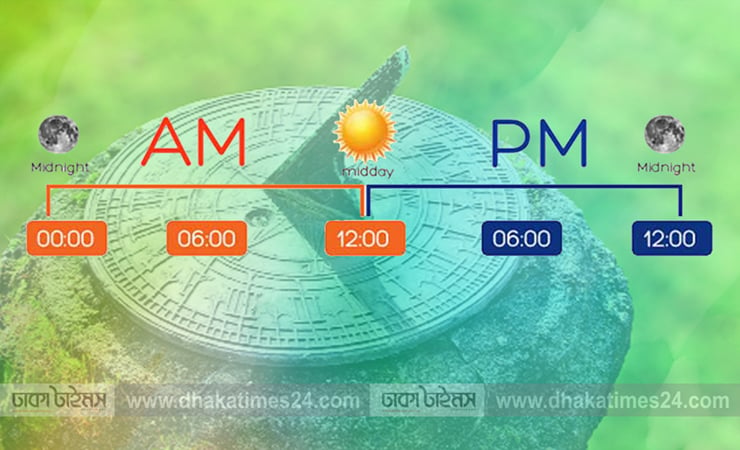স্বাস্থ্যখাত ঢেলে সাজাতে প্রয়োজন সঠিক পরিকল্পনার বাস্তবায়ন
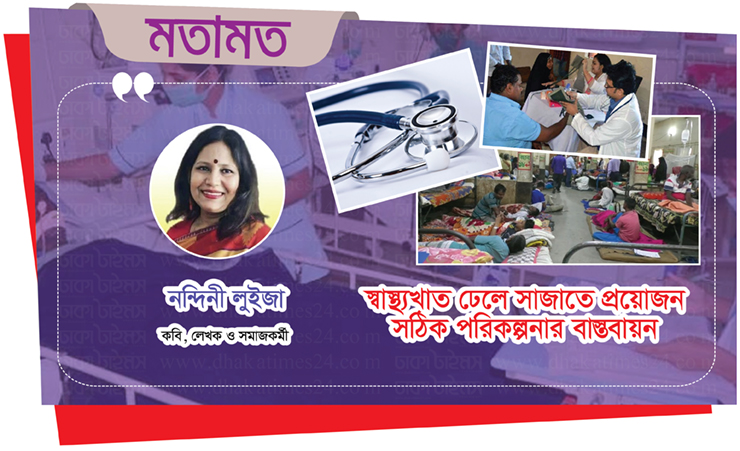
চিকিৎসা বিষয়ক শিক্ষা এবং তার প্রয়োগিক ব্যবহার একটি নৈতিকতাসম্পন্ন মানবিক কর্ম প্রক্রিয়া বলে মনে করি। চিকিৎসা শাস্ত্র নামের এই বিদ্যাটি অর্জন এবং তার চলমানতা সময়োগযোগী রাখার জন্য একজন চিকিৎসকের জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তার পড়াশোনার কাজটি চালিয়ে যেতে হয়। মানবকল্যাণে চিকিৎসাসেবা দিতে সর্বশেষ আবিষ্কৃত বিষয়ের সাথে একজন চিকিৎসককে সম্পৃক্ত থাকতেই হয়।
১৮৪৭ সালে আমেরিকান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন বিশ্বে প্রথম চিকিৎসকদের জন্য চিকিৎসা বিষয়ক নৈতিকতা কোড প্রণয়ন করে। সংস্থাটি বলছে চিকিৎসা পেশায় নৈতিকতার বেশকিছু নীতি রয়েছে। সেগুলো হলো- স্বায়ত্তশাসন, উপকারিতা, বিশ্বস্ততা, ন্যায়বিচার ও উপযোগিতা। স্বায়ত্তশাসন বলতে একজন ব্যক্তির আত্মসংকল্পের প্রতি শ্রদ্ধা ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে রোগীর পছন্দকে বোঝায়। উপকারিতা অর্থাৎ রোগীদের ভালো করা বোঝায়। ন্যায়বিচার নির্দেশ করে রোগীর চিকিৎসার বিষয়ে একজন চিকিৎসকের সিদ্ধান্ত ন্যায্য ও নিরপেক্ষভাবে হওয়া প্রয়োজন। আর উপযোগিতার ব্যাখ্যায় সংস্থাটি বলেছে সম্পদের অপচয় না করে একজন রোগীকে সর্বাধিক সুবিধা দেওয়া হবে এমন কার্যক্রম পরিচালিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।
আজকের এই লেখায় বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাত কতটুকু মানবকল্যাণমুখী হয়ে উঠেছে আর কী কী প্রতিবন্ধকতা রয়েছে সেই বিষয় নিয়ে একটু আলোকপাত করতে চাই। বর্তমানে মানসম্মত চিকিৎসক তৈরি হচ্ছে না বলে মন্তব্য করেন অনেকেই। তারা বলেন- যে কারিকুলামে তাদের পড়ানো হচ্ছে তাতে তাদের আরো বিস্তারিত নৈতিক শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। কেননা ডাক্তারি বিদ্যাটি এমন একটি শিক্ষা যেখানে প্রতিনিয়তই তাকে নতুন নতুন সমস্যায় পড়তে হয় এবং তার সমাধান দিতে হয় খুবই সতর্কতার সঙ্গে। মানবিকভাবে এবং ভালোবেসে ধৈর্য সহকারে চিকিৎসা করে যাওয়াটাই হচ্ছে এই পেশার মুখ্য উদ্দেশ্য। এক্ষেত্রে স্বাস্থ্য সুরক্ষা আইন বাস্তবায়ন করাও অত্যন্ত জরুরি একটি বিষয়। দুঃখজনক যে- চিকিৎসা শিক্ষার স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে নৈতিকজ্ঞানের অধ্যয়ন খুববেশি সন্তোষজনক নয় বলে বাংলাদেশ চিকিৎসা গবেষণা পরিষদের একটি গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে বলা হচ্ছে- তারা বেশিরভাগই চিকিৎসাবিষয়ক নৈতিকতা শিখেছে মূলত বই পড়ে। দ্বিতীয়ত, এরপর সর্বোচ্চ নৈতিকতা শিখেছে লেকচার শোনে। তবে ৯৭% চিকিৎসক মনে করেন চিকিৎসাশিক্ষার স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে চিকিৎসাবিষয়ক নৈতিকতার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে যুক্ত করা প্রয়োজন। ৭৫% চিকিৎসক কর্মক্ষেত্রে নৈতিকতার বিষয়ে গুরুত্ব দিলেও শতকরা ৩৫ শতাংশের এ বিষয়ে জানাশোনা খুবই কম আর ৪৬ শতাংশের ধারণা গড় অবস্থানে রয়েছে।
এদেশে ১৮ কোটি মানুষের জন্য সরকারি হাসপাতালগুলোতে ডাক্তার আছে ৩৪ হাজার। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়- দেশে ২৩ হাজার মানুষের জন্য রয়েছে মাত্র একজন ডাক্তার। সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে দেশে মোট ডাক্তারের সংখ্যা প্রায় ৯০ হাজার। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার গাইড লাইন অনুযায়ী একজন ডাক্তারের বিপরীতে তিনজন নার্স থাকার কথা থাকলেও তা নেই। এখানে রয়েছে যেমন ডাক্তারের ঘাটতি তেমনি রয়েছে নার্সের ঘাটতি। এই মুহূর্তে দেশে কমপক্ষে আরো দেড় লাখ ডাক্তার প্রয়োজন। সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে বর্তমানে শতাধিক মেডিকেল কলেজ থেকে প্রতিবছর প্রায় ১০ হাজার ছাত্রছাত্রী ডাক্তার হয়ে বের হচ্ছেন। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মতে যেকোনো দেশে প্রতি এক হাজার মানুষের জন্য কমপক্ষে একজন ডাক্তার থাকা প্রয়োজন।
বর্তমানে বেসরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় এক ধরনের জোড়াতালি হওয়ার কারণে সবার মাঝেই অসন্তোষ বিরাজ করছে। দুঃখজনক হলেও সত্য ঢাকা শহরে একজন নবীন শিক্ষানবিস বেসরকারি ডাক্তারের চেয়ে একজন সিএনজি চালকেরও মাসিক আয় তুলনামূলকভাবে বেশি। আমি জানি না এই দুঃসহ বাস্তবতা আমাদের নীতি নির্ধারক কিংবা পেশাজীবী নেতাদের আদৌ ব্যথিত করে কি না। দালাল পরিবেষ্টিত ক্লিনিক ব্যবসায় মুনাফার লোভে মালিকেরাও যে যার মতো পারছে নবীন ডাক্তারদের পারিশ্রমিক প্রদানের বেলায় ঠকাচ্ছে। এসব অনিয়ম-অব্যবস্থা দেখার কেউ নেই।
যদিও দেশে চিকিৎসা ব্যবস্থার আকার দিনদিন বাড়ছে কিন্তু তাতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে প্রশাসনিক অপব্যবস্থপনা। বর্তমানে চিকিৎসা সেবাপ্রাপ্তিতে যেমন রোগীর নিজস্ব ব্যয় বেড়েছে তেমনি বেড়েছে অসন্তুষ্টি। মূলত রোগীকে পর্যাপ্ত সময় না দেওয়া, সঠিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করা, অপ্রয়োজনীয় পরীক্ষা ও ওষুধের পরামর্শ দেওয়া, কমিশন নেওয়া, রোগীর রোগের বিবরণে মনোযোগ না দেওয়াসহ রোগীর প্রতি বিভিন্ন বৈষম্যমূলক আচরণই এই অসন্তুষ্টির কারণ। বিশেষজ্ঞদের মতে চিকিৎসা বিষয়ক অবহেলার প্রতিকার না হওয়াই এই খাতকে দিন দিন ক্ষতিগ্রস্ত করছে।
আমরা জানি, চিকিৎসা ক্ষেত্রে উন্নত বিশ্বে রেফারেন্স সিস্টেম চালু আছে। এটা আমাদের বাংলাদেশেও চালু করতে হবে। রেফারেন্স সিস্টেমে ডাক্তারদের সাধারণত জেনারেল প্র্যাকটিশনার বা ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান বলা হয়। এরা প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর যদি মনে করেন রোগীর উন্নতমানের চিকিৎসা লাগবে তাহলে তারা রোগীকে প্রয়োজনীয় বিষয়ের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে রেফার করেন। আমাদের দেশের মতো সামান্য সর্দি, কাশি, জ্বর, ঠান্ডা হলে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের কাছে সরাসরি যাওয়ার সুযোগ সেখানে নেই। ফলে জেনারেল প্র্যাক্টিশনার যেমন সাধারণ রোগীদের দেখার সুযোগ পাচ্ছেন তেমনি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরাও অপ্রয়োজনীয় রোগী দেখে সময় নষ্ট না করে জটিল রোগীদের অধিক মনোযোগ সহকারে দেখার সুযোগ পাচ্ছেন। এর ফলে ডাক্তারদের ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ার গড়ার ব্যাপ্তিও বাড়ে। আমাদের দেশেও এ ধরনের সংস্কৃতি চালু করা দরকার। তাহলে এখন যেমন ডাক্তারদের মধ্যে এফআরসিএস, এমডি, এফসিপিএস, এমএস-সহ বিভিন্ন ধরনের স্নাতকোত্তর ডিগ্রি করার এক ধরনের অসুস্থ উন্মাদনার প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়েছে সেটি তখন অনেকাংশেই হ্রাস পাবে। গুরুত্ব পাবে এমবিবিএস ডিগ্রিরও। বর্তমানের মতো তখন আর এমবিবিএস ডিগ্রিকে গুরুত্বহীন মনে করার অবকাশ কমে যাবে। এমবিবিএস পাশ করার পর সবাইকেই স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিতে হবে এমন কোনো কথা নেই।
দেশের রেফারেন্স পদ্ধতি চালু করতে হলে নীতি নির্ধারক পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পাশাপাশি এমবিবিএস ডিগ্রির মান নিশ্চিত করতে হবে। বর্তমানে দেশের সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে যে শতাধিক মেডিকেল কলেজ রয়েছে সবগুলোর শিক্ষার মান সমান কিংবা কাছাকাছি নয়। এগুলোর শিক্ষার মান নিশ্চিত করা এক বড়ো চ্যালেঞ্জ। এমবিবিএস ডিগ্রিধারী ডাক্তারকে কেন্দ্র করে যেহেতু রেফারেন্স সিস্টেমের চিকিৎসাসেবা প্রদান আবর্তিত হয় সেহেতু এমবিবিএস পাস করা ডাক্তারকে দক্ষ হিসেবেই গড়ে তুলতে হবে। ডাক্তারের চিকিৎসা সংক্রান্ত সব কর্মকাণ্ডকেই নিয়মিত তদারকির মধ্যে রাখতে হবে। যাতে ডাক্তারের পক্ষে কোনো রকমের ম্যালপ্র্যাকটিস করার অবকাশ না থাকে।
নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে যদি রেফারেন্স সিস্টেমের পক্ষে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, তাহলে তা বাস্তবায়নে পৃথিবীর বহু দেশ থেকেই সহায়তা পাওয়া যাবে। নতুন করে খুব বেশি কিছু তৈরি করতে হবে না। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার সংকট থাকলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় স্বাস্থ্যসেবা প্রত্যাশী জনগণ। যদিও বাংলাদেশের নীতি অনুযায়ী স্বাস্থ্যখাত মানে শুধু ডাক্তার। জনগণের আচরণ দেখে মনে হয় ডাক্তারের কাছে কোনোমতে হাজির হতে পারলেই হলো; ডাক্তার যেন যেকোনো রোগীকেই চিকিৎসাসেবা দিয়ে সুস্থ করতে পারবেন। এমনকি মুমূর্ষু রোগী অবস্থায় হাসপাতালে আনার পর চিকিৎসা প্রদান সত্ত্বেও যদি রোগীর মৃত্যু হয় তাও যেন ডাক্তারের দোষ।
তবে এটা সত্য যে- গ্রামে-মফস্বলের হাতুড়ে ডাক্তার এবং নানা রকমের ভুয়া ডিগ্রিধারী ডাক্তাররা রোগীর জীবন বিপন্ন করে তোলে। এদের ভুল চিকিৎসার খপ্পরে পড়ে অসংখ্য রোগী মারা যায়। অনেক ক্ষেত্রে রোগী যখন ডাক্তারের কাছে আসে তখন অনেক দেরি হয়ে যায়। ডাক্তারের তখন চিকিৎসা করার তেমন কোনো সুযোগ থাকে না। পাশাপাশি প্রয়োজনীয় বাজেট এবং অনুকূল পরিবেশ না থাকলে ডাক্তারদের পক্ষেও সর্বোচ্চ চিকিৎসা প্রদান অনেকটা কষ্টসাধ্য। এই বোধটা এখনো সাধারণ জনগণের ভেতরে সেভাবে গড়ে ওঠেনি। বরং স্বাস্থ্যখাতের যেকোনো সীমাবদ্ধতার জন্য অভিযোগের আঙুল ডাক্তারের দিকেই উত্তোলন করা হয়। পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ ও এর সঠিকভাবে ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং চিকিৎসা ও ওষুধ সরবরাহ, জনবল নিয়োগসহ অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা না গেলে চিকিৎসাখাত উন্নত হবে না। এ খাতে সরকারের সঠিক হস্তক্ষেপ প্রদানে ব্যর্থ হলে শুধু সংশ্লিষ্ট বিভাগ এবং কর্তৃপক্ষকে ঢালাওভাবে দায়ী করলে হবে না। এ সত্য মেনে না নেওয়ার কিছু নেই। আরও কিছু বিষয় স্বাস্থ্যখাতের সাথে সংযুক্ত রয়েছে। রোগীদের অশিক্ষা ও সচেতনতার অভাবও ঘুরে ফিরে আসে। ডাক্তারের নির্দেশনা না মেনে চলা এবং চিকিৎসা প্রক্রিয়ায় ভুল বোঝাবুঝির কারণেও চিকিৎসা কার্যক্রম ব্যাহত হয় অনেক সময়। সঠিক শিক্ষা ও নৈতিক মানসিকতার অভাবের ফলে অনেক সময় চিকিৎসকরা আন্তর্জাতিক মানের সেবা প্রদান করতে ব্যর্থ হচ্ছে। চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতি এবং ডাক্তারদের পেশাগত মানসিকতা পরিবর্তনের মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব। সরকারের পাশাপাশি সামাজিক সংগঠন ও সাধারণ মানুষকেও এ বিষয়ে সচেতন হতে হবে।
আমার ধারণা ২০৪১ সালে এদেশের প্রতি ১০০০ জন মানুষের জন্য নূন্যতম একজন ডাক্তার থাকবে। তবে শুধু পর্যাপ্ত সংখ্যক ডাক্তার থাকলেই হবে না সেই সঙ্গে আনুপাতিক হারে নার্স, অন্য দক্ষ স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদেরকেও সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে নিয়োগ দিতে হবে। আমাদের দেশে বর্তমানে ডাক্তারের চেয়ে নার্সের সংখ্যা কম অথচ এর উল্টো হওয়ার দরকার ছিল। চিকিৎসকদের মতো নার্সদের কর্মও একটা গুরুত্বপূর্ণ সম্মানজনক পেশা, সেটাকেও আমাদের অনুধাবন করতে হবে।
বাংলাদেশের ডাক্তারদের আন্তরিকতা আমরা দেখতে পেয়েছি, করোনা মহামারীতে। করোনা মহামারীর সংকটময় অবস্থায় ডাক্তারদের ইতিবাচক ভূমিকা জাতীয় জীবনের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে স্থিতিশীল রাখতে এবং রোগীদের সর্বোচ্চ সেবা প্রদানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তাদের নিরলস পরিশ্রম, ঝুঁকি নিয়ে সামনের সারিতে থেকে সম্মুখযোদ্ধা হিসেবে এবং সমাজের ভারসাম্য বজায় রাখতে তারা তখন বিশেষ অবদান রেখেছেন। করোনা ভাইরাস মহামারীর সময় তারা অতিরিক্ত সময় কাজ করেছেন এবং অনেক সময় নিজেদের পরিবারের থেকে দূরে থেকেছেন জনস্বাস্থ্য রক্ষায়।নন্দিনী লুইজা: কবি, লেখক ও সমাজকর্মী
 ঢাকা টাইমস অনলাইন এর সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিডটি ফলো করুন
ঢাকা টাইমস অনলাইন এর সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিডটি ফলো করুন
মন্তব্য করুন