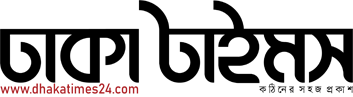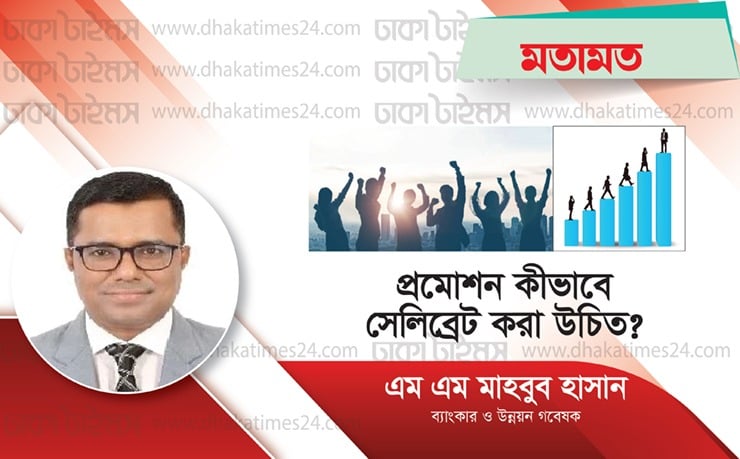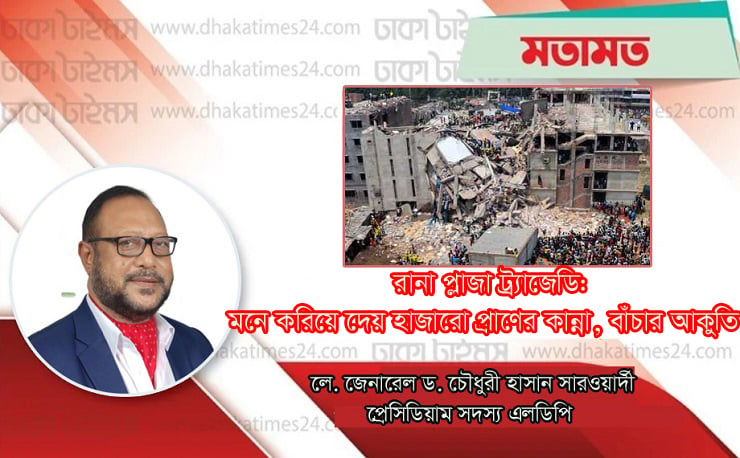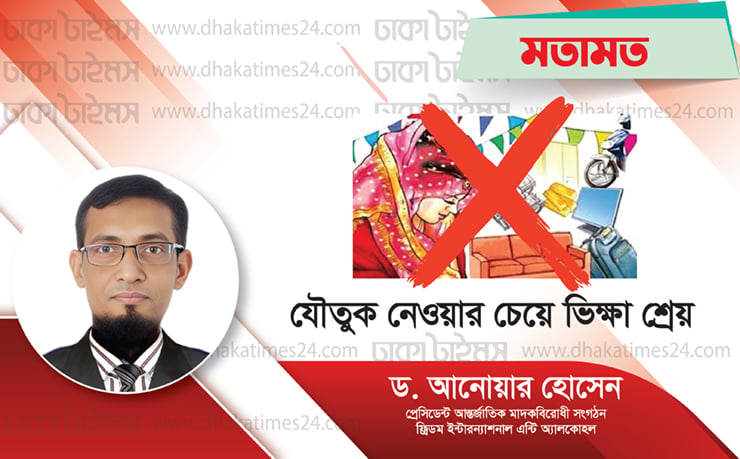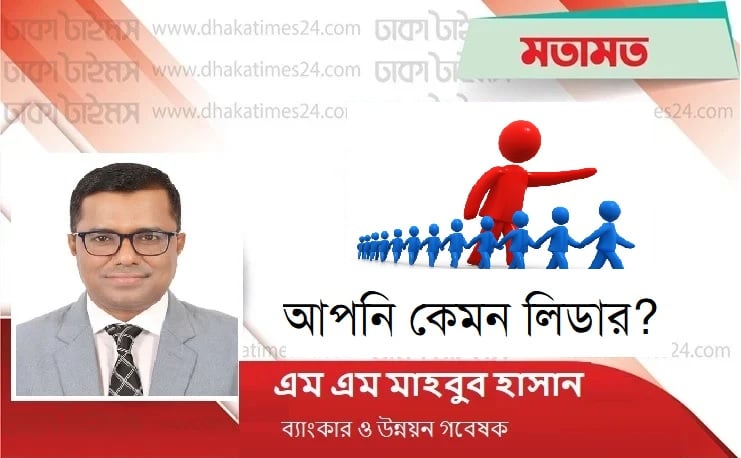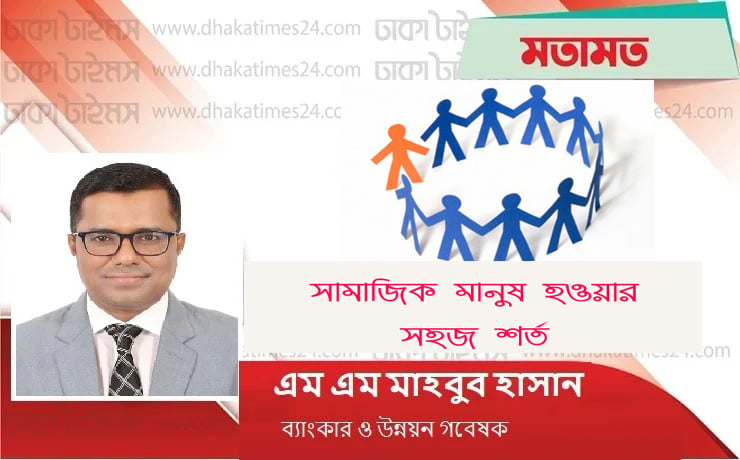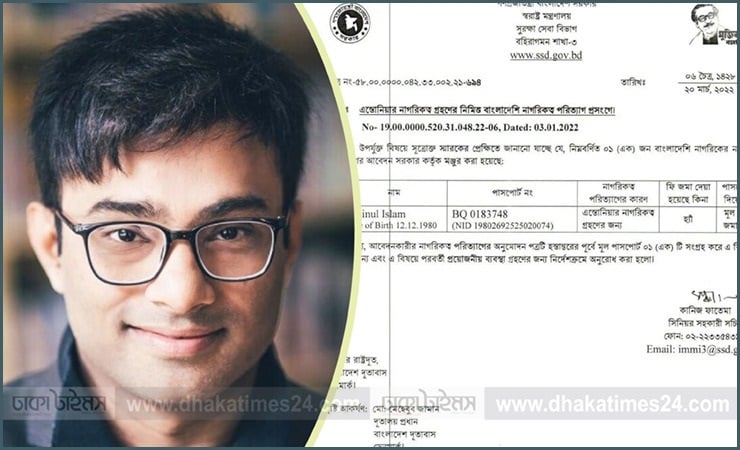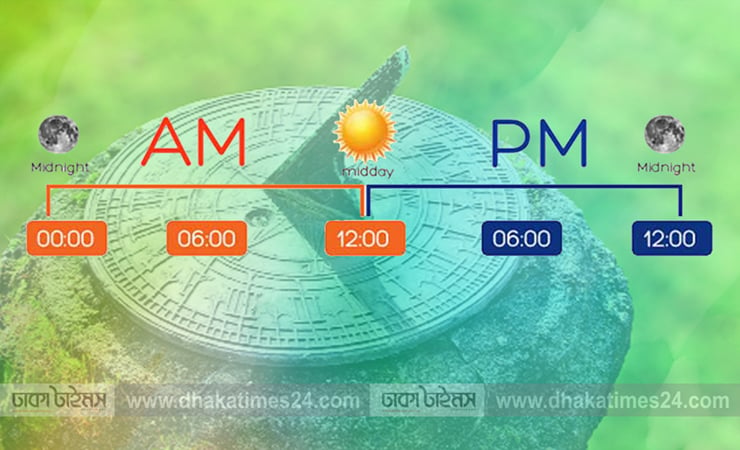শিক্ষা-সংস্কার কমিশন কেন জরুরি
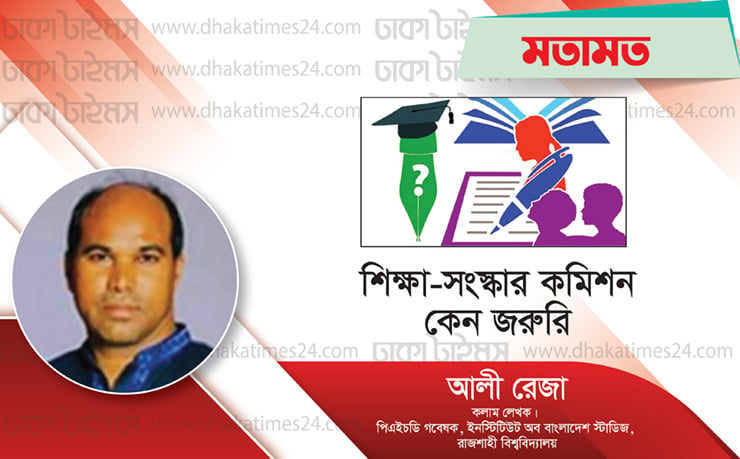
বিচার বিভাগ, দুর্নীতি দমন কমিশন, জনপ্রশাসন, সংবিধান ও পুলিশ বাহিনী- এই ছয়টি ক্ষেত্রে সংস্কারের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ছয়টি কমিশন গঠন করেছে। প্রধান উপদেষ্টার বক্তব্য অনুযায়ী এ কমিশনগুলো অক্টোবর মাসে কাজ শুরু করে তিন মাসের মধ্যে প্রতিবেদন জমা দেবে। কমিশনের রিপোর্ট পেশ হলে রাজনৈতিক দলগগুলোর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে পরবর্তী করণীয় নির্ধারণ করা হবে- এমন আভাসও পাওয়া গেছে প্রধান উপদেষ্টার বক্তব্যে। এ ছয়টি কমিশন গঠন করার মাধ্যমে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কাজের একটি রোডম্যাপ তৈরি হয়েছে বলা যায়। তবে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সংস্কার প্রয়োজন। সেসব ক্ষেত্রেও কমিশন গঠন করার দাবি উঠেছে।
ইতোমধ্যে গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন গঠনের কথা বলেছেন তথ্য উপদেষ্টা। খুব শীঘ্রই এ কমিশন গঠন হবে বলে জানা গেছে। বিগত সরকারের সময়ে শিক্ষাক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তন আনা হয়েছিল। বিশেষ করে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকে ব্যাপকভাবে পরিবর্তন আনা হয়েছিল। চাপিয়ে দেওয়া সেসব পরিবর্তনকে গ্রহণযোগ্য মনে করেননি বেশিরভাগ মানুষ। শিক্ষা উপদেষ্টা দায়িত্ব নেওয়ার পর সেই শিক্ষাক্রমের উপযুক্ততা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন এবং প্রয়োজনীয় সংশোধনের পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে মত প্রকাশ করেছিলেন। পাঠক্রম ও পরীক্ষা পদ্ধতির বারবার পরিবর্তনের ফলে শিক্ষক, অভিভাবক এমনকি শিক্ষার্থীরাও ছিলেন দিশেহারা। অনেক অভিভাবক মূল্যায়ন পদ্ধতির বিরোধিতা করে আন্দোলনে নেমেছিলেন। সে বিবেচনা থেকেও শিক্ষা সংস্কারের বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে বলা যায়। ফলে শিক্ষা সংস্কার কমিশন গঠনের মাধ্যমে পাঠক্রম, মূল্যায়ন পদ্ধতি ও শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যমান নানা বৈষম্য দূর করার দাবি উঠেছে।
শিক্ষা রাষ্ট্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খাত। তাই রাষ্ট্র সংস্কার করতে হলে শিক্ষা সংস্কারকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। শিক্ষায় বিনিয়োগের মাধ্যমেই একটি দেশ দক্ষ জনশক্তি বা মানবসম্পদের উন্নয়ন ঘটায়। বাংলাদেশের বিপুল পরিমাণ জনগোষ্ঠীকে মানবসম্পদে পরিণত করার জন্য প্রয়োজন একটি সময়োপযোগী শিক্ষাক্রম ও দক্ষ শিক্ষকমণ্ডলি। পাঠক্রমের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকগণকেও দক্ষ ও যোগ্য করে গড়ে তোলা প্রয়োজন। এর জন্য শিক্ষা সংস্কার কশিমন গঠন করে এ দুটি বিষয়ে অতিদ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে। বিগত সরকারের শেষ সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ ‘প্রত্যয়’ নামক পেনশন স্কিমের বিরোধিতা করে আন্দোলনে নেমেছিলেন। সে আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিল আরো কিছু দাবি যেগুলো তাঁদের পেশাগত মর্যাদার সঙ্গে যুক্ত। কলেজ পর্যায়ের সরকারি শিক্ষকদের পদোন্নতিসহ আন্তঃক্যাডার বৈষম্য নিরসনের দাবি ছিল। সে দাবিতে তাঁরা নানা কর্মসূচি পালন করেছে। এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের জাতীয়করণের দাবিই প্রধান। তবে তাঁরা দীর্ঘদিন যাবৎ বেতনবৈষম্য নিরসনের দাবি করে আসছেন। বাড়িভাড়া ও চিকিৎসাভাতা বৃদ্ধি ও ঈদ বোনাস শতভাগ করার দাবি তাঁদের দীর্ঘদিনের। সরকারি প্রাথমিক শিক্ষকগণের গ্রেড উন্নয়নের দাবি আছে। মোটা দাগে এসব দাবি ছাড়াও বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কারের দাবিতে আন্দোলন ও আলাপ-আলোচনা হতে দেখা যায় মাঝে-মধ্যেই। সরকারের পক্ষ থেকে এসব দাবির যৌক্তিকতা অস্বীকার করা না হলেও পূরণ হয়েছে সামান্যই। শিক্ষাক্ষেত্রে নানা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও প্রতিশ্রুতি অনুয়ায়ী কাজ হয়নি। বর্তমান সরকার বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের ফসল। ফলে এ সরকারকে বৈষম্য নিরসনের জন্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালাতে হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যমান বৈষম্য চিহ্নিত করে সেগুলো নিরসন কিংবা সংস্কার করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
শিক্ষা সংস্কারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো শিক্ষক নিয়োগ পদ্ধতির সংস্কার। এক্ষেত্রে পৃথক শিক্ষক নিয়োগ কমিশনের কথাও ভাবা হয়েছে বিভিন্ন সময়ে। বিশ^বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগে যে সংক্ষিপ্ত প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয় তাতে যোগ্য, দক্ষ ও নৈতিক জ্ঞানসম্পন্ন শিক্ষক নির্বাচন করা কঠিন। বিদ্যমান এ নিয়োগ প্রক্রিয়ার বদলে কেন্দ্রীয়ভাবে শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া চালু করা যেতে পারে। বাংলাদেশে প্রায় ৯৮% শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত ও বেসরকারি। এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষক-কর্মচারীদের চাকরিকে বেসরকারি বলার কোনো যৌক্তিকতা নেই। কারণ তাঁরা সরকার অনুমোদিত কমিটির মাধ্যমে নিয়োগ পেয়েছেন এবং বর্তমানে সরকারি ব্যবস্থাপনায় এনটিআরসিএর মাধ্যমে সরাসরি নিয়োগ পাচ্ছেন। শুধু তাই নয়, এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীগণ জাতীয় বেতনস্কেল-এর অন্তর্ভুক্ত এবং শতভাগ বেতন, ইনক্রিমেন্ট ও বাড়িভাড়া-চিকিৎসা ভাতার একটি অংশ সরকারি কোষাগার থেকেই পান। এসব বিবেচনায় এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীগণকে বেসরকারি বলার যৌক্তিকতা নেই। কলেজ শিক্ষকগণের পদবিন্যাসে প্রভাষক, সহকারী অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক ও অধ্যাপক- এই চারটি পদসোপান থাকলেও এমপিওভুক্ত প্রভাষকগণ শুধু সহকারী অধ্যাপক পর্যন্ত হতে পারেন। একই যোগ্যতায় নিয়োগ পেয়ে অধিকতর যোগ্যতা-দক্ষতা, উচ্চতর গবেষণা ও চাকরিকাল বিবেচনায় কেন তাঁরা সহযোগী অধ্যাপক ও অধ্যাপক হতে পারবেন না- এর কোনো যৌক্তিক ব্যাখ্যা নেই। ফলে এই বৈষম্য নিরসন হওয়া জরুরি। এমপিওভুক্ত শিক্ষকগণ বদলির দাবি করে আসছেন দীর্ঘদিন ধরে। এ দাবির যৌক্তিকতা অস্বীকার করা যায় না। একই প্রতিষ্ঠানে চাকরির বাধ্যবাধকতা থাকলে সবক্ষেত্রেই একটি গোষ্ঠী আর একটি গোষ্ঠীর দ্বারা অন্যায়ভাবে নিগৃহীত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। সেখানে লোকাল-এন্টিলোকাল সমস্যার সৃষ্টি হয়। একটি গোষ্ঠীর আধিপত্যবাদী মনোভাবের কারণে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নষ্ট হয়। ফলে বদলি পদ্ধতি চালু করা যেতে পারে এবং এতে কোনো আর্থিক সংশ্লেষ নেই।শিক্ষা সংস্কারের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হলো এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান নিয়োগ। বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ আইন-২০০৫ অনুসারে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক হতে হলে কেন্দ্রীয়ভাবে পরিচালিত পরীক্ষার মাধ্যমে যোগ্যতা অর্জনের সনদ লাভ করতে হবে। ২০০৫ সালের পর এ সনদ লাভ করেই সবাই শিক্ষক হয়েছেন। বর্তমানে এনটিআরসিএ পিএসসির আদলে এমসিকিউ, রচনামূলক ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে যোগ্য প্রার্থী নির্বাচন করে সরাসরি নিয়োগের সুপারিশ করার ক্ষমতা পেয়েছে এবং সে ক্ষমতাবলে ইতোমধ্যেই প্রায় লক্ষাধিক শিক্ষক নিয়োগ পেয়েছেন। কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান নিয়োগের ক্ষেত্রে সেই পুরোনো বিতর্কিত পদ্ধতিই বহাল আছে। ফলে রাজনৈতিক বিবেচনা, অর্থ লেনদেন ও স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে তুলনামূলকভাবে অযোগ্য প্রার্থীরাও প্রতিষ্ঠানপ্রধান হিসেবে নিয়োগলাভের সুযোগ পাচ্ছে। কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রেও পূর্বের নিয়ম বহাল থাকায় ঘুষ-দুর্নীতি বন্ধ হয়নি। প্রতিষ্ঠান প্রধান ও কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়োগ পদ্ধতির সংস্কার করা খুবই জরুরি। তা না হলে যোগ্য শিক্ষকগণকে অযোগ্য অধ্যক্ষ ও প্রধান শিক্ষকের অধীনে চাকরি করতে হবে। এ মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা থাকলে ফলপ্রসু শিক্ষাদান প্রক্রিয়া বিঘ্নিত হবে। সুতরাং শিক্ষা সংস্কারের এই বড়ো জায়গাটির প্রতি যত তাড়াতাড়ি মনোযোগ দেওয়া যাবে ততই এর সুফল পাবে সাধারণ মানুষ। এক্ষেত্রে সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ন্যায় শিক্ষকগণের মধ্য থেকে পদায়নের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান প্রধান নিয়োগ করা যেতে পারে। এটা করা হলে সরকারকে আলাদাভাবে প্রতিষ্ঠান প্রধান নিয়োগের প্রক্রিয়ায় যেতে হবে না।
নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সংস্কারের পাশাপাশি নিয়োজিত শিক্ষকদের দক্ষতা, যোগ্যতা, উচ্চতর ডিগ্রি ও চাকরিকাল বিবেচনায় নিয়ে একটি ন্যায়সংগত পদোন্নতি নীতিমালা প্রণয়ন করা দরকার। বিদ্যমান পদোন্নতি নীতিমালায় দক্ষতা, যোগ্যতা ও উচ্চতর ডিগ্রি বিবেচনা করা হয় না। শুধু চাকরিকাল বিবেচনায় নিয়ে আনুপাতিক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। ফলে শিক্ষকগণ দক্ষতা, যোগ্যতা ও উচ্চতর গবেষণার মাধ্যমে নিজেকে পেশাগতভাবে যোগ্য করে গড়ে তোলার কোনো চিন্তাই করেন না। বিভাগীয় পরীক্ষার মাধ্যমে পদোন্নতির পদ্ধতি চালু করলে শিক্ষকগণ নিজেরাই পেশাগতভাবে যোগ্য হয়ে ওঠার চেষ্টা করবেন। বাংলাদেশে শিক্ষকদের বেতনকাঠামোও সন্তোষজনক নয়। বাংলাদেশে শিক্ষার সকল স্তরেই শিক্ষকদের বেতন বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় কম। বিশ^মানের শিক্ষা নিশ্চিত করতে হলে যোগ্য শিক্ষক নিয়োগের পাশাপাশি শিক্ষকদের বেতন বাড়াতে হবে। বেতন বাড়ালেই কেবল মেধাবীরা শিক্ষকতা পেশায় আগ্রহী হবে। দেশের বর্তমান বাস্তবতায় শিক্ষকতাকে কেউ প্রথম পছন্দ হিসেবে গ্রহণ করে না। এর নানাবিধ কারণ আছে। শিক্ষকরা একদিকে বেতন ও পদোন্নতিতে পিছিয়ে আছে অন্যদিকে তাঁদের প্রশাসনিক ক্ষমতা বলে কিছু নেই। মুখে যতই সম্মানজনক পেশা বলা হোক না কেন- বাস্তবে শিক্ষকতা কোনো আকর্ষণীয় পেশায় পরিণত হতে পারেনি। এ বাস্তবতার নিরিখে শিক্ষা সংস্কার কমিশন গঠনের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।
শিক্ষার কোন স্তরে কী ধরনের বৈষম্য আছে এবং সে বৈষম্য নিরসন করার যৌক্তিকতা খতিয়ে দেখতে হবে। বিভিন্ন সময়ে গঠিত শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ পর্যালোচনা করলে সেখান থেকেও করণীয় নির্ধারণের ব্যাপারে একটি দিক-নির্দেশনা লাভ করা সম্ভব। দুঃখজনক বিষয় হলো বাংলাদেশে এ যাবৎ যতগুলো শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছে তার কোনোটারই সুপারিশ পুরোপুরি বাস্তবায়ন করা হয়নি। বিভিন্ন সময়ে ক্ষমতাসীন সরকার সাধারণ মানুষকে দেখানোর জন্য শিক্ষা কমিশন গঠন করেছে বটে, কিন্তু কাজের বেলায় সে কমিশনের সুপারিশ আমলে নেয়নি। নিজেদের খেয়াল-খুশি অনুযায়ী শিক্ষাব্যবস্থায় পরিবর্তন এনেছে।
মাননীয় শিক্ষা উপদেষ্টা দায়িত্ব নিয়েই পাঠক্রম ও পরীক্ষা পদ্ধতির ইতিবাচক পরিবর্তনের কথা বলেছেন। উপদেষ্টা মহোদয়ের এ বক্তব্যে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বেশিরভাগ মানুষ সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তবে শুধু পাঠক্রম ও পরীক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তন নয়, একই সঙ্গে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া ও পদোন্নতি নীতিমালার সংস্কার প্রয়োজন। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্থাবর-অস্থাবর আয় রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা করা হলে বেসরকারি শিক্ষা জাতীয়করণ করার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত অর্থ লাগবে না বলে বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে। এর সত্যতা যাচাই করে শিক্ষা জাতীয়করণের পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে। শিক্ষা ব্যক্তির মৌলিক মানবিক অধিকার। এ অধিকার নিশ্চিত করা রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত সরকারের। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কারের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সে অনুযায়ী এ সরকার একটি শিক্ষা সংস্কার কমিশন গঠন করে শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যমান বৈষম্য দূর করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে- এমন প্রত্যাশা করছেন সাধারণ মানুষ।আলী রেজা: কলাম লেখক, কলেজ শিক্ষক ও গবেষক, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
 ঢাকা টাইমস অনলাইন এর সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিডটি ফলো করুন
ঢাকা টাইমস অনলাইন এর সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিডটি ফলো করুন
মন্তব্য করুন