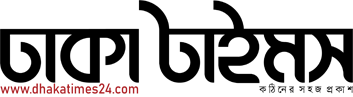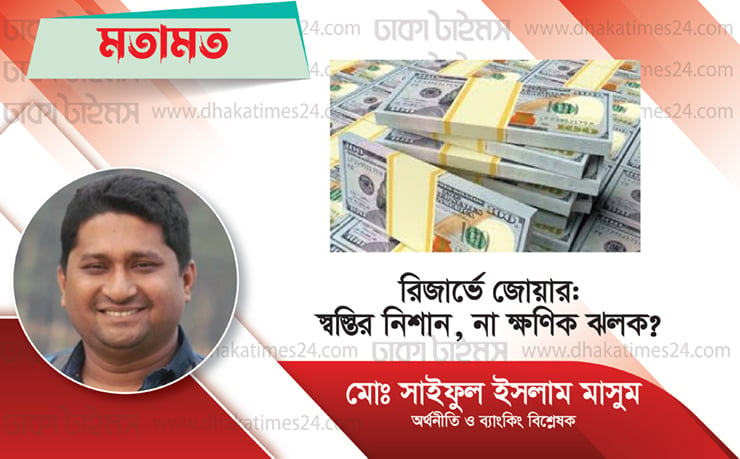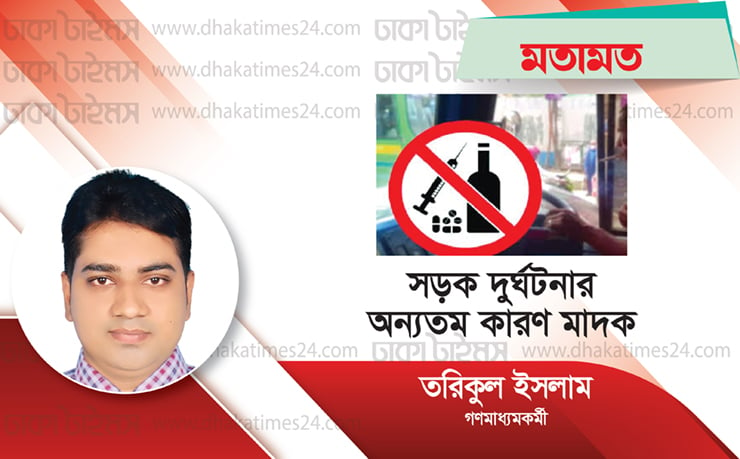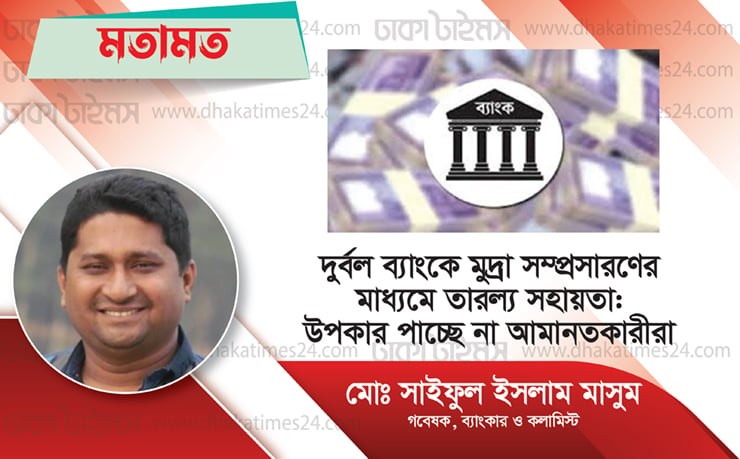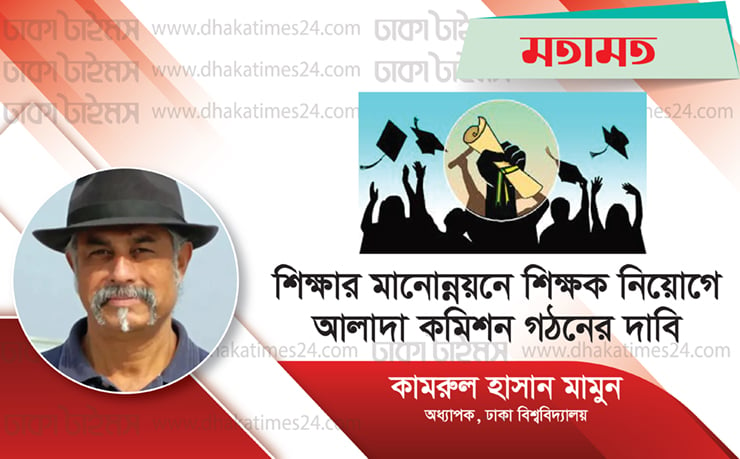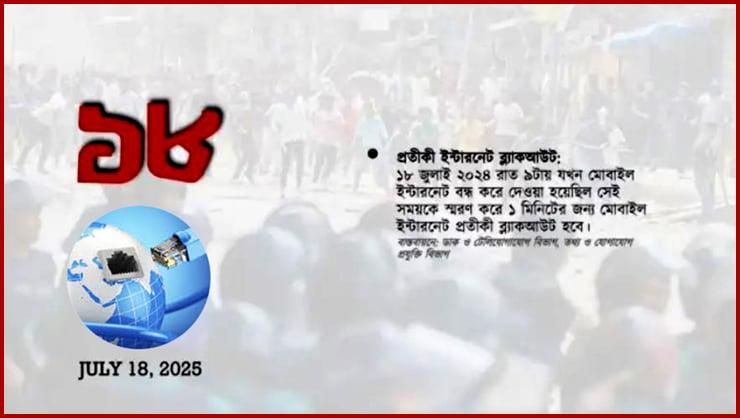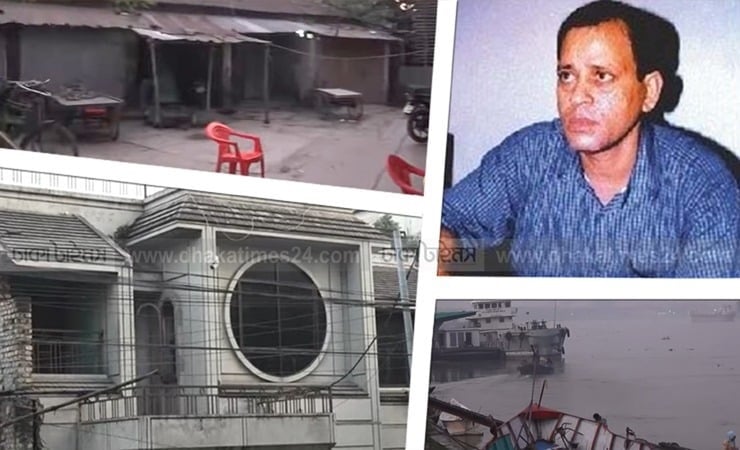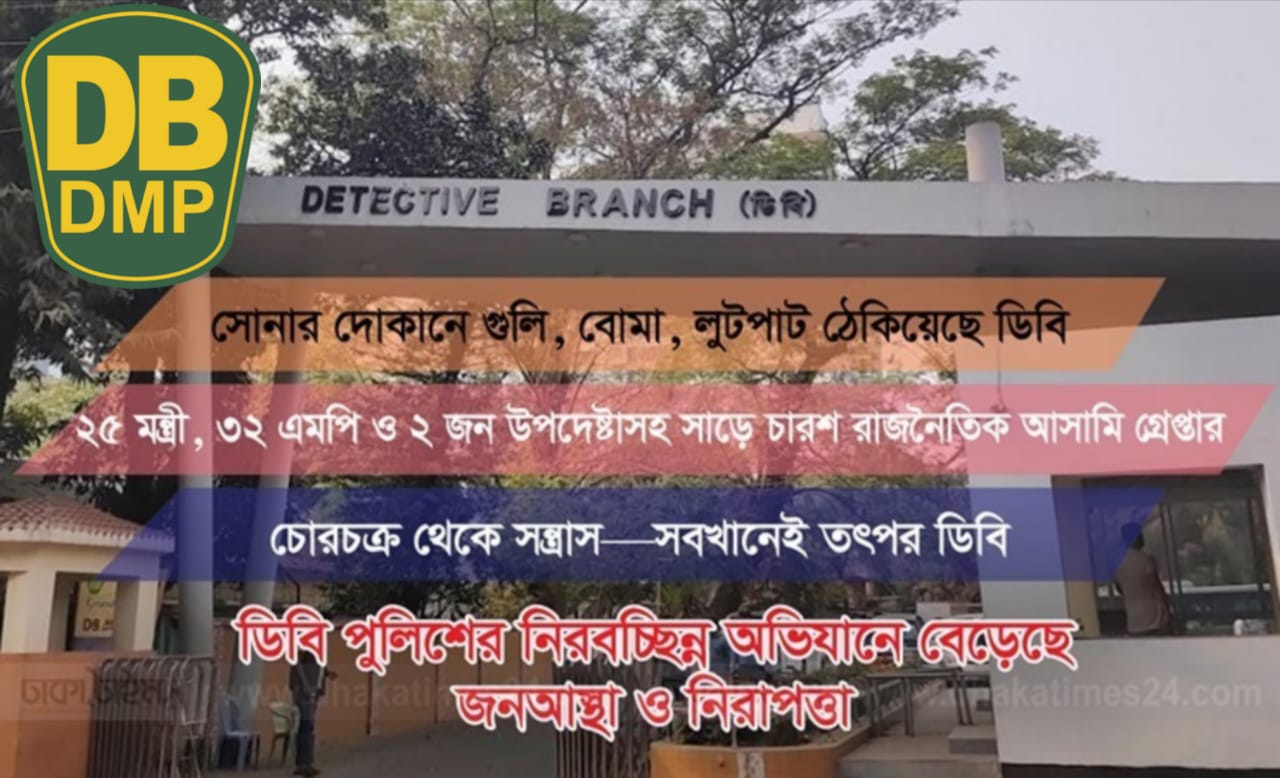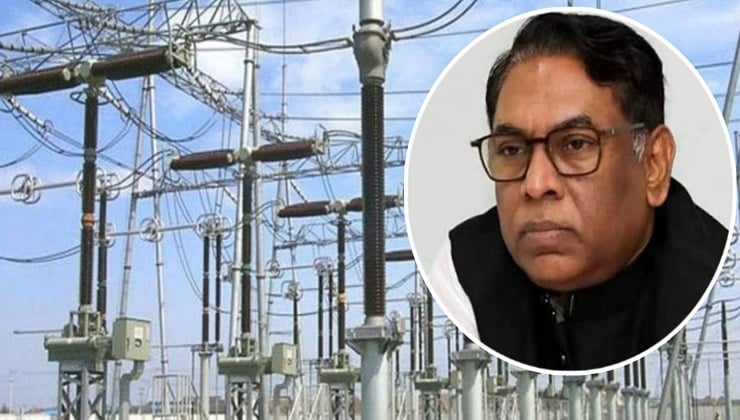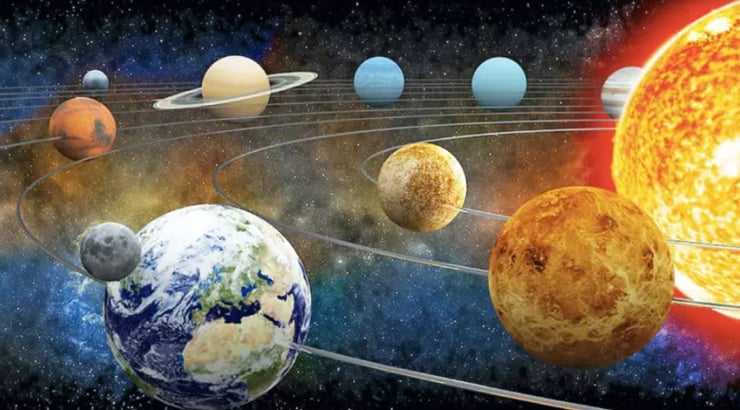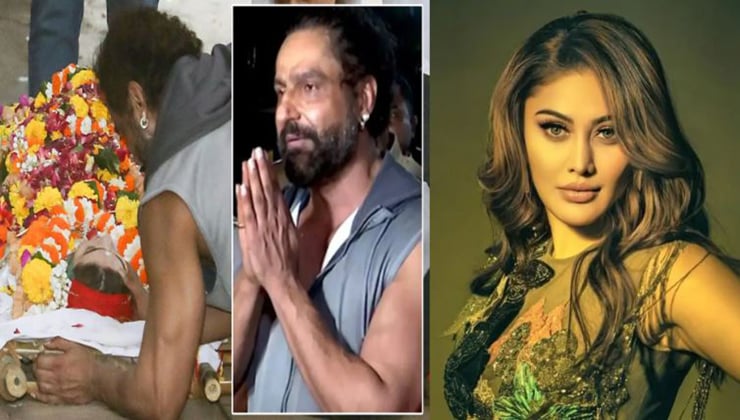উচ্চ আদালতে বিচারক নিয়োগ: প্রসঙ্গ বিচার বিভাগ সংস্কার
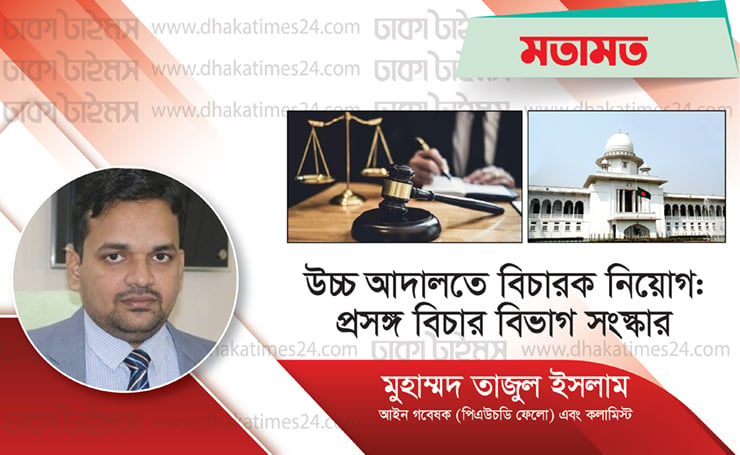
বাংলাদেশে উচ্চ আদালতে বিচারক নিয়োগ নিয়ে বিগত কয়েক দশকে দলীয়করণ, স্বজনপ্রীতি ও অস্বচ্ছতার মারাত্মক অভিযোগ রয়েছে। বিচার সংশ্লিষ্টদের মাঝে তথা মানুষের মনে কোনো সন্দেহ রেখে বিচারক নিয়োগদান কোনোদিন সুখকর নয়। বিষয়টি আরও সুস্পষ্ট হয়েছে গত ৫ই আগস্ট স্বৈরাচারী আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পরে। রাজনীতির প্রেক্ষাপট বদলে যাবার কারণে রাজনৈতিক নেতাদের মতো বিচারকদের যা অবস্থা হয়েছে তা কোনোভাবেই কাম্য নয়। মোটাদাগে আইনের শাসনের পরিপন্থিও বটে। যদিও আমাদের দেশে বিচারালয় নিয়ে রাজনীতির চর্চা নতুন নয় তবে সকলেরই উচিত বিচার বিভাগকে রাজনীতির বাইরে রাখা। সকল বিতর্কের উর্ধ্বে রাখা। মনে রাখতে হবে বিচারালয় হলো মানুষের ভরসার শেষ আশ্রয়স্থল। উচ্চ আদালতে আইন জানা, দক্ষ এবং যোগ্য বিচারক নিয়োগ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শর্ত।
বাংলাদেশের সংবিধানে রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতির সাথে পরামর্শের পর এ নিয়োগ দেন। সংবিধানে বিচারক নিয়োগে কিছু সুনির্দিষ্ট শর্তাবলির উল্লেখ আছে। তাছাড়াও ৯৫ (২) (গ) নং অনুচ্ছেদমতে আইনের দ্বারা শর্তাবলি নির্ধারণের বিষয় রয়েছে। বিগত পঞ্চাশ বছরে এই উপ-অনুচ্ছেদের অধীনে আজও কোনো আইন প্রণয়ন করা হয়নি। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৫ (২) (গ)-এর অধীনে বিচারক নিয়োগের নতুন শর্তাবলি নির্ধারণ সম্বলিত আইন প্রণয়ন ব্যতীত রাষ্ট্রপতির প্রধান বিচারপতির সঙ্গে পরামর্শ এবং এমন পরামর্শের ফলাফল কী এবং ৯৫ (২) (খ) নং অনুচ্ছেদমতে অধস্তন আদালতের বিচারক হিসেবে চাকুরির ১০ বছর অথবা ৯৫ (২) (ক) নং অনুচ্ছেদ মতে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী হিসেবে অভিজ্ঞতার ১০ বছর, কীভাবে গণনা করা হবে, অভিজ্ঞতা বা চাকুরির মেয়াদের সাথে অতিরিক্ত কোনো শর্ত যোগ হবে কি না তা সরকার আইন বা অধ্যাদেশ বা ঘোষণা দ্বারা নির্ধারণ করতে পারেন।
যুক্তরাজ্য তার সাতশত বছরের ইতিহাস ভেঙে ২০০৬ সালে এবং পাকিস্তান তার সংবিধানের অষ্টাদশতম সংশোধনীর মাধ্যমে ২০১০ সালে বিচারক নিয়োগের সুপারিশের জন্য বিশেষ বিচার বিভাগীয় কমিশন গঠনের ব্যবস্থা করেছে। তবে অস্ট্রেলিয়া ও কানাডায় বিচার বিভাগীয় নিয়োগ পুরোপুরি নির্বাহী ক্ষমতার অন্তর্গত, যদিও তা নিয়োগকৃতদের একাডেমিক, পেশাগত ও ব্যক্তি চরিত্রগত গুণাবলির প্রয়োজন সম্বলিত নীতিমালা দ্বারা শর্তায়িত। আমাদের দেশে উচ্চ আদালতে বিচারক নিয়োগে যত সমস্যা ।
মোটাদাগে বিচার বিভাগ তথা আমাদের উচ্চ আদালতে প্রধানত ৪/৫টি সমস্যা দেখি। তা হলো প্রথমত, বিচারক নিয়োগে চরম অস্বচ্ছতা, স্বেচ্ছাচারিতা ও দলীয়করণ; দ্বিতীয়ত, বিচারিক কাজে নির্বাহী বিভাগের প্রভাব; তৃতীয়ত, উচ্চাদালতের সহায়ক কর্মচারীদের বেপরোয়া দুর্নীতি ও আদালত ব্যবস্থাপনায় বিশৃঙ্খলা; চতুর্থত, মামলা নিষ্পত্তিতে অনাকাক্সিক্ষত বিলম্ব; এবং পঞ্চমত, বিচারকদের সাংবিধানিক শপথের প্রতি অঙ্গীকারের অভাব। তবে এতসব সমস্যার মধ্যে আজকের আলোচ্য বিষয় থাকবে বিচারক নিয়োগে সীমাহীন অস্বচ্ছতা, স্বেচ্ছাচারিতা ও দলীয়করণ নিয়ে।
প্রথমত- বিচারক নিয়োগে সীমাহীন অস্বচ্ছতা, স্বেচ্ছাচারিতা ও দলীয়করণ, এটা একটা বিরাট সমস্যা। উচ্চ আদালত সংশ্লিষ্টরা বলছে, বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের দীর্ঘ শাসনামলে সংবিধান-এর ৯৫ (১) অনুচ্ছেদের ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি হাইকোর্ট-এ ৭০ জন-এর অধিক অস্থায়ী বিচারক নিয়োগ দেন। যারা প্রায় সকলেই আওয়ামী লীগ সরকারের ও দলের ঘনিষ্ট এবং ছাত্র জীবনে ও পেশা জীবনে পেশাজীবী লেজুরবৃত্তিক রাজনীতির সাথে জড়িত ছিল তাদেরকে হাইকোর্ট-এর বিচারক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করে।
সংবিধান ও আইনানুযায়ী উচ্চ আদালতে বিচারকগণ অস্থায়ী ভিত্তিতে ২ বছরের জন্য নিয়োগ পান। অনেক সময় দেখা যায় ২ বছর পরে যখন স্থায়ীকরণ হয় তখন একের অধিক বিচারককে স্থায়ী করা হয় না তা অনেকেরই জানা। এখানে অস্থায়ী বিচারককে স্থায়ী না করার পিছনে কিছু নিয়ামক কাজ করে। যেমন যখন যে সরকার নিয়োগ দেন বিচারকালে যদি উক্ত বিচারক দলীয় এজেন্ডা বাস্তবায়ন না করেন বা যদি নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষকে সন্তষ্ট করতে ব্যর্থ হন বা তার বিরুদ্ধে যদি করাপশনের অভিযোগ পাওয়া যায় ইত্যাদি। যেহেতু রাষ্ট্রপতি ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্স অনুযায়ী ১ নং ব্যক্তি ফলে তিনি কাকে স্থায়ী করবেন আর কাকে করবেন না তা জিজ্ঞাসা করা যায় না- বিধায় কী কারণে কাউকে বিচারপতি পদে স্থায়ী করা হয় না তা অজানা থাকে। অনেকে স্থায়ী বিচারপতি হতে না পেরে রিট দায়ের করে থাকেন তবে তাতে খুব একটা যে লাভ হয়েছে তা প্রতীয়মান হয়নি।
উচ্চাদালত সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলি থেকে যে বিষয়গুলো প্রণিধানযোগ্য সেগুলো হচ্ছে (১) বিচারক নিয়োগে চরম অস্বচ্ছতা, স্বেচ্ছাচারিতা ও দলীয়করণ; (২) বিচারিক কাজে নির্বাহী বিভাগের প্রভাব; (৩) উচ্চাদালতের সহায়ক কর্মচারীদের বেপরোয়া দুর্নীতি ও আদালত ব্যবস্থাপনায় বিশৃঙ্খলা; (৪) মামলা নিষ্পত্তিতে অনাকাক্সিক্ষত বিলম্ব; এবং (৫) বিচারকদের সাংবিধানিক শপথের প্রতি অঙ্গীকারের অভাব।
আমাদের সংবিধানের ৯৪ (৪) নং অনুচ্ছেদে প্রধান বিচারপতি এবং অন্যান্য বিচারক বিচারকার্য পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এছাড়া ১১৬/ক অনুচ্ছেদে বিচার-কর্মবিভাগে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ এবং ম্যাজিস্ট্রেটগণ বিচারকার্য পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকবেন বলেও সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪৭ (২) অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্টের একজন বিচারকের কার্যভারকালে তাঁর পারিশ্রমিক, বিশেষ-অধিকার ও কর্মের অন্যান্য শর্তের এমন তারতম্য করা যাবে না, যা তাঁর পক্ষে অসুবিধাজনক হতে পারে। উচ্চ আদালতের বিচারকদের পারিশ্রমিক ইত্যাদির রক্ষাকবচ থাকা এবং সাংবিধানিকভাবে বিচারিক স্বাধীনতার সুস্পষ্ট ঘোষণা সত্ত্বেও বিগত স্বৈরাচারী সরকারের সময় তো বটেই এমনকি অন্যান্য সরকারের সময়ও আমাদের উচ্চ ও অধস্তন আদালতের বিচারকগণ তাঁদের বিচারকার্যে স্বাধীনতার কতটুকু প্রতিফলন ঘটাতে চেয়েছেন বা পেরেছেন তা একটি প্রশ্নবিদ্ধ ও বিতর্কিত বিষয়। সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে বিচার বিভাগের বিচারিক কার্যক্রমেও তার প্রতিফলন ঘটতে দেখা যায়। এটি কাম্য নয় এবং এটির দ্বারা বিচার বিভাগের ওপর নির্বাহী বিভাগের সুস্পষ্ট প্রভাব প্রমাণিত হয়।
একটি স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ বিচার-আদালতে প্রকাশ্য শুনানি লাভের অধিকারকে একটি সর্বজনীন মানবাধিকার বলে ঘোষণা করে জাতিসংঘের মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষনাপত্রের ১০ অনুচ্ছেদে এবং বাংলাদেশ সংবিধানের ৩৫(৩) নং অনুচ্ছেদে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ আদালতে বা ট্রাইব্যুনালে দ্রুত ও প্রকাশ্য বিচার লাভের অধিকারকে একটি মৌলিক অধিকার হিসেবে নিশ্চয়তা দেয়। এ অধিকারগুলো সঠিকভাবে উপভোগ করতে দরকার স্বচ্ছতার ভিত্তিতে উচ্চ আদালতে বিচারক নিয়োগ যা স্বৈরাচারের যাতাকলে এতদিন নিষ্পেষিত ছিল। উচ্চ আদালতে বিচারক নিয়োগ করার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকার অতি দ্রুত কিছু পদক্ষেপ নিতে পারেন। যেমন:
১। আমাদের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৫ (২) (খ)-এর অধীনে বর্তমানে সুপ্রিম কোর্টের বিচারক হিসেবে নিয়োগ লাভের জন্য অধস্তন আদালতে চাকুরির অভিজ্ঞতা ১০ (দশ) বছর বিশেষভাবে বুঝতে ও গণনা করতে হবে। এই ১০ (দশ) বছর পুরোটাই বিচার কাজে নিয়োজিত অবস্থায় থাকতে হবে, কোনো বিচার বিভাগীয় প্রশাসন যেমন, আইন মন্ত্রণালয়, বা অন্য কোনো সরকারি সংস্থায় কর্মের সময় গণনায় আনা যাবে না। উল্লিখিত ১০ (দশ) বছরের মধ্যে অবশ্যই ন্যূনতম তিন বছর জেলা জজ বা সম পর্যায়ের বিচারক হিসেবে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হতে হবে।
২। অনুচ্ছেদ ৯৫(২) (ক)-এর অধীন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী হিসেবে কর্মকালের ১০ (দশ) বছরও বিশেষভাবে বুঝতে এবং পড়তে হবে। আদালতে ১০ (দশ) বছরের জন্য নিছক অন্তর্ভুক্তি যথেষ্ঠ বিবেচিত হবে না। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মামলা সফলভাবে পরিচালনাসহ তাঁকে নিয়মিত সক্রিয়ভাবে প্র্যাকটিস করতে হবে, যা প্রধান বিচারপতি ও তাঁর সহবিচারপতিবৃন্দ নির্ধারণ করবেন। এছাড়া কমপক্ষে দুই বছর আপিল বিভাগে মামলা পরিচালনায় অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
৩। ৯৫ (২) (ক) ও ৯৫ (২) (খ)-এর অধীন আইনজীবী ও বিচারক ছাড়াও ৯৫ (২) (গ)-এর অধীন কোনো আইনজ্ঞ, যেমন আইনের অধ্যাপক বা আইনের গবেষক, যার প্রাতিষ্ঠানিক পরিচয় রয়েছে, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হিসেবে নিয়োগের জন্য বিবেচিত হতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর বয়সের নিম্ন সীমা হবে পয়তাল্লিশ (৪৫) বছর।
৪। সুপ্রিম কোর্টে অধস্তন আদালত হতে বিচারক নিয়োগের আনুপাতিক সংখ্যা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।
৫। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৮-এর অধীন হাইকোর্ট বিভাগে অস্থায়ী মেয়াদে অতিরিক্ত বিচারক নিয়োগ এবং হাইকোর্ট বিভাগ হতে অস্থায়ী মেয়াদে কোনো বিচারকের আপিল বিভাগে আসন গ্রহণের বিধান যুক্তিসংগত কারণে বিচার বিভাগের স্বাধীনতার ধারণার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয় বিধায় সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে তা বিলুপ্ত করা প্রয়োজন।
৬। বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রধান বিচারপতির সঙ্গে ‘পরামর্শ’ নিছক আভিধানিক অর্থে নয়, বরং তা সাংবিধানিক ও বিচার বিভাগীয় ধ্যান ধারণায় বিশেষ অর্থে পড়তে ও বুঝতে হবে (উল্লিখিত প্যারা ৭-এর বর্ণনা মতে), যার ফলে ‘পরামর্শ’ হয়ে উঠতে পারে অর্থবহ ও কার্যকর। এজন্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রধান বিচারপতির পরামর্শ চাওয়া এবং প্রধান বিচারপতির পরামর্শ প্রদান প্রক্রিয়া হতে হবে স্বচ্ছ ও লিখিতভাবে যাতে তার উপর সামাজিক পর্যবেক্ষণ সম্ভবপর হয়।
৭। সুপ্রিম জুডিসিয়াল কমিশন অধ্যাদেশ জারি করে সুপ্রিম কোর্টের উভয় বিভাগে বিচারক নিয়োগে স্বচ্ছতা ও ন্যায্যতা নিশ্চিত করা যাতে করে কেবল উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিরাই এ বিভাগে বিচারক হিসেবে নিয়োগ লাভ করতে পারেন।
৮। সংবিধানের পুনরুজ্জীবিত ৯৬ নং অনুচেছদ অনুসারে সুপ্রিম জুডিসিয়াল কাউন্সিলকে কার্যকর করা। ষোড়শ সংশোধনীর রায়ের বিরূদ্ধে আপিল বিভাগে সরকার কর্তৃক কোনো রিভিউ দায়ের করা থাকলে অবিলম্বে তা প্রত্যাহার করা। এ বিষয়ে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের প্রয়োজনীয় সহায়তা নেওয়া যেতে পারে।
৯। রুলস অব বিজনেস এবং এলোকেশনশ অব বিজনেস সংশোধন করে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন বিচার বিভাগ নামীয় একটি বিভাগ সৃজন করে তার নিয়ন্ত্রণ বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের অধীন ন্যস্ত করা যেতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের কথা বলা যায়। বিচার বিভাগই বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের কার্যকর নিয়ন্ত্রণ করবে।
১০. বিচার বিভাগের জন্য পর্যাপ্ত তহবিল বরাদ্দ করা এবং প্রয়োজনীয় লোকবল ও সরঞ্জাম নিশ্চিত করাও এখন সময়ের দাবি।মুহাম্মদ তাজুল ইসলাম: কলাম লেখক ও আইন গবেষক
 ঢাকা টাইমস অনলাইন এর সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিডটি ফলো করুন
ঢাকা টাইমস অনলাইন এর সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিডটি ফলো করুন
মন্তব্য করুন