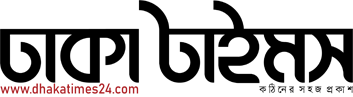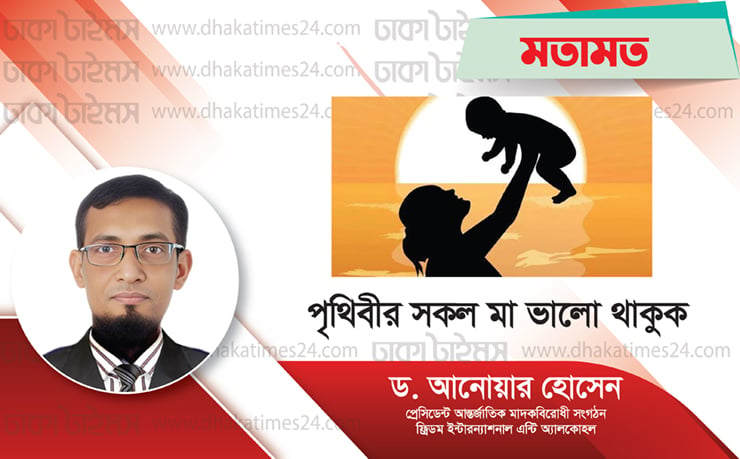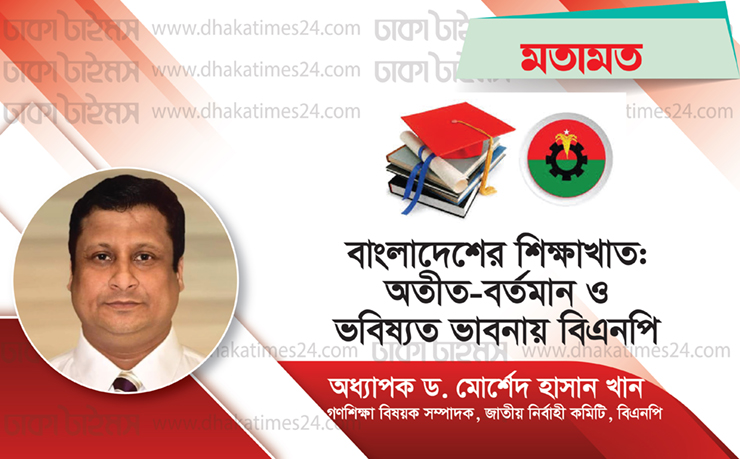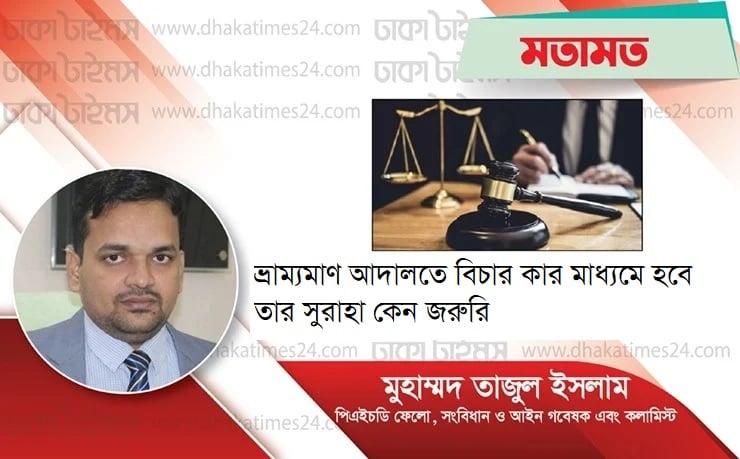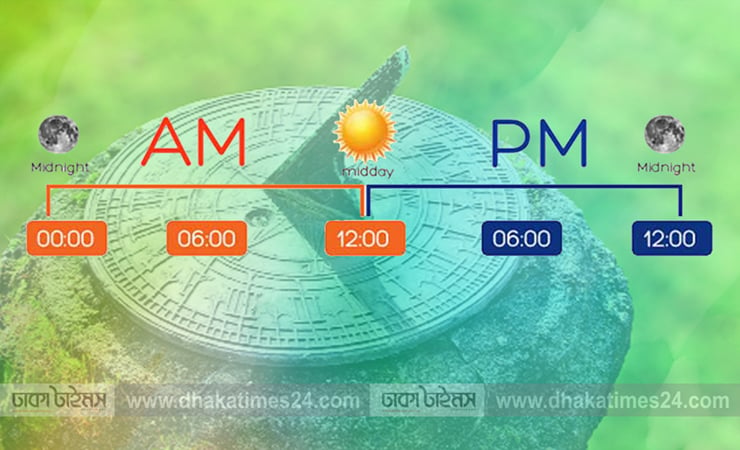গার্মেন্টস শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি এতটা ন্যূনতম কেন?

বিদেশে রপ্তানিযোগ্য বাংলাদেশের অর্থনৈতিক আয়ের সবচেয়ে বড়ো উৎস হচ্ছে গার্মেন্টস শিল্প। এই পোশাকশিল্প বাংলাদেশের মানুষের জীবনমান ও অর্থনৈতিক চাকাকে অধিকমাত্রায় সচল করে রেখেছে, এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়। বিদেশে রপ্তানিযোগ্য আমাদের দেশের অর্থনৈতিক আয়ের মধ্যে সিংহভাগ আয়ই আসে এই গার্মেন্টস শিল্প থেকে। আশির দশকের পর থেকে এই পোশাকশিল্প আমাদের সাধারণ মানুষের জীবনমান বৃদ্ধি করেছে আশাতীতভাবে এবং সমৃদ্ধ করেছে গ্রাম ও শহরসহ আমাদের জাতীয় অর্থনীতি। গ্রামের সাধারণ মানুষ- বিশেষ করে লক্ষ লক্ষ নারী আজ আয়ের একটি বড়ো জায়গা তৈরি করতে পেরেছে গার্মেন্টস শিল্পে নিজেদের যুক্ত করার মাধ্যমে। এই উন্নয়নশীল দেশে রপ্তানি শিল্পের উৎকর্ষসাধনে সবচেয়ে বড়ো ভূমিকাই যেখানে রাখছে এই পোশাক শিল্পখাতের শ্রমিকরা সেখানে এই বিপুলসংখ্যক শ্রমিকের অবদানকে কোনোভাবেই খাটো করে দেখবার কি কোনো অবকাশ আছে?
চলতি বছরের অক্টোবর-নভেম্বরে বেতন বৈষম্য নিয়ে শুরু হয় শ্রমিক-মালিক অসন্তোষ। এই অসন্তোষ এক মাসেরও অধিককাল ধরে চলতে থাকে; এতে করে মালিক শ্রমিক উভয়ই ক্ষতিগ্রস্তে নিপতিত হয়। মালিক-শ্রমিক অসন্তোষের কারণে নিহতও হয় বেশ কয়েকজন শ্রমিক। ক্ষতি হয় শিল্প-কারখানাসহ দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের বিভিন্ন সম্পদ। এমনিতেই রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতায় বিভিন্ন সময় হরতাল-অবরোধে দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় দেশের জাতীয় অর্থনীতি, তার ওপর এই শ্রমিক অসন্তোষে মাঝে-মাঝেই গার্মেন্টস খাতও হয়ে ওঠছে বিস্ফোরোণ্মুখ। এ সময় রাস্তাঘাটে সাধারণ মানুষের চলাচল ব্যবস্থা হয়ে পড়ে ভীষণ রকমের সমস্যা-সংকুল। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা একসময় একটা সমাধানের দিকে যায় হয়তো কিন্তু শ্রমিকের আশানুরূপ বেতন বৈষম্যের কোনো সমাধান হয় না। আয়ের সঙ্গে ব্যয়ের তুলনামূলক যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় শ্রমিকদের যাপিত জীবনে তা এক কথায় খুবই অমানবিক।
শ্রমিকের শ্রমে ও ঘামেই এই শিল্পের বিকাশ ঘটেছে তা স্বীকার না করে উপায় আছে কি? ’৮০ দশক থেকে বর্তমান সময়ে এসেও শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি এখনো প্রতিষ্ঠিত হলো না- এটা দুঃখজনক। একমাত্র গার্মেন্টস শিল্পে সবচেয়ে কম মজুরি দিয়ে পোশাক তৈরি করে পুঁজিপতিরা রাতারাতি অর্থের পাহাড় গড়ছে। অথচ অন্যদিকে বর্তমান সময়ে এসে যে বেতন কাঠামো নির্ধারণ করা হয়েছে শ্রমিকদের জন্য তা নিতান্তই অপ্রতুল।
কিছুদিন পূর্বে বাস্তবায়িত শ্রমিকদের বেতন কাঠামোতে গার্মেন্টস শ্রমিকদের জন্য মজুরির ৫টি গ্রেড রাখা হয়েছে। গ্রেড-১ এ ৮০০০ হাজার ২০০ টাকা মূল মজুরিতে শ্রমিকের মোট বেতন দাঁড়িয়েছে ১৪ হাজার ৭৫০ টাকা। গ্রেড-২ এ ৭০০০ হাজার ৮০০ টাকা মূল মজুরিতে মোট বেতন হবে ১৪ হাজার ১৫০ টাকা। গ্রেড-৩ এ ৭০০০ হাজার ৪০০ টাকা মূল মজুরিতে মোট বেতন হবে ১৩০০০ হাজার ৫০০ টাকা। গ্রেড-৪ এ ৭০০০ হাজার ৫০ টাকা মূল মজুরিতে বেতন হবে ১৩০০০ হাজার ২৫ টাকা। সর্বনিম্ন গ্রেড- ৫ এ ৬০০০ হাজার ৭০০ টাকা মূল মজুরিতে একজন শ্রমিকের বেতন হবে ১২,৫০০/- টাকা। বলার অপেক্ষ রাখে না- এই সময়ের বাজারব্যবস্থা, বাসা ভাড়া, চিকিৎসা ও অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করলে খুবই নগণ্য এই নতুন নির্ধারিত বেতন কাঠামো। প্রকাশ থাকে যে, ৫৬.২৫% শ্রমিকের বেতন ১২,০০০ হাজার ৫০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে; যা ১লা ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে কার্যকর হয়েছে। মালিক পক্ষের দাবি পূরণ করে সরকার এই প্রজ্ঞাপন জারি করে কিন্তু শ্রমিকের দাবি অপূর্ণই রয়ে যায়। পক্ষান্তরে শ্রমিক সংগঠনও এই দাবি মানতে বাধ্য হয় কিন্তু তা যথাযথ হয়েছে কি না তা ভেবে দেখার বিষয়।
পৃথিবীর কোনো দেশই শ্রমিকের বেতন এত নিম্নমানের নয়। আমাদের দেশ থেকে জনশক্তি রপ্তানি করে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি করছে সরকার- যা রাজস্ব আয়ে বড়ো ধরনের ভূমিকা রাখছে। এখানে এই বিষয়টিই বুঝতে হবে যে- বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শ্রমিকের ন্যায্য মজুরি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলেই তো তাদের আয়ের একটা বড়ো অংশ আমাদের সরকার রেমিট্যান্স হিসেবে পাচ্ছে। যদি বৈদেশিক আয় না হতো, শ্রমিকের মজুরি বেশি না হতো তবে রেমিট্যান্সের মাধ্যমে রাজস্ব আয় কি এতটা বাড়তো কোনোভাবেই?
গত ৭ই নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী বিদেশ থাকাকালে মজুরি বোর্ডের ষষ্ঠ বৈঠকের পরই একইদিনে তড়িঘড়ি করে শ্রম প্রতিমন্ত্রী ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা দিলেন ১২ হাজার ৫০০ টাকা। এর পরপরই শ্রমিকরা এই ন্যূনতম বেতন নিয়ে অনেকগুলো প্রশ্ন তোলেন। বর্তমানে সাধ্যের চেয়েও বেশি টাকা দরে বিক্রি হওয়া পেঁয়াজ-মরিচ ও অন্যান্য নিত্যপণ্যের যুগে এ মজুরি কি যথার্থ? শ্রমিকরা বলছেন, ৮০ টাকার তেল এখন ১৮০ টাকা, ৫০ টাকার চিনি ১৫০ টাকা, ৬০ টাকার ডাল ১৪০ টাকা, সবকিছুর দাম যখন দুই-তিন গুণ; তখন আগের ৮ হাজার টাকার মজুরি কেন ৫ বছরে পরে মাত্র ১২ হাজার ৫০০ টাকায় নির্দিষ্ট হবে? শ্রমিকদের বলতে শোনা যায়, ‘আমার বেতন এখন ১২ হাজার টাকা, অথচ খরচ ১৭ হাজার টাকা, ঋণ ৫ হাজার টাকা। বাড়িতে বাবা-মাকে পাঠামু কী, আর সংসারই-বা চালামুই বা কীভাবে?’ পোশাক শিল্পে এ ধরনের শ্রমিকের সংখ্যাই ৮০ শতাংশ, যারা উচ্চসুদে ঋণ করে বেঁচে থাকে এবং পোশাক খাতের প্রায় ৯০ শতাংশ শ্রমিকই তাদের সন্তানের শিক্ষার খরচ বহন করতে অপারগ হয়।
আমি বলতে চাই, আমাদের গার্মেন্টস শ্রমিকদের যে বেতন নির্ধারণ করা হয়েছে তা তাদের জন্য কোনোভাবেই ন্যায্য বেতন হতে পারে না- অন্তত বর্তমান বাজার দর অনুযায়ী মানুষের ন্যূনতমভাবে বেঁচে থাকার জন্য তো নয়ই। বেতন কাঠামো শ্রমিকদের ন্যূনতমভাবে জীবনযাপনে কতটুকু শর্ত পূরণ করেছে তা বিশেষজ্ঞদের ভাববার বিষয় বলে আমি মনে করি। বর্তমান সময়ে প্রতিটি দ্রব্যমূল্যের ক্রমাগত ঊর্ধ্বগতিতে একজন শ্রমিকের বেঁচে থাকার জন্য হতাশা ছাড়া আর কিছু দেখি না। এর আশু উত্তরণ প্রয়োজন। এটা তো অস্বীকার করার কোনো জো নেই যে- শ্রমিক বাঁচলে কারখানা বাঁচবে। কারখানা বাঁচলে মালিকরা ফুলেফেঁপে বড়ো হবে এবং দেশ অর্থনীতিতে স্বয়ংসম্পুর্ণ হবে- এটাই তো বাস্তবতা।
আমার বোধগম্য নয় কোন যুক্তিতে মাত্র ১২,৫০০টাকা সর্বনিম্ন মজুরি করা হলো! বাংলাদেশ শ্রম আইনের ১৪১ ধারা অনুসারে যে ১২টি সূচকের ওপর নির্ভর করে শ্রমিকের মজুরি নির্ধারণ হওয়ার কথা, তার মধ্যে মুদ্রাস্ফীতি, জীবনযাপনের মান, শ্রমিকের জীবনযাপন ব্যয়, শিল্পের সক্ষমতা ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত আছে। আজকের বাজারের যে বাস্তবচিত্র তার সঙ্গে ঘোষিত মজুরি কি কোনোভাবেই সামঞ্জস্যপূর্ণ? কারণ গত ১২ বছরে খাদ্য মুদ্রাস্ফীতি ও টাকার মুদ্রাস্ফীতি দুই-ই হয়েছে রেকর্ড পরিমাণ। গত পাঁচ বছরে ভোক্তা মূল্যসূচক বেড়ে হয়েছে ৩৫ শতাংশের ওপরে। ফলে শ্রমিকদের মধ্যে একটি বড়ো অংশের জীবনমান দারিদ্র্যসীমার অনেক নিচে নেমে গেছে, অনেক শ্রমিক নতুন করে অপুষ্টির মধ্যে পড়েছে। এসবই জাতীয় গণমাধ্যমের রিপোর্ট থেকে নেওয়া বাস্তবচিত্র।
দেখা যায়, ২০১৮ সালে ৮ হাজার টাকার মজুরি দিয়ে যে ধরনের জীবনযাপন করতে পারত শ্রমিকরা, তা এখন কমে গেছে ৩ হাজার ৫৯ টাকার পরিমাণে। অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতি বিবেচনায় নিলে ২০১৮ সালের ৮ হাজার টাকা এখন হয়েছে ১২ হাজার টাকার কাছাকাছি। এ হিসাবে ধরলে শ্রমিকের মজুরি বেড়েছে মাত্র ৫০০ টাকা। যারা বলছেন মজুরি বেড়েছে ৫৬ শতাংশ, সেটি কি আসলে ঠিক হিসাব? আসলে শ্রমিকের মজুরি বাড়েনি, শুধু পঞ্চম গ্রেডের শ্রমিকদের মজুরি মুদ্রাস্ফীতির সঙ্গে সমন্বয় হয়েছে মাত্র। আর অন্যান্য গ্রেডের শ্রমিকের মজুরি প্রস্তাব করা হয়েছে ৬ শতাংশ বৃদ্ধি হারে, বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাবে মুদ্রাস্ফীতি যেখানে ১০ শতাংশের কাছাকাছি, তখন ৬ শতাংশ মজুরি বৃদ্ধি কি মানবিকতাসম্মত? উল্লেখ করা দরকার, পোশাক খাতে অধিকাংশ শ্রমিক গ্রেড ৪, ৩, ২, ১-এ কাজ করেন। বৃহত্তর অংশের এ শ্রমিকদের মজুরি তেমন বাড়েনি। ফলে এ নির্ধারিত মজুরি শ্রমিকদের গণহারে ক্ষুধা, অপুষ্টি এবং দারিদ্র্যের দিকেই ঠেলে দেবে বলে মনে করি।
জীবনমানের পরিসংখ্যান বলছে, সর্বশেষ ঘোষিত মোট মজুরি শ্রমিকের শুধু খাবার খরচের থেকেও অনেক কম! খাদ্য ও পুষ্টিবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার হিসাব অনুযায়ী, পূর্ণ বয়স্ক একজন শ্রমিক যে ১০ ঘণ্টা কাজ করেন, তার দরকার তিন হাজার কিলোক্যালরি। এ পরিমাণ খাবার ও অন্যান্য পণ্য কিনতে কোনোভাবেই ১২ হাজার ৫০০ টাকা দিয়ে সম্ভব না। শ্রমিকের সন্তানের জন্য শিক্ষা বাবদ কোনো খরচ ধরা হয়নি, আর চিকিৎসা বাবদ খরচ ধরা হয়েছে ৭৫০ টাকা, (মজুরি গেজেট, ১১ নভেম্বর, ২০২৩)। যেখানে বাংলাদেশে গড় মাথাপিছু স্বাস্থ্য বাবদ ব্যয় ৫ হাজার ৯৭৫ টাকা (৫৪ ডলার, ১ ডলার সমান ১১০ দশমিক ৩২ পয়সা হিসেবে), যারা বিদেশে চিকিৎসা করে তাদের ৫ লাখ ৫১ হাজার ৬০০ টাকা। তাহলে মালিকরা বিদেশে চিকিৎসা করবেন আর শ্রমিক শুধু ফার্মেসিতে ওষুধ কিনে খাবেন, ডাক্তার দেখানোর অধিকারও তাদের থাকবে না- এটাই কি মানবতা! কারণ এ টাকায় তো একজন শ্রমিক এমবিবিএস ডাক্তারও দেখাতে পারবে না।
ইতোমধ্যেই আন্তর্জাতিক শ্রম অধিকার সংস্থাগুলো সর্বশেষ মজুরিবোর্ড নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। তারা বলতে চায়, মজুরি নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় শ্রমিকের অংশগ্রহণ কার্যকরভাবে নিশ্চিত করা হয়নি। ফলে ঘোষিত মজুরিতে শ্রমিকের বাস্তব প্রয়োজনের কোনো প্রতিফলন ঘটেনি। যেহেতু ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশে উত্তরণ ঘটেছে বাংলাদেশের, শ্রমিকের মজুরিটাও স্মার্ট হতে হবে এবং মজুরি বোর্ডের কার্য প্রক্রিয়াও ডিজিটাল হতে হবে। এটাই সকলে আশা করে।
আমি চাই, শ্রমিকদের বাস্তব প্রয়োজনের নিরিখে শ্রম আইন অনুসারে একটি যৌক্তিক মজুরি পুনঃনির্ধারণ করা হোক। অন্যথায় অভুক্ত, অপুষ্টিতে ভোগা শ্রমিকদের দিয়ে কাক্সিক্ষত লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হবে না। মনে রাখা দরকার যে- আমাদের তৈরি উৎপাদিত পণ্য বিদেশি বিনিয়োগকারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে যদি একজন শ্রমিক তার প্রাপ্য বেতনে সন্তুষ্টি প্রকাশ করে। কারণ এতে তাদের কাজের গতি আরও বাড়বে এবং কাজের গুণগত মান আরও উন্নত হবে। আর প্রোডাকশন বাড়লে মালিকের মুনাফা বৃদ্ধিসহ দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক আয়ের পথই অনেকখানি সুগম হবে।আনিসুর রহমান খান: গীতিকবি, সাংবাদিক ও কলাম লেখক
 ঢাকা টাইমস অনলাইন এর সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিডটি ফলো করুন
ঢাকা টাইমস অনলাইন এর সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিডটি ফলো করুন
মন্তব্য করুন