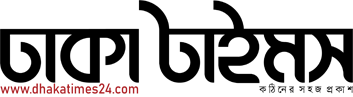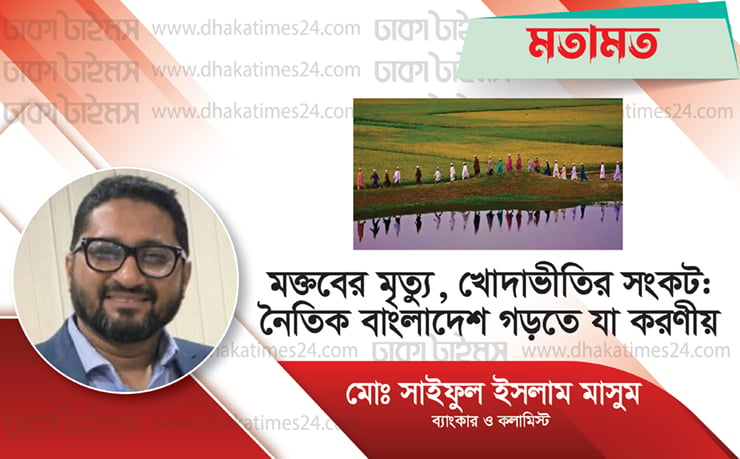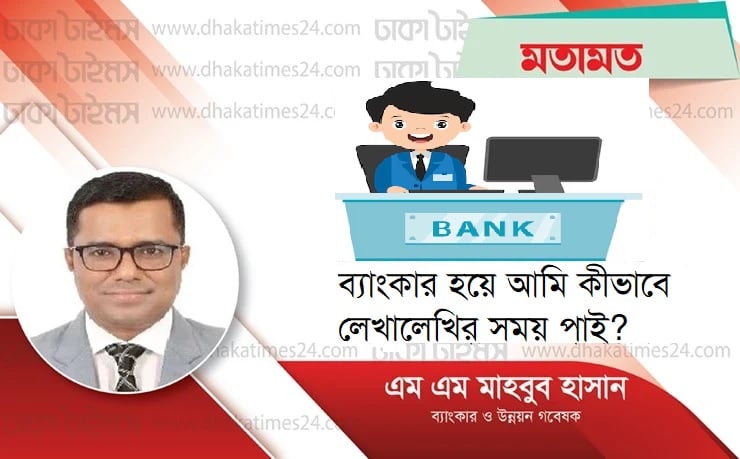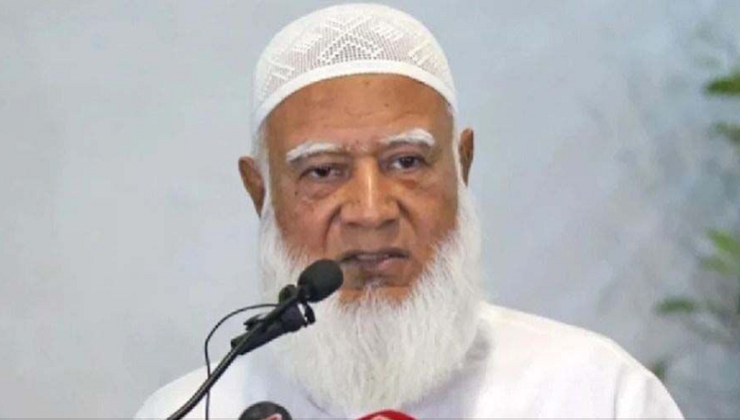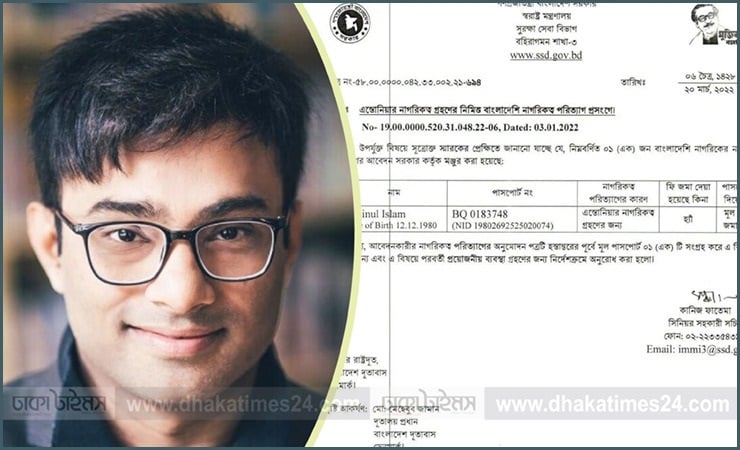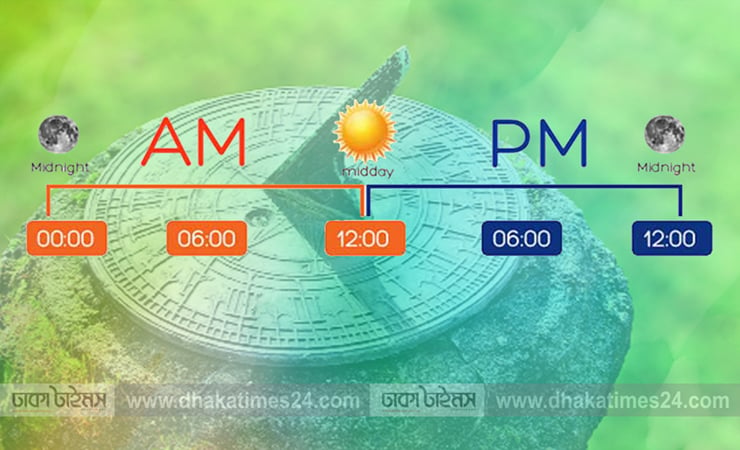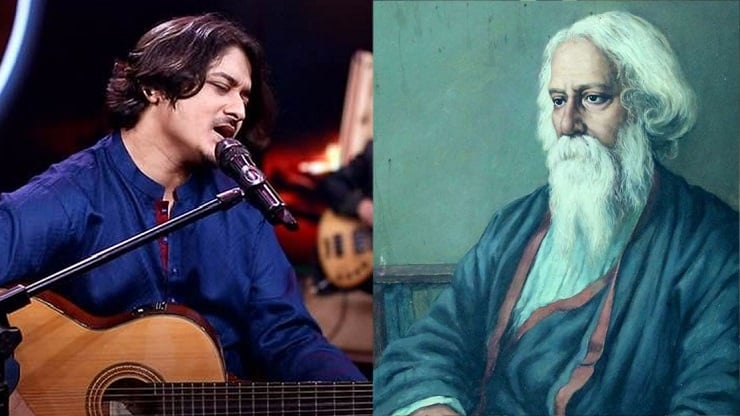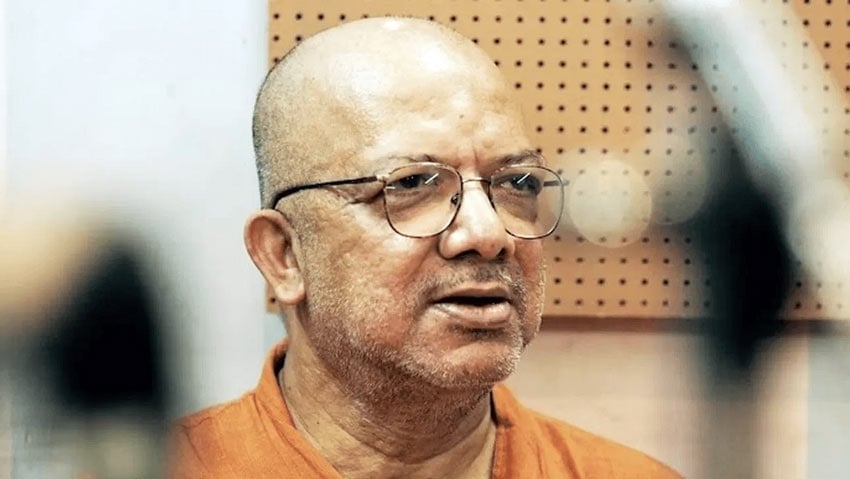গ্রামভিত্তিক ‘শিল্পকলা একাডেমি’ ভাবনা সময়ের দাবি
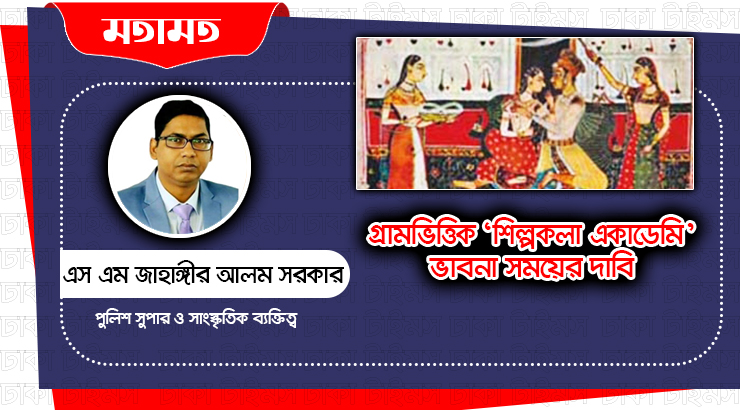
রাষ্ট্র তখনই সমৃদ্ধিশালী হয় যখন সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিক অবাধ মেধাচর্চা, সুস্থ ধারার বিনোদন, মুক্ত সংস্কৃতি চর্চার সুযোগ লাভ করে। আমাদের দেশে বেশির ভাগ মানুষের আবাসস্থল এখনো গ্রামে সেই দিকটা বিবেচনা করে বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গ্রামকেন্দ্রিক যে ভাবনা ‘গ্রামই হবে শহর’, অর্থাৎ মানবকল্যাণে ব্যবহৃত শহুরে সুযোগ-সুবিধাসমূহ গ্রামেও নিশ্চিত করা। নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে কেননা এমন ভাবনা থেকেই বোধকরি রবীন্দ্রনাথ শত বছর আগে বলেছিলেন ‘গ্রাম যেন শহরের উচ্ছিষ্টভুজি না হয়।’ আর সংখ্যাগরিষ্ঠ গ্রামের মানুষকে পিছিয়ে রেখে উন্নত বা আধুনিক রাষ্ট্র গঠন সম্ভব নয়। সরকার যে পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে তার সঙ্গে দরকার গ্রামে শিল্পকলা একাডেমির শাখা তৈরি করা এবং তাতে গ্রামে যারা বেড়ে উঠছে তাদেরকে সম্পৃক্ত করা।
গ্রামকে শিল্প-সাহিত্য-সাংস্কৃতিক চর্চার প্রাণকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সকল ধরনের গ্রামীণ সামাজিক এবং প্রশাসনিক পরিবেশ নিশ্চিত করা খুব জরুরি বলেই মনে হয়। যদি আমরা নিজস্ব সংস্কৃতির চেতনা চর্চা, বিকাশ এবং ইতিমধ্যে বিকশিত উৎকর্ষ আগামী প্রজন্মের জন্য একটি প্রকৃত সুন্দরকে উপহার হিসেবে দেখতে চাই। প্রকৃত সুন্দর মানুষের ভাবনাগুলোর মধ্যে অন্যতম ভাবনা হচ্ছে সে তার পরবর্তী প্রজন্মের জন্য আধুনিকমনা বাসযোগ্য সুন্দর একটি গ্রাম বা নগর রেখে যেতে চায়।
গ্রাম-বাংলার লোকজ সাহিত্য-সংস্কৃতি সেখানকার জনপদের সকল ধরনের বক্তব্য উপস্থাপন করে, শুধু তাই নয় আজকের আধুনিক সংস্কৃতি চর্চার এখনো বেশিরভাগ উপজীব্যই গ্রামীণ প্রকৃতি এবং জনপদ। ইট-পাথরের ব্যস্ততার শহরে নিজস্ব সাংস্কৃতিক যান্ত্রিকতার বাইরে শহরেও খুব বেশি জনপ্রিয় না হওয়ায় শহরের কিছু লেখকের অনেকেই গ্রামের চিত্র উপস্থাপন করতেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে।
বাংলার লোকজ ঐতিহ্যের আভিজাত্য অহংকার করার মতো এবং এতটাই সমৃদ্ধ যা অপসংস্কৃতি রোধে মহাওষুধ হিসেবে কার্যকর। এমন আশঙ্কা থেকেই সিনেমা হল কিংবা রমনার বটমূলে বোমা হামলা হয়েছে বলে অনেকেই একমত পোষণ করবে এটাই স্বাভাবিক। যারা দ্বিমত পোষণ করেন তারা কোনো না কোনোভাবে অপসংস্কৃতি দ্বারা বেশি আসক্ত কিংবা অতি আবেগতাড়িত। কারণ তারা জানে বাংলা সংস্কৃতির মার্গীয় ক্ষমতা এতটাই যে রাতের অন্ধকারে মাফলার মুখে পেঁচিয়ে হলেও যাত্রাপালা না দেখলে ঘুম হয়নি অনেকের। কাজেই যত ছবকই সে তার পরিবারে দিয়ে থাকুক না কেন ঢোলের বারি পড়লে তথাকথিত সামাজিক ভয়ে দৌড়াতে না পারলেও মনটা তো আর আটকে রাখা যায় না কোনোভাবেই। এটা প্রমাণ করে দেখানোর কোনো ব্যাপার না, কারণ কমবেশি অভিজ্ঞতা এ দেশের বেশিরভাগ মানুষেরই আছে।
সংস্কৃতি চর্চাকে বাড়তে দেওয়া যাবে না এমন মনোভাবসম্পন্ন কিছু মানুষ আছে যাদের বিভিন্ন সময় দেখেছি মূল সংস্কৃতিকে ন্যক্কারজনকভাবে অপছন্দ করতে! একটু আলোচনা করা যেতেই পারে বাংলা সংস্কৃতি তাদের শত্রু হলো কেন কিংবা সংস্কৃতির মতো স্পর্শকাতর বিষয়টি অপছন্দের জন্য তারা বেছেই বা নিল কেন?
হাজার বছর ধরে কর্ষিত হয়ে আমরা যে অবস্থায় পেয়েছি তা এত বেশি জীবন্ত, এত বেশি সমৃদ্ধ আর হাজার রকম আধার উপজীব্য নানা রং রসে এমনভাবে পরিপূর্ণ যে, মানুষ তার নিজস্ব সংস্কৃতিতে খুব সহজেই সে নিজেকে খুঁজে পায়। জাতি, প্রথা, অঞ্চল, ধর্ম আর প্রকৃতির যুক্ত হওয়া অনুকূল কিংবা প্রতিকূল নানা বিষয় বিবেচিত হয়ে লোকজ সংস্কৃতি এতটাই সুন্দর ও মাধুর্যমণ্ডিত যে, সকলেই এঁর মধ্যে নিজের সক্রিয় অস্তিত্ব প্রেম-ভালোবাসা, দুঃখ-কষ্ট প্রয়োজনীয় সবটাই খুঁজে পায় খুব সহজে।
বাংলার লোকজ ঐতিহ্য যতটা বিচিত্র এবং সুন্দর বিশ্বের আর কোথায় এতটা মাধুর্য, এতটা বৈচিত্র্যময় লোকজ ঐতিহ্য আছে কি না তা আমার জানা নেই। বাংলার লোকজ ঐতিহ্য অঞ্চলভেদে নানা রকম স্বাদে-গন্ধে রূপে-রঙে রসে অনন্য এবং চলমান। বিদেশি সংস্কৃতি এবং আধুনিকতার ছোঁয়ায় কোথাও কোথাও খানিকটা ক্ষতিগ্রস্ত হলেও একেবারে নিঃশেষিত হয়নি এখনও।
কবিগান, যাত্রাপালা, পুঁথিপাঠ, লাঠির বারি, (কবিরাজি, মোরগ যুদ্ধ, সাপ খেলা প্রদর্শন, বেজি বানর যুদ্ধ) জারিসারি ভাটিয়ালি কাওয়ালি আদিবাসীদের বিশেষ কিছু উৎসব, বিয়ের গান সার্কাস নানা রকম রূপরস গন্ধের লোকজ ঐতিহ্য আমাদের চেতনা এবং পরিচিতির সাথে সরাসরি সম্পর্কিত। আবার হামদ-নাত-গজল, ভোজন, কীর্তন, শ্যামাসংগীত, বৈষ্ণব পদাবলী যুগে যুগে অভিন্ন। কবি যুগে নজরুল, রবীন্দ্র বাংলার নন্দিত পঞ্চ কবিখ্যাত কবি-সাহিত্যিকগণ যখন বাংলার সাহিত্য অঙ্গনে বিচরণ করেছেন তখন তাঁরা বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের সুর গীতি এগুলোকে বিবেচনায় নিয়ে লোকজ সুর বাণী শ্রুতি ইত্যাদির সুসমন্বয় ঘটিয়ে লোকজ নন্দনতত্ত্ব উপলব্ধি করে রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলসংগীত এবং আধুনিক গান রচনা করে সংগীত অঙ্গনকে বিশ্বদরবারে পরিচিত করেছেন।
আবার অঞ্চলভিত্তিক সুর ও বাণীর সমন্বয়ে পল্লীগীতি, ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া ইত্যাদি গানগুলোর মধ্যে বিশেষ বিশেষ অঞ্চল বিশেষায়িত রূপে প্রকাশিত হয়েছে যা লোকজসংগীত কলাকে অনেক পরিশীলিত ও সমৃদ্ধ করেছে নিঃসন্দেহে। সেই সাথে সুফি ও সাধক পুরুষদের আত্মকর্ষণ সাথে স্রষ্টা ও সৃষ্টি প্রেমের গুরু-রহস্যভিত্তিক আধ্যাত্মবাদী গান লালন সাঁইজি, সিরাজ সাঁইজি, বাউল কবি আবদুল করিম হাছন রাজারা বাউল চর্চায় বাংলার লোকজ গান বিশ্বের জন্য গবেষণার দ্বার উন্মুক্ত করে গেছেন। সেই সাথে ফকির, কাওয়ালি সাধুমত বিভিন্ন রকম লোকজ সাংস্কৃতিক স্কুলের ধারা ও বিশেষ আলোচনার ক্ষেত্র তৈরি করেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। দেশি-বিদেশি অনেকেই লালন গবেষণায় অনন্য অবদান রেখে চলেছেন সেটি এখন দৃশ্যমান। বাউল আবদুল করিমের সংগীত নিয়ে গবেষণার নামে পাশেই কলকাতা যেন রীতিসই যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছে। কাউকে জানবার প্রচেষ্টা প্রাতিষ্ঠানিক কিংবা ব্যক্তি পর্যায়ে হোক তার জন্য সাধুবাদ ও সম্মান রইলো।
নদীমাতৃক মেঠো মাটির সুরে গ্রাম-বাংলার নারী জীবনের অন্তর্নিহিত দুঃখ অনুভবের জায়গাটাতে আব্বাস উদ্দিন যে পল্লিগীতি রেখে গেছেন তা এদেশের লোক সংস্কৃতির অন্যতম উপজীব্য হিসেবে এখনও সমানভাবে সমাদৃত ও বিবেচিত। সুফিবাদের হাত ধরে আসা চট্টগ্রাম অঞ্চলে ধর্মীয় সংস্কৃতিতেও অনেকখানি জায়গা করে নিয়েছে কাওয়ালি। বিশেষ ধরনের গজল ঘরানার বাংলা গান আমাদের লোকজ শিল্পে সহঅবস্থান করে নিয়েছে খুব সহজেই। আধুনিক রবীন্দ্র, নজরুল তাদের সংগীতে স্বর, সুর, লয়, গীতি ইত্যাদির ব্যবহারে একটি একাডেমিক চর্চা রয়েছে যেখানে রাগ রাগিণীর ব্যবহার হয়েছে অত্যন্ত সতর্কভাবে ও পাণ্ডিত্বের সাথে। কেউ কেউ আমরা এমন করেই জানি যে ধ্রুপদি সংগীত লোকজর মার্গীয় নন্দনতত্ত্ব হতে উৎসারিত।
নদীমাতৃক ও কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির চর্চা থেকে শিল্পভিত্তিক অর্থনীতির চর্চাতে যখন আমরা অভ্যস্ত হতে শুরু করলাম আর বিদেশি সাহায্য সংস্থার দান দক্ষিণায় চলার প্রয়োজন অনুভূত হতে শুরু করল ঠিক তখন থেকেই চিন্তাভাবনার জগতে কিছু পরিবর্তন আসতে শুরু করল, এক পর্যায়ে ফোকপ্রিয় মানুষগুলো আধুনিক যন্ত্রপাতির সাথে অভ্যস্ত হতে গিয়ে লোকজ গানে আসতে থাকে পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তন। ফলে মূলধারা কর্ষিত হতে হতে খানিকটা নতুন লোকজ ধারার দিকে চলতে শুরু করল। মুজিব পরদেশি, বারি সিদ্দিকী এরকম কিছু গুণী মানুষের হাত ধরে লোকজ গানগুলো মডার্ন ফোকের দিকে ধাবিত হলো অবশ্য এর অন্যতম কারণ তাঁরা শহরে বসে এসব চর্চা করতো আর আধুনিক ইনস্ট্রুমেন্ট ব্যবহার করার প্রবণতা তাদেরকে মডার্ন ফোকের দিকে ধাবিত করেছে বলেই আমার মনে হয়েছে। যদিও সুর চর্চার গৎবাধা কোনো সীমানা নেই। আর বর্তমান বাংলাদেশের আমরা যাঁরা গাচ্ছি তার প্রায় সবটাই মডার্ন ফোক যা বেসিক ফোক চরিত্রের মাঝেও খানিকটা নতুনত্ব বা নতুন আরেকটি অধ্যায় হিসেবে স্বীকৃত। দেশজ লোকজ সংগীত কত উঁচুমানের হতে পারে তার উদাহরণ আমাদের জাতীয় সংগীত যা সারা বিশ্ববাসীকে ইতিমধ্যেই দেখিয়ে দিয়েছে। রাষ্ট্রীয় প্রটোকলে প্রধানমন্ত্রীর সফর কিংবা আন্তর্জাতিক খেলার আসরে যখন কোনো বিদেশি মিউজিশিয়ানরা এটা বাজিয়ে থাকে দর্শক ও যন্ত্রশিল্পীদের অভিব্যক্তি থেকে এটা সহজে অনুমেয়।
দেশপ্রেম ঈমানের অঙ্গ আমরা কমবেশি সবাই জানি। দেশের মঙ্গল ও কল্যাণমুখী ভাবনাগুলোকে লালন করা, পালন করা আর বিপরীতমুখী অকল্যাণকামী বিষয় ও বিশ্বাস থেকে যতদূর সম্ভব দূরে থাকাই ঈমানদারের কাজ। কিন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য, এক শ্রেণির মানুষ আছে যারা তার দেশের জাতীয় সংগীতকে পর্যন্ত যথাযথ সম্মান না দেখিয়ে বরং অসম্মানিত করার নানাবিধ কার্যক্রমে লিপ্ত থাকে, বিপরীতে আবার নিজেদেরকেই শক্তিশালী ঈমানদার ব্যক্তি হিসেবে সমাজের ওপর চেপে বসে এমনকি ধীরে ধীরে এরূপ বিষয়ের সাথেই মানুষ অভ্যস্ত হতে থাকে নিরুপায় হয়ে। এ দেশের খেয়েপরে নির্মল আলো-বাতাস-পানি থেকে শুরু করে সকল সুবিধা ভোগ করেও যদি কেউ দেশের প্রচলিত শিল্প-সংস্কৃতির বিরোধিতা করে তবে তাদের ঈমান কতটা শক্তিশালী তা সহজেই অনুমেয়!
এ রকম অসুন্দর বড়ই ভয়ানক! এ রকম অসুন্দরের চর্চা সাধারণ মানুষকে দ্বান্দ্বিক পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দিয়ে তাদের আবেগকে হরণ করে নেয় আর যা ইচ্ছে তাই চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে থাকে অনেকেই। মনে রাখতে হবে নিজ স্বার্থে বুঝে করলে সেটি অবশ্য অবশ্যই চরম অন্যায় করছে আর যারা না বুঝে করছে সেটিও অগ্রহণযোগ্য। প্রকৃত লোকজ গানগুলো শহুরে গীতিকার-সুরকার এবং শিল্পীদের হাত ধরে মডার্ন ফোক আত্মপ্রকাশ করেছে ইতোমধ্যেই। এভাবে চলতে থাকলে আগামী বিশ-পঁচিশ বছর সময় অতিক্রম করতেই আমরা লোকজ শিল্পের মূলধারা, চলন-বলন ভাষাশৈলী এগুলো হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থেকে কোনোভাবেই মুক্ত নই বরং পঞ্চাশ বছর অতিক্রম করতেই শত শত কোটি টাকা খরচ করে এগুলো পুনরুদ্ধারের জন্য দেশ-জাতিকে গবেষণা করতে হবে তাও আবার সেই শহুরে গবেষকদের হাত ধরেই যাঁদের কারও মধ্যেই হয়তো বিলের মধ্যে ডুব দিয়ে শালুক তোলার বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকবে না। আমি মনে করি বাংলার লোকজ সংস্কৃতির যে অসীম শক্তিমত্তা আছে তা ধরে রাখা এবং বিকশিত করা কিংবা ভবিষ্যৎ সংরক্ষণের জন্য এখনই জরুরি হয়ে পড়েছে গ্রামে গ্রামে একটি শিল্পকলার শাখা সরকারিভাবেই তৈরি হওয়া।
৬৮ হাজার গ্রামে যেমন কিছু কিছু মানুষের কর্মসংস্থান হবে পাশাপাশি সাংস্কৃতিক শিক্ষায় শিশু-কিশোরদের মেধা বিকাশ, মনন তৈরিতে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। সমাজের অসংগতি, কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা, মাদক, সন্ত্রাস, জঙ্গি কার্যক্রমকে রুখতে এবং সুন্দরের চর্চা করতে সাংস্কৃতিক শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। তাই গ্রামে গ্রামে শিক্ষা ব্যবস্থায় যেমন স্কুল-কলেজ- মাদ্রাসা-মক্তব ভূমিকা পালন করছে সাথে সাথে সাংস্কৃতিক শিক্ষার জন্য প্রয়োজন শিল্পকলার শাখা যা গ্রামীণ শিশু-কিশোরদের শিক্ষা, মনন তৈরি ও চেতনা বিকাশে সরাসরি ভূমিকা রাখবে। সেই সাথে লোকজ শিল্পের চর্চা, সংরক্ষণ যেমন নিশ্চিত করবে তেমনি হাজার বছরের ঐতিহ্য বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা পাবে। গ্রামবাসী বিনোদন উপভোগ করতে পারবে যা প্রতিটি মানুষের অন্তর চাহিদার সাথে গ্রথিত।
লেখক: পুলিশ সুপার ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব
 ঢাকা টাইমস অনলাইন এর সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিডটি ফলো করুন
ঢাকা টাইমস অনলাইন এর সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিডটি ফলো করুন
মন্তব্য করুন