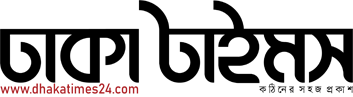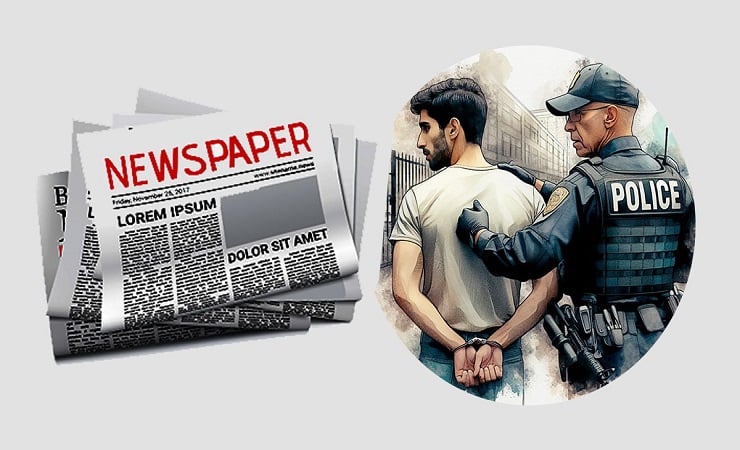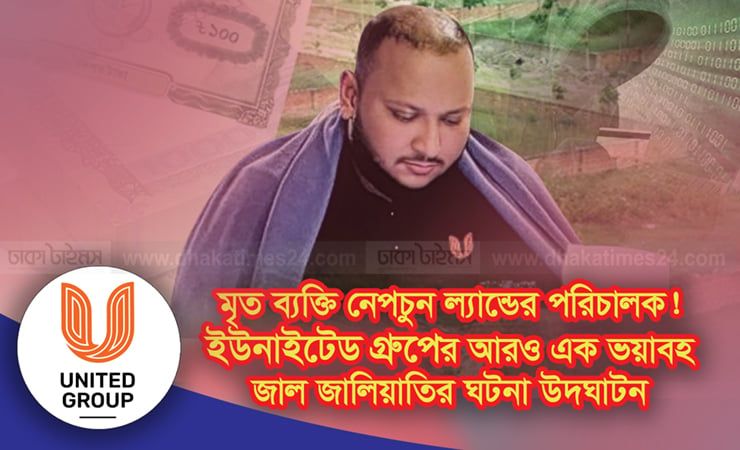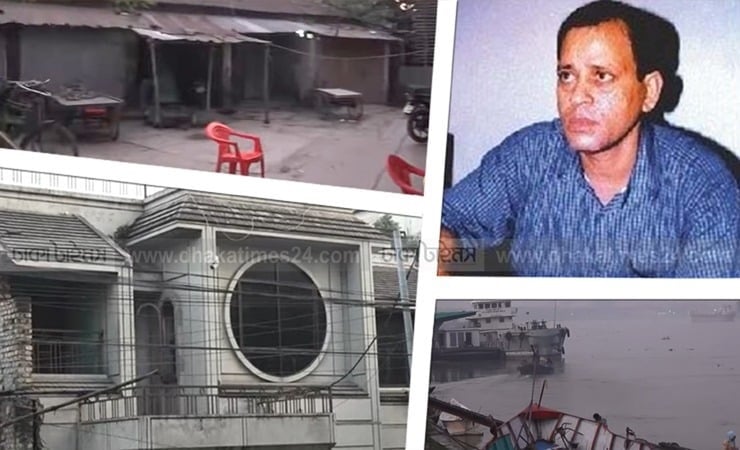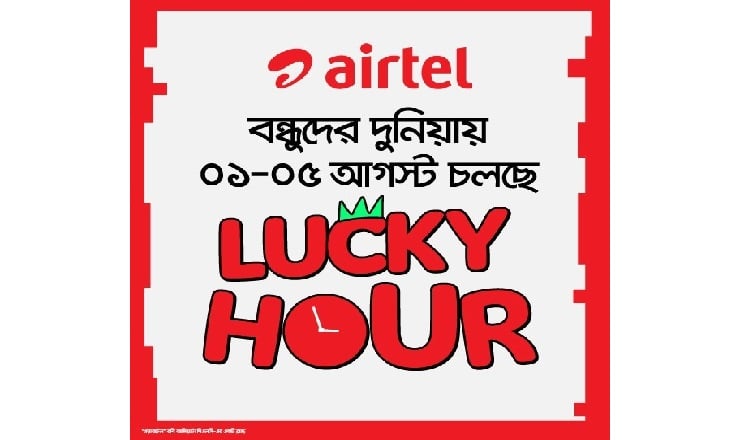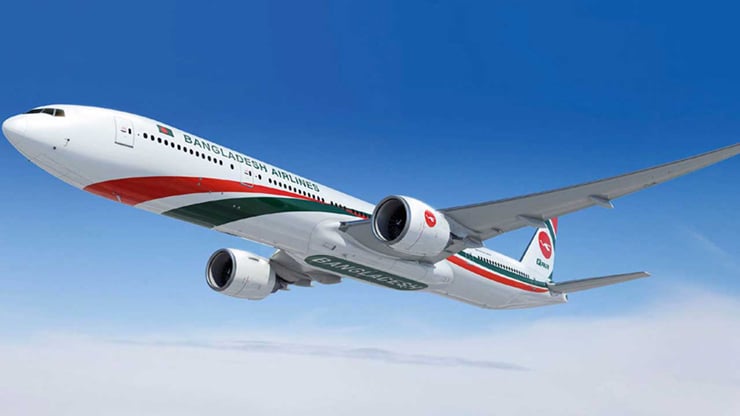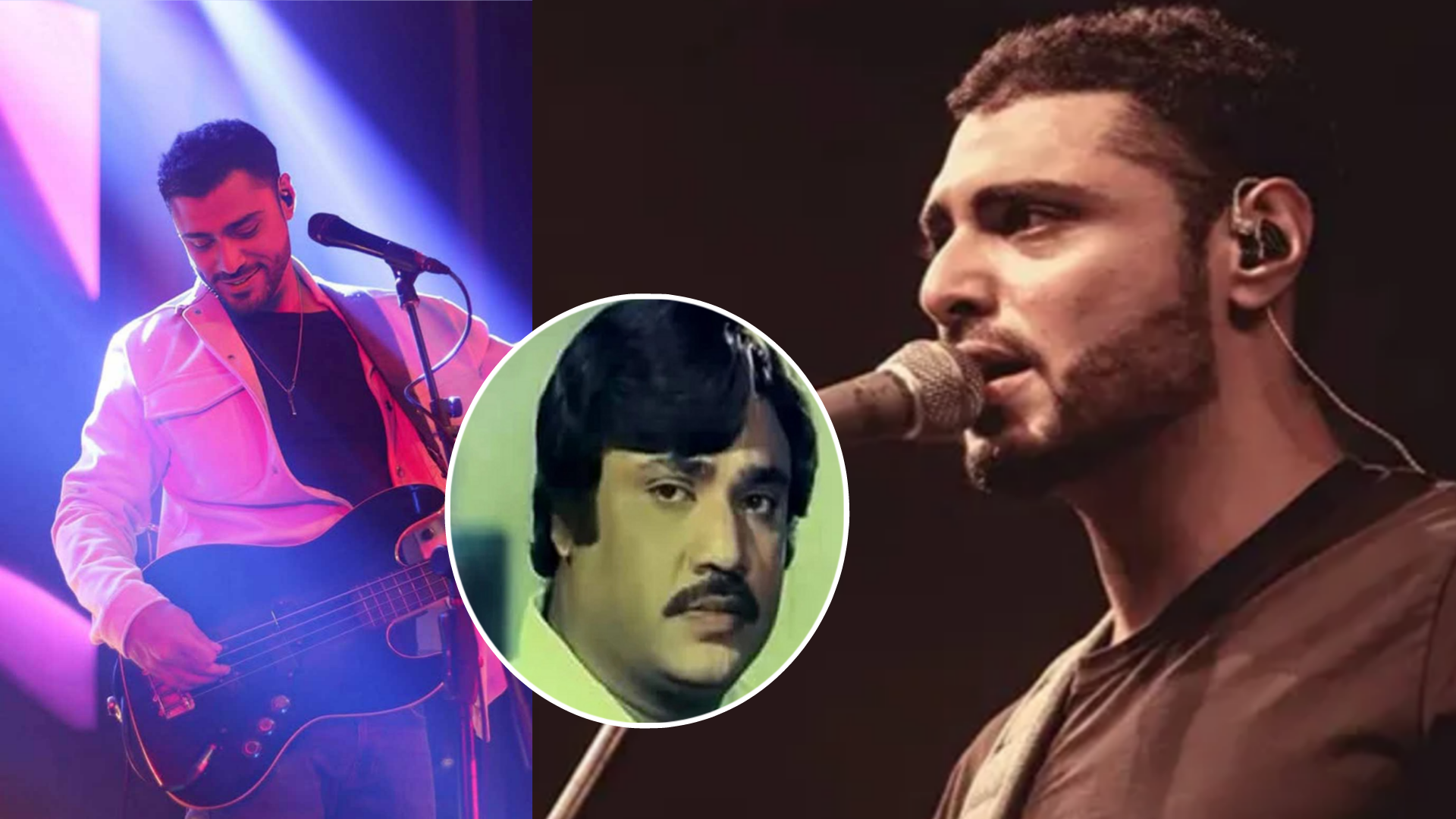অন্য সেই পুরুষের কবি
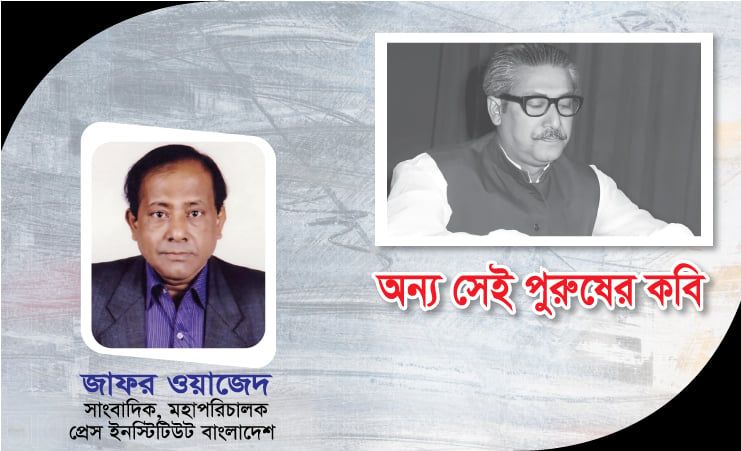
শিল্পী-সাহিত্যিক-কবি-সাংবাদিক-সংস্কৃতিকর্মীর প্রতি বঙ্গবন্ধুর ছিল অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, স্নেহ, ঘনিষ্ঠতা এবং গভীর আন্তরিকতা। কলকাতার ইসলামিয়া কলেজে অধ্যয়নকালে বেকার হোস্টেলের পাশের রুমেই ছিলেন চল্লিশ দশকের কবি গোলাম কুদ্দুস, যিনি কমিউনিস্ট রাজনীতিতে সম্পৃক্ত ছিলেন। কলেজজীবনে রবীন্দ্রনাথে আচ্ছন্ন বঙ্গবন্ধু তার সুবাদেই ত্রিশের দশকের কবিতার সাথে পরিচয় ঘটেছিল। আর পল্লিকবি জসীমউদ্দীন ছিলেন ঘনিষ্ঠ বন্ধুস্থানীয়। কবি অন্নদাশঙ্কর রায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, মনোজ বসু, বনফুল, প্রবোধ সান্যাল, কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর বেশ ঘনিষ্ঠ সম্পর্কই ছিল। স্বাধীন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর আমন্ত্রণে তারা সফরও করেছেন। জীবনের একটা বড় অংশ কেটেছে বঙ্গবন্ধুর কারাগারে। প্রায় সময় কেটেছে পড়াশোনা করে। পুরো রবীন্দ্র রচনাবলী থেকে বিশ্বসাহিত্য পাঠ সে সময়ে হয়েছিল। আর স্বাভাবিক কারণেই স্বাধীনতা-পরবর্তী পূর্ববঙ্গের কবিতা ও সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়ও ঘটেছিল কারাগারেই। এদের অনেকেরই সঙ্গে ছিল ব্যক্তিগত পরিচয় ও যোগসূত্র। কবি সুফিয়া কামাল তো ছিলেন অনেক নিকটজন। কবি শামসুর রাহমানের কবিতাও এড়িয়ে যাওয়ার কথা নয়। তার কবিতা তখন গণ-অভ্যুত্থানের রণহুংকারের সঙ্গে ধ্বনিত হচ্ছিল। স্বাধিকারকামী মানুষের ভাষা হয়ে গেল তার কবিতা। পোস্টার, ব্যানারে তার কবিতার চরণ স্ফুলিঙ্গের মতো জ্বলছিল। একাত্তরের প্রথম প্রহরে লিখেছিলেন স্বাধীনতা নিয়ে অসাধারণ দুটি কবিতা। স্বাধীনতা-পরবর্তী স্বদেশে কবিতানুরাগী বঙ্গবন্ধুর তা অজানা থাকার কথা নয়। এবং তা ছিলও না। তাই বঙ্গবন্ধু ডেকেছিলেন দেশের শীর্ষ কবি স্বাধীনতার কবি শামসুর রাহমানকে। কবিকে স্বচক্ষে দেখার, কথা বলার, কবিতা শোনার ইচ্ছেও ছিল বঙ্গবন্ধুর। কিন্তু কবির যাওয়া হয়নি। যেমন যাওয়া হয়নি বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের মিছিলে, উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের সমাবেশে, সাতই মার্চের ইতিহাসখ্যাত জনসমুদ্রেও। লাজুক, বিনম্র, বাক্সংযমী, রাজনীতিমুক্ত থাকা কবির বঙ্গবন্ধুকে কবিতা শোনানো দূরে থাক, মুখোমুখি হওয়া হয়নি। এমনকি মওলানা ভাসানীর সঙ্গেও ঘটেনি সাক্ষাৎ। কেবল বাল্যকালে পিতার সঙ্গে শেরেবাংলার বাড়ি গিয়েছিলেন। বাঙালি নেতা একজনকেই কাছে থেকে দেখেছেন। আর সবই দূর থেকে। কিন্তু কবিতায় সবাই এসেছেন শামসুর রাহমানের কলম ছুঁয়ে। বঙ্গবন্ধু চেয়েছিলেন ট্রাস্ট নিয়ন্ত্রিত দৈনিক বাংলার সম্পাদক হিসেবে কবিকে দায়িত্ব নেওয়ার জন্য। প্রস্তাব পেয়ে লজ্জিত যেন কবি। রাজি হননি গুরুদায়িত্ব গ্রহণে। যদি কাব্যচর্চা ক্ষতিগ্রস্ত হয়Ñ সেই আশঙ্কা তখনো বদ্ধমূল। কবি বরং বলেছেন, যিনি দায়িত্বে আছেন, তিনি অনেক ভালোভাবে পরিচালনা করছেন। বঙ্গবন্ধু পরিবারের সঙ্গে কবির পরিবারের আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকলেও কবি কখনো বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে যাননি। কবির অনুজ ছিলেন বঙ্গবন্ধুর ভগ্নিপতি ও তৎকালীন মন্ত্রী প্রয়াত আবদুর রব সেরনিয়াবাতের জামাতা এবং প্রয়াত যুবনেতা শেখ ফজলুল হক মনির ভায়রা ভাই। আত্মীয়তার সূত্রে প্রয়াত সেরনিয়াবাতের মিন্টো রোডের বাসভবনে নৈশভোজে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন কবি শামসুর রাহমান। বঙ্গবন্ধুও ছিলেন উপস্থিত। কিন্তু অফিসে কাজের চাপে যাওয়া হয়নি। বঙ্গবন্ধু অবশ্য সেই নৈশভোজে জেনেছিলেন কবির সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধন। বঙ্গবন্ধু গৃহকর্তাকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘কী সেরনিয়াবাত, কবিকে দাওয়াত করোনি?’ সেরনিয়াবাত বললেন, ‘‘তাকে দাওয়াত দেয়া হয়েছিল, কিন্তু কাজের চাপের দরুন তিনি আসতে পারবেন না জানিয়েছেন। সেদিন সেই মুহূর্তেই বঙ্গবন্ধু জানতে পারেন যে, আমি ওই দৈনিক বাংলার একজন সহকারী সম্পাদক।” (আত্মজীবনী: শামসুর রাহমান)। কবিকে এরপরই বঙ্গবন্ধু প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব পালনের জন্য। কবি বলেছিলেন, বঙ্গবন্ধু বিদেশ থেকে ফিরে এলে তিনি তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে কবির আর কোনো দিনই দেখা হয়নি। দূর থেকে কয়েকবার দেখেছেন। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে কোনো দিনই মুখোমুখি হয়ে বসার কিংবা কথা বলার সুযোগ হয়নি কবির। এজন্য কখনো সখনো আমার মনে খেদ জেগে ওঠে। কোনো প্রাপ্তির জন্য অবশ্যই নয়। ও রকম বড়মাপের ব্যক্তি আমাদের রাজনৈতিক ইতিহাসে অত্যন্ত বিরল। তাঁর শাহাদাত আমাদের কাঁদাবে যুগের পর যুগ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অন্ধভক্ত ছিলাম না আমি, তবে তাঁকে একজন অসামান্য গণনেতা, অসীম সাহসী, হৃদয়বান পুরুষ বলে শ্রদ্ধা করেছি।’’
স্বাধীনতা ও স্বাধিকারবিষয়ক কবিতা রচনার সুবাদে সেই উনসত্তর সাল থেকে স্বাধীনতা-উত্তর সময়ে শামসুর রাহমানকে বলা যায়, আমাদের সমকালে স্বাধীনতার কবি হিসেবে বাংলার ঘরে ঘরে সর্বাধিক পরিচিত; যেন পারিবারিক নামে পরিণত হন। দেশের প্রকাশ্য স্থানে তার কবিতা উৎকীর্ণ প্রতিফলকও স্থাপিত হয়েছে তত দিনে। শামসুর রাহমানের ব্যক্তিগত জীবন ছিল সহজ-সরল। সাদামাটা জীবনে ছিলেন অভ্যস্ত। পার্থিব জাঁকজমক আর আড়ম্বর এড়িয়ে থাকতেন। অন্তর্মুখী, লাজুক, স্বল্পভাষী প্রকৃতির মানুষ। আড্ডায় ছিলেন নীরব শ্রোতা। এমনকি রাজনীতি নিস্পৃহও। অথচ এই তিনিই পুরোপুরি নগর প্রভাবিত, মার্জিত, কোমল, সংস্কৃতিবান, বিনয়ী এবং পরিশীলিত ছিলেন। কিন্তু রাজনীতিবিমুখ বলে নিজেকে মনে করতেন। অথচ তার রচনা রাজনৈতিক আলোড়নকে ধারণ করেছে সময়ে সময়ে। “আমি যৌবনের প্রাথমিক পর্যায় থেকেই নিজেকে রাজনীতির আঁচ থেকে দূরে রাখতে চেষ্টা করেছি। রাজনীতি আমার কাছে আকর্ষণীয় মনে হতো না। এক ধরনের ঔদাসীন্য আমাকে রাজনীতি থেকে আড়াল করে রাখতো।” অন্যত্র আবার শামসুর রাহমান বলেছেন, “আমি আমার যৌবনে, স্বীকার করছি, রাজনীতিবিমুখ ছিলাম। এটা কোনো গৌরবের কথা হিসেবে জাহির করছি না।... রাজনীতি গোড়ার দিকে আমাকে তেমন প্রভাবান্বিত করেনি। কোনো বিশেষ দলের তাঁবেদারি করার প্রবণতাও আমার প্রকৃতিতে অনুপস্থিত।” ব্যক্তি শামসুর রাহমান স্পষ্টত রাজনীতির লোক নন। কোনো রাজনৈতিক দলের প্রতিই তার আনুগত্য ছিল না। লেখালেখির শুরুর দিক থেকেই যাতে তার কাব্যক্ষেত্রে রাজনীতির অনুপ্রবেশ না ঘটে, সে জন্য কড়া পাহারা বসিয়ে রেখেছিলেন চতুর্দিকে। বুদ্ধদেব বসুর অনুরাগী শামসুর রাহমান বুদ্ধদেবের মতোই মনে করতেন রাজনীতি কর্কশ ও জটিল। অথচ এই শামসুর রাহমানকে পরবর্তী সময়ে দেশ, জাতি, সমাজের কবি কণ্ঠস্বর হতে হয়েছে। দেশ ও সমাজ ভাবনার সূত্রে রাজনীতিও তাকে গভীরভাবে স্পর্শ করে। অনিবার্য দায়বোধ ষাট থেকে সত্তর দশকে ধাবমান সময়ে গণমানুষের রাজনৈতিক ভাবনার সঙ্গে নিজেকে জড়িয়েছেন। তার কণ্ঠস্বরে এসেছে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের সুর।
শামসুর রাহমানকে প্রথম মিছিলে দেখা যায় একাত্তরের মার্চে অসহযোগ আন্দোলনের সময়। বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে শিল্পী-সাহিত্যিকরা রাজপথে নেমে এসেছিলেন। শহীদ মিনারে ব্যানার হাতে কামরুল হাসান ও শামসুর রাহমান দাঁড়িয়েছিলেন। লেখা ছিল যাতে ‘কান্ডারী বল ডুবেছে মানুষ সন্তান মোর মার।’ কিন্তু এই শামসুর রাহমানকে দেখা যায় একাত্তরের সাতই মার্চের বিকেলে আশেক লেনের অদূরে একটি চায়ের দোকানে এককাপ চা ও একটি বিস্কুট কিনে রেডিওর সামনে বসে থাকা বেশ কৌতূহল নিয়ে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শোনার আকাক্সক্ষায়। যদিও সেদিন বেতারে তা প্রচারিত হয়নি। কৈফিয়ত কবির ‘‘রমনার ময়দানে যাইনি মানুষের ভিড়ের ভয়ে। মানুষের মিছিল দেখতে এবং মিছিলে অংশ নিতে ভালো লাগে আমার, কিন্তু ভিড়-ভীতি আজ অবধি রয়ে গেছে।” সেদিনের ভাষণ পরদিন বেতারে প্রচারিত হয়েছিল। ময়দানে না যাবার কারণেও হয়তো সেদিনের উত্তাপ ধারণ করেননি। তাই সাতই মার্চ নিয়ে শামসুর রাহমানের কোনো কবিতা মেলে না। অসুস্থতার কারণে ভাষা আন্দোলনে যোগ দিতে পারেননি। হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত ‘একুশে ফেব্রুয়ারি’ সংকলনে সম্পাদকের আগ্রহে যে কবিতাটি শামসুর রাহমানের ছাপা হয়, তা ভাষা আন্দোলনভিত্তিক ছিল না। ভাষা আন্দোলন মূর্ত রূপ পায় ১৯৬৯ সালে ‘বর্ণমালা আমার, দুঃখিনী বর্ণমালা’ কবিতায়।
শামসুর রাহমানের জীবন ও সাহিত্যে বঙ্গবন্ধু দুটি পর্বে বিভক্ত। পঁচাত্তর পূর্বাপর প্রেক্ষাপটে শামসুর রাহমানের সৃষ্টিতে বঙ্গবন্ধুকে খুঁজে পেতে গেলে দেখা যায়, কবি শামসুর রাহমান বঙ্গবন্ধুর বিষয়ে আলোড়িত হয়েছেন তীব্রভাবে পঁচাত্তর-পরবর্তী সময়ে। যদিও বঙ্গবন্ধুর প্রতি অবিচল শ্রদ্ধা ছিল বিদ্যমান। বঙ্গবন্ধু যখন সংগ্রামী ছাত্রনেতা ছিলেন তখন থেকেই তিনি তার ভক্ত বলে উল্লেখ করেছেন কবি। কিন্তু অন্যত্র সরল ভাষণ রেখেছেন, “একটি সত্য কথা উচ্চারণ করতে চাই; গোড়ার দিকে আমার তেমন আকর্ষণ ছিল না শেখ মুজিবের প্রতি। ক্রমান্বয়ে দীর্ঘ লয়ে বেড়েছে আকর্ষণ।” স্বাধীনতা-পূর্ব সময়ে বা স্বাধীনতাযুদ্ধকালে সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনা শামসুর রাহমানের কবিতায় উঠে এলেও বঙ্গবন্ধুর অবস্থানকে এড়িয়ে যেতে চেয়েছেন। এটা হতে পারে পাক সরকার নিয়ন্ত্রিত পত্রিকায় চাকরি করার কারণে, ‘‘একাত্তরের সাতই মার্চে তাঁর (বঙ্গবন্ধুর) নক্ষত্রের আলোর মতো আগুন ঝরানো, বিপ্লবী কোনো প্রথম শ্রেণির কবিতার মতো তার ভাষণ শুনে, ‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম’ এই উচ্চারণ শুনে আমি নিজে ঝংকৃত হয়ে উঠলাম অগ্নিবীণার মতো। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সেদিন সাত কোটি বাঙালি আমারই মতো অগ্নিবীণা হয়ে উঠেছিল। সেদিন থেকে তার প্রতি দুর্মর আকর্ষণ, শ্রদ্ধা বোধ করতে শুরু করি।’’ (শেখ মুজিবকে শ্রদ্ধা করি বলেই)।
শেখ মুজিব যখন ‘বঙ্গবন্ধু’ উপাধি পাননি, তখনই ১৯৬৭ সালে তাঁকে নিয়ে একটি কবিতা লিখেন গ্রিক পৌরাণিক কাহিনির আড়ালে। কবিতাটির নাম ‘টেলেমেকাস’। রূপক কবিতা। বঙ্গবন্ধু তখন কারাবন্দি। গ্রিক পুরাণের ওডিসিয়াস বাধ্যতই দেশছাড়া, বিপন্ন স্বদেশ ইথাকা বিদেশি বর্বরদের দখলে, পুত্র টেলেমেকাস পিতার প্রত্যাবর্তনের জন্য অপেক্ষমাণ। কারণ সে জানে, পিতা ফিরলেই আবার উজ্জীবন ঘটবে। টেলেমেকাসের চোখে শুধু স্বপ্ন-বাঁচার স্বপ্ন। পিতার প্রতীক্ষায় সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে রয়েছে ব্যাকুল দৃষ্টিতে, ‘তুমি নেই বলে বর্বরের দল করেছে দখল/বাসগৃহ আমাদের। কেউ পদাঘাত করে, কেউ/নিমেষে হটিয়ে দেয় কনুই-এর গুঁতোয় আবার/... থমথমে আকাশের মতো/সমস্ত ইথাকা, গরগরে জনগণ প্রতিষ্ঠিত/অনাচার, অজাচার ইত্যাদির চায় প্রতিকার।’ (নিরালোকে দিব্যরথ, ১৯৬৮)। কবিতাটি যে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লেখা, সে সময় তা কারো কাছে সেভাবে প্রতিভাত হয়নি। শুধুই পৌরাণিক বলে মূল্যায়িত হয়েছিল। বলেছেন শামসুর রাহমান, ‘সেকালে কবিতাটির আড়ালে যে আমাদের দেশের হাল হকিকত এবং জননেতা শেখ মুজিবের কথাই বলা হয়েছে, এই সত্য অনেকের কাছেই সম্ভবত উদ্ভাবিত হয়নি।’ হবার কথাও নয়। কারণ শামসুর রাহমান তখন সরকার নিয়ন্ত্রিত পত্রিকার সাংবাদিক। তার কবিতাকে প্রতিবাদী হিসেবে দেখা হতো যদিও।
স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে শামসুর রাহমানের কবিতায় স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধ মেলে। বঙ্গবন্ধুর প্রসঙ্গ ছাড়াই। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান, সংগ্রামী রাজনীতির যে আকার তৈরি করেছিল, তাতে যোগ দিল ধনী-গরিব নির্বিশেষে বৃহৎ বাঙালি সমাজ। সামরিক শাসনের দুঃসময়ে আন্দোলন যখন এভাবেই পাকিয়ে উঠেছিল, তখন দেশের ওই রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কবির কবিতারও পরিবর্তন হতে থাকে। ‘আইয়ুব খানের সামরিক শাসনামলে আমার কাব্যপ্রয়াস একটা নতুন বাঁক নেয় বলে আমি মনে করি। যে আমি ছিলাম পুরোপুরি বিবরবাসী অন্তর্জীবনে সমর্পিত, সে আমি ক্রমান্বয়ে হয়ে উঠলাম বহির্জীবনের প্রতি মনোযোগী এবং রাজনীতিমনস্ক। কোনো বিশেষ রাজনৈতিক দলের অনুগত না হয়েই আমি রাজনীতি থেকে, গণসংগ্রাম থেকে শোষণ করে নিলাম আমার কবিতার নানা উপাদান।’
পঁচাত্তর-পূর্ব দীর্ঘ সময়ে শামসুর রাহমান দেশের ঘটনাবলিতে আলোড়িত হলেও, ঐতিহাসিক অনেক মুহূর্ত তার কলমের স্পর্শ পায়নি। তবে পঁচাত্তরের পনেরো আগস্টের হত্যাকাণ্ড অসংখ্য বাঙালির মতো শামসুর রাহমানকেও শোকার্ত করেছিল। তার অনুজ ব্যারিস্টার তোফায়েলুর রাহমানের স্ত্রী মঞ্জু পিতা সেরনিয়াবাত-মাতা-ভাই-বোন-স্বজন হারিয়ে শোকাচ্ছন্ন ছিলেন শামসুর রাহমানদের বাড়িতে। কবি তাকে কাঁদতে বারণ করেছিলেন। কান্নার শব্দে যাতে পাড়ার লোক চলে না আসে এবং সবার নিরাপত্তার কথা ভেবেছিলেন তিনি। সেই পরিস্থিতিতে কবি নিজেও বেদনার্ত এবং অসহায় বোধ করেছিলেন। ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর পরিবারবর্গের করুণ মৃত্যু অনেকের মতো আমাকে অত্যন্ত শোকার্ত, বিচলিত এবং ক্রুদ্ধ করে তুলেছিল। নিজের অসহায়তার দরুন শামসুর রাহমান নামক ব্যক্তিটির প্রতি কেন জানি অসন্তুষ্ট হয়ে পড়েছিলাম।’ শামসুর রাহমান সেদিন দৈনিক বাংলায় যাননি। কর্মক্ষেত্রে পরদিন অফিস সহকর্মীদের সঙ্গে পরিস্থিতি পর্যালোচনাকালে কবি বলেছিলেন দৃপ্তকণ্ঠে, ‘শেখ মুজিব উইল সুন রাইজ ফ্রম হিজ গ্রেইভ।’ হত্যাকাণ্ডে আলোড়িত কবি, পনেরো আগস্টের কয়েক দিন পর লিখলেন কবিতা ‘বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে’। যা তার একটি গ্রন্থেরও শিরোনাম। কবিতার বিভিন্ন পঙ্ক্তির আড়ালে বঙ্গবন্ধুর হত্যা ও ঘাতকদের পরিচয় তুলে ধরেন। ১৯৭৫ সালের আগস্ট সংখ্যায় ‘সমকাল’ সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক সিকান্দার আবু জাফর প্রথম কবিতা হিসেবে ছেপেছিলেন। ‘কবিতাটিতে যে শেখ মুজিব এবং তাঁর ঘাতকদের প্রতীকধর্মী বর্ণনা ছিল কোনো কোনো অংশে, এ কথা ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ের মুজিববিরোধী কতিপয় ছাত্র টের পেয়েছিল এবং কোনো কোনো অছাত্র পান্ডা তাদের বুঝিয়ে দিয়েছিল। তারা ‘সমকাল’-এর সেই সংখ্যার কিছু কপি পায়ে থ্যাঁতলে, আগুনে পুড়িয়ে নিজেদের উষ্মা প্রকাশ করে।’ (আত্মজীবনী)।
পঁচাত্তর-পরবর্তী সময়ে শামসুর রাহমান রাজনৈতিক ভূমিকাও পালন করেছেন কোনো কোনো ক্ষেত্রে। আওয়ামী লীগের প্রতি তার পক্ষপাত ক্রমশ প্রকাশ্য হতে থাকে ইতিহাসের বাস্তবতার নিরিখে। ‘এ- ওতো বাংলাই এক, তোমার ধ্যানের বাংলাদেশ/ হোক বা না হোক; আজও এখানে এ-বাটে দৈনন্দিন/ চলে আনাগোনা নানা পথিকের, মাঠে বীজ বোনে/ ধান কাটে কর্মিষ্ঠ কৃষক আর মাঝি টানে দাঁড়, /...সবই তো বেসুরো বাজে আজকাল; অথবা তোমার/গানের অজস্র জলে যেমন যোজন যোজন রুক্ষ ভূমি/ হয়ে যায় নিমেষেই গোলাপ বাগান আর রুগ্ন/মজা নদী ফিরে ফিরে পায় তরঙ্গিত তুমুল যৌবন। (এ-ওতো বাংলাই এক, এক ধরনের অহংকার, ১৯৭৫)।
শামসুর রাহমান যখন এ কবিতা লেখেন তখন তিনি দৈনিক বাংলায় কর্মরত। সংবাদপত্রে জান্তাদের দৌরাত্ম্য থাকলেও কবির কাব্যভুবনে তারা প্রবেশ করতে পারেননি। ফলে কবি লিখেছিলেন ‘বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে’। ‘বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে একটি ব্রোঞ্জের মূর্তি, নিথর বিশাল,/ মাটি ফুঁড়ে জেগে ওঠে গম্ভীর রাত্তিরে।/’ কিংবা আরো গভীরে গিয়ে লিখেন, ‘এবং মাছের পেট থেকে নারী আর শিশু আসে ভেসে ভেসে,/ মেহেদি পাতার ভিড় থেকে; বেলুনের ঝাঁক থেকে/ নারী আর শিশু ভেসে আসে।/’ পঁচাত্তরের পনেরো আগস্ট কালোরাতের ঘটনা এই কাব্যে বিধৃত হয়েছে। মূলত বঙ্গবন্ধু হত্যা-পরবর্তী বাংলাদেশের চিত্র উঠে আসে কবিতায়, ‘বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে একজন অসুস্থ নৃপতি শয্যাশায়ী।/ একটি সোনালি খাটে অলৌকিক ফলের আশায়/ প্রহর ফুরায়, তাহলে কি দীপ নিভে যাবে গহন বেলায়?/ কোন তেপান্তরে আজ হাঁপাচ্ছে বিশীর্ণ পক্ষিরাজ,/ ভাবেন নৃপতি, চোখ বুজে আসে, তৃতীয় কুমার তার এখনো ফেরেনি।/’ ১৯৭৭ সালে প্রকাশিত হয় কবিতাটি। যখন বঙ্গবন্ধুর নাম উচ্চারণ করতে দেওয়া হতো না, তখন কবির এই কবিতা সাহসের সঞ্চয় অবশ্যই। শামসুর রাহমান চলমান জীবন থেকে নিজস্ব কাব্যের রসদ নিয়েছেন। পূর্ব পাকিস্তান ও বাংলাদেশের ইতিহাসের এক একটা স্তর পার হয়েছে, আর কবি তার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে আছেন। বঙ্গবন্ধুকে সপরিবার হত্যা, তারপর ক্রমাগত সামরিক বা আধাসামরিক শাসন স্বাধীনতার মূল্যবোধকে বিনষ্ট করে দেশকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। শামসুর রাহমান স্বদেশের এই পশ্চাৎযাত্রা ও বিপর্যয় প্রত্যক্ষ করেছেন। তার কবিতায় যে অনিবার্য পুনরাবৃত্তি তার পেছনে স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশের ইতিহাস ও কিছুটা অনড় বাস্তবও দায়ী। বঙ্গবন্ধু হত্যা দেশের একজন সচেতন মানুষ হিসেবে তার বিবেককে নাড়া দিয়েছে। শামসুর রাহমান উপলব্ধি করেন তার দেশ লাঞ্ছিত হচ্ছে বারবার। জান্তার শাসনে পর্যুদস্ত স্বদেশ। তবু এই শামসুর রাহমানই মুক্তির মন্ত্র তুলে ধরেছেন বারবার।
১৯৬৯ সালের ৫ ডিসেম্বর যখন বঙ্গবন্ধু তাঁর বজ্রকণ্ঠে পূর্ব পাকিস্তানের নাম রাখলেন ‘বাংলাদেশ’, কবি শামসুর রাহমানের মনে হয়েছিল, ‘এই নামটির জন্য তৃষ্ণার্ত চাতকের মতোই উদগ্রীব ছিল কোটি কোটি বাঙালি। তাদের প্রাণপ্রিয় নেতা শেখ মুজিব সেই তৃষ্ণা মেটালেন। সবুজ মাঠ, জল-ছল ছল নদীর দেশ আমাদের এই বাংলা। যখন মাইল-মাইল জোড়া মাটিতে ধান গাছের ঢেউ খেলে যায়, যখন সবুজ গাছ-গাছালির শাখা থেকে আকাশের দিকে উড়ে যায় নানা রঙের পাখ-পাখালি। যখন নদীর বুকে গর্বিত পাল উড়িয়ে নৌকাগুলো এগিয়ে যায় গন্তব্যের দিকে, যখন দূর থেকে ভেসে আসে বাউলের একতারার সুর, তখন প্রকৃত বাঙালির মনে প্রাণে সৃষ্টি হয় এক অপরূপ জগতের রূপ। তখন দেশের নানা স্মৃতি উড়ে উড়ে এসে বসে আমাদের মানস ডালে। তখন সুখ স্বপ্ন আমাদের কঠোর বাস্তবের ধুলোবালির ভয় দেখানো ঢিবি থেকে অনেক দূরে মখমল-কোমল পথে নিয়ে যায় অন্য এক জগতে।”
শামসুর রাহমান পাকিস্তান পর্বে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে যে আন্দোলন-সংগ্রাম হয়েছে, আশির দশকের শেষে এসে তার মূল্যায়ন শুরু করেন। ১৯৮৬ সালে শামসুর রাহমান লিখেন বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে তাঁর উল্লেখযোগ্য কবিতা ‘ধন্য সেই পুরুষ।’ আওয়ামী লীগের পনেরো আগস্টের প্রকাশনার জন্য দলীয় সভাপতি জননেত্রী শেখ হাসিনা কবির কাছে কবিতা চেয়েছিলেন। সেই চাওয়ার বিপরীতে শামসুর রাহমান লিখলেন “ধন্য সেই পুরুষ, যাঁর নামের ওপর রৌদ্র ঝরে/ চিরকাল, গান হয়ে/ নেমে আসে শ্রাবণের বৃষ্টিধারা, যাঁর নামের ওপর/ কখনো ধুলো জমতে দেয় না হাওয়া,/ ধন্য সেই পুরুষ, যাঁর নামের ওপর পাখা মেলে দেয়/ জ্যোৎস্নার সারস,/ ধন্য সেই পুরুষ যাঁর নামের ওপর পতাকার মতো/ দুলতে থাকে স্বাধীনতা,/ ধন্য সেই পুরুষ যাঁর নামের ওপর ঝরে/ মুক্তিযোদ্ধাদের জয়ধ্বনি।’ শামসুর রাহমান উপলব্ধি করেছেন যে, ইতিহাসের অনিবার্য সত্যকে চাপা দিয়ে রাখা যায় না। সত্যকে মুছে ফেলা যায় না। বলেছেনও তিনি, সত্যের নিজস্ব একটা শক্তি আছে, যার স্রোতের টানে মিথ্যার বর্জ্য ভেসে যায় একদিন না একদিন। কখনো সেই দিনটি আসে শিগগিরই, কখনো দেরিতে। মূঢ় মানুষ যেটি বুঝতে পারে না। বঙ্গবন্ধুর নাম বাংলাদেশ থেকে মুছে ফেলা, ইতিহাস বিকৃতির বিরুদ্ধে শামসুর রাহমানের কলমে অবিরল গদ্য ঝরেছে। তিনি বিশ্বাস করতেন, কবরে বঙ্গবন্ধুর মৃতদেহ বিনষ্ট হয়েছে সত্য, কিন্তু তিনি জেগে উঠেছেন প্রবলভাবে লক্ষ-কোটি বাঙালির মনে। তাঁর শত্রুপক্ষ বড় বেশি ভীত তাঁর নামের জ্বলজ্বলে প্রভাবে। বলেছেন কবি, ‘যতদিন বাংলাদেশ থাকবে ততদিন এদেশের নির্ভীক, অনন্য দেশপ্রেমিক, বীর সন্তান শেখ মুজিবুর রহমান সগৌরবে জীবিত থাকবেন কোটি কোটি বাঙালির মনে। চন্দ্র, সূর্যকে বিস্মৃত হওয়া যেমন অসম্ভব, তেমনি অসম্ভব বঙ্গবন্ধুকে ভুলে যাওয়া।’
১৯৮৬ সালের পর শামসুর রাহমান সংবাদপত্রে নিবন্ধ ও কলামে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে তাঁর মূল্যায়ন ও পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেছেন। আত্মজীবনী ‘কালের ধুলোয় লেখা’তে তিনি বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, বঙ্গবন্ধু হত্যা প্রসঙ্গ ও দেশের পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়ে লিখেছেন। বলেছেন, “শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য দেশপ্রেমিক নেতা আমাদের উদ্বুদ্ধ করেছেন, নিজ নিজ প্রক্রিয়ায় ঠিক পথটি দেখিয়েছেন। আমরা কি তাদের অবদানের কথা ভুলতে পারি? আমাদের স্মৃতি থেকে কি মুছে ফেলতে পারি তাঁদের অসামান্য সংগ্রাম, ত্যাগ এবং জাতি গঠনের অক্লান্ত সাধনার কথা? যদি অবহেলা করি আমাদের মহান নেতাদের, তাহলে আমরা চিহ্নিত হবো অকৃতজ্ঞ জনগোষ্ঠী হিসেবে।’ শামসুর রাহমান মূল্যায়ন করেছেন, ‘এটা তো শেখ মুজিবের শত্রুরাও স্বীকার করবেন যে, তাঁর জীবনের অনেকগুলো বছর কারাগারে কেটেছে মতাদর্শের জন্যে। নেলসন ম্যান্ডেলার মতো অত দীর্ঘকাল না হলেও সেই সময়ের কাছাকাছি হবে। তিনি বহু ত্যাগ স্বীকার করেছেন, নিজের জীবনকে বিপন্ন করেছেন, স্বদেশ এবং স্বদেশবাসীর মুক্তি এবং কল্যাণের গুরুত্বকে নিজের প্রাণের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতেন বলেই।’
১৯৯২ সালে শামসুর রাহমান লিখলেন বঙ্গবন্ধু এবং পনেরো আগস্ট হত্যাকাণ্ডকে সামনে রেখে কবিতা ‘তোমারই পদধ্বনি’। কলকাতার আনন্দবাজার প্রকাশনা থেকে ১৯৯৩ সালে প্রকাশিত ‘হরিণের হাড়’ গ্রন্থভুক্ত। ‘এই লেখা উঠে এসেছে সেই সিঁড়ি থেকে,/ যেখানে পড়েছিল ঘাতকের গুলিবিদ্ধ তোমার লাশ,/ এই লেখা উঠে এসেছে তোমার বুক জোড়া রক্তাক্ত গোলাপ থেকে/ বুলেটে ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া নব পরিণীতার/ মেহেদি-রাঙা হাত এবং শিশুর নেকড়ে খোবলানো শরীর থেকে।/ তোমার দিকে ওরা ছুঁড়ে দিয়েছিলো মৃত্যু;/ কিন্তু ওরা জানতো না’/ কোনো কোনো মৃত্যু জীবনের চেয়েও সতেজ, মহিমান্বিত,/ তোমার মৃত্যুর কাছে কোটি কোটি জীবন আজো নতজানু,/ তোমার গুলিবিদ্ধ শরীর এখনো/ রাজপথ উপচে পড়া মিছিলের সামনে।’ ইতিহাসের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার ও হত্যাকারীদের শাস্তি চেয়েছিলেন কবি শামসুর রাহমান মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত। ‘আওয়ামী লীগের প্রতি আমার দুর্বলতা শেখ মুজিবের জন্যে। তাঁর প্রতি অটল শ্রদ্ধা রেখেই বলছি তাঁর কোনো কোনো কাজ আমার কাছে সমর্থনযোগ্য মনে হয়নি। মনে মনে ঝগড়া করেছি ওই মহান নেতার সঙ্গে। আমি ভালো করেই জানি, তাঁর জন্যেই, তাঁর মতোই কারিশমাদীপ্ত আমাদের ছিলেন বলেই বাংলাদেশের জন্ম হয়েছে এক রক্ত সমুদ্রে বিশাল লাল পদ্মের মতো।’ শামসুর রাহমান বঙ্গবন্ধু যে সংবিধান রেখে গেছেন, তা আদিরূপ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নিবন্ধও লিখেছিলেন। চেয়েছিলেন ধর্মনিরপেক্ষতার পুনর্বহাল। শামসুর রাহমান বাংলাদেশ এবং ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি বঙ্গবন্ধুর যে আন্তরিক টান ছিল, তা উপলব্ধি করেছেন সেই অতীতেই। ‘পূর্ব পাকিস্তান নামটি শেখ মুজিবুর রহমান পছন্দ করতেন না বলেই মহান জননেতা ১৯৬৯ সালের ৫ ডিসেম্বর “বাংলাদেশ” নামকরণের উদ্যোগ নেন। আমি বলতে লুব্ধ হচ্ছি, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি একটি সহজাত ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ ছিল শেখ মুজিবের। তিনি ১৯৭১ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি বাংলা একাডেমির একুশের কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দৃঢ়কণ্ঠে বলেছিলেন, “আমাদের হাতে যেদিন ক্ষমতা আসবে সেদিন থেকেই দেশের সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু হবে। বাংলা ভাষার পণ্ডিতেরা পরিভাষা তৈরি করবেন তারপরে বাংলা ভাষা চালু হবে, সে হবে না।” এখানে উল্লেখ করা দরকার, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি গভীর অনুরাগ ছিল বলেই তিনি এই ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথের “গীতবিতান” থেকে আমাদের জাতীয় সংগীত নির্বাচন করেছিলেন।’
সরকারি খেতাব বা মৃত্যুর পর রাষ্ট্রীয় মর্যাদা না পাওয়া কবির বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা না হওয়া, বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনকালে ক্যাম্পাসে হাজির থাকতে না পারার আক্ষেপ ছিল। পঁচাত্তর-পরবর্তী সময়ে কবি শামসুর রাহমান বিভিন্ন রচনায় বঙ্গবন্ধুর যে মূল্যায়ন করেছেন, তা অনেক ক্ষেত্রে সরলীকরণ প্রতীয়মান হয়। দূরত্ব দূরে থাকা, বঙ্গবন্ধু বিরোধীদের অপপ্রচারে প্রতিষ্ঠিত অসত্য তথ্য কবিকেও ভারাক্রান্ত করেছে বৈকি। দেশবরেণ্য কবি, আমাদের কালের বাংলা ভাষার প্রধান কবি শামসুর রাহমান বাঙালির ইতিহাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে জেগে আছেন। শুধু অনুতাপ, জাতির জনকের সঙ্গে তাঁর দেশের ও ভাষার প্রধান কবির কখনো দেখা-সাক্ষাৎ, কবিতা শোনা হলো না, আত্মীয়তার বন্ধন থাকা সত্ত্বেও। ‘তোমাকে ওরা অবজ্ঞায়, অপমানে; অবহেলায়/ ঠেলে দিয়েছিল এই বাংলার অজপাড়া গাঁয়ে/ এক কবরে, অথচ আজ ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইল জুড়ে/ তোমারই পদধ্বনি, আলো-জাগানো ভাস্বর পদধ্বনি।’ জয়তু বঙ্গবন্ধু। জয়তু শামসুর রাহমান।
লেখক: একুশে পদকপ্রাপ্ত সাংবাদিক, মহাপরিচালক,
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
 ঢাকা টাইমস অনলাইন এর সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিডটি ফলো করুন
ঢাকা টাইমস অনলাইন এর সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিডটি ফলো করুন
মন্তব্য করুন