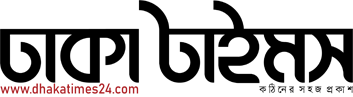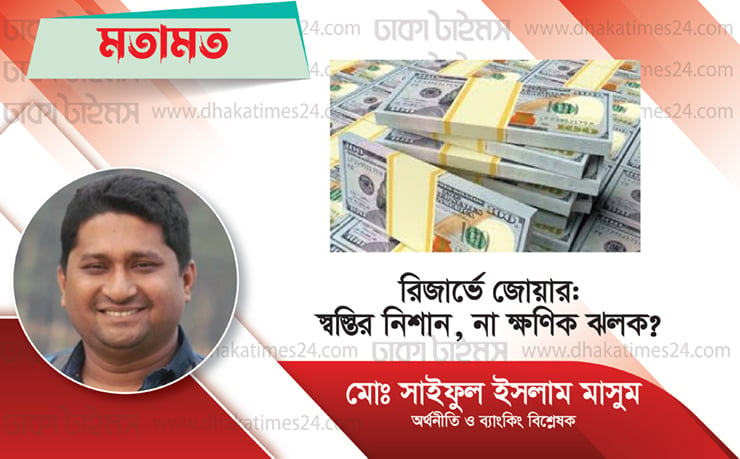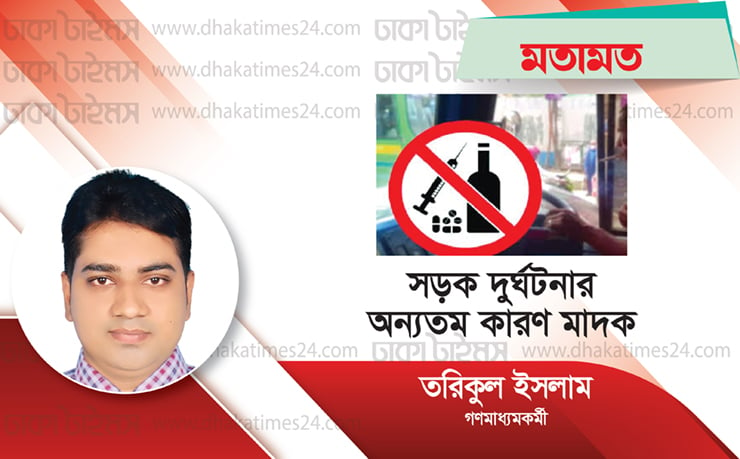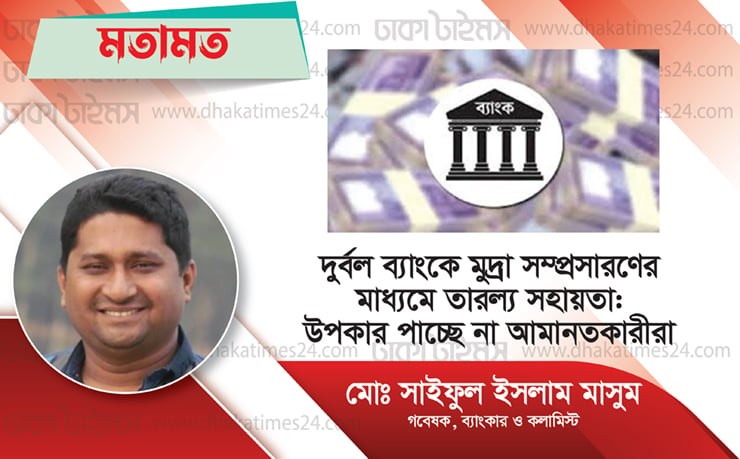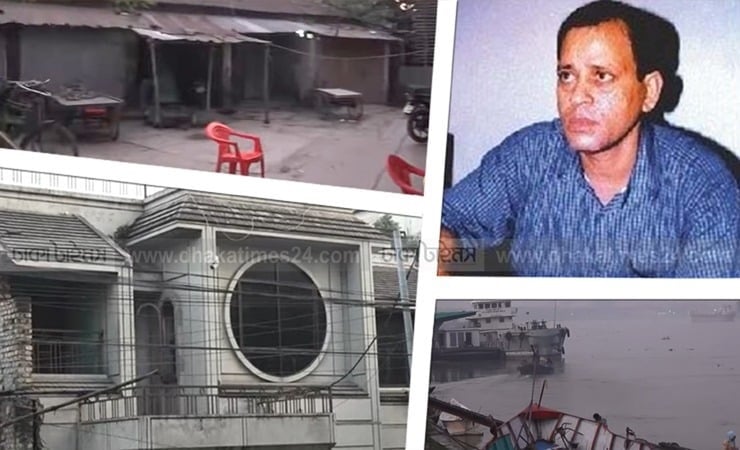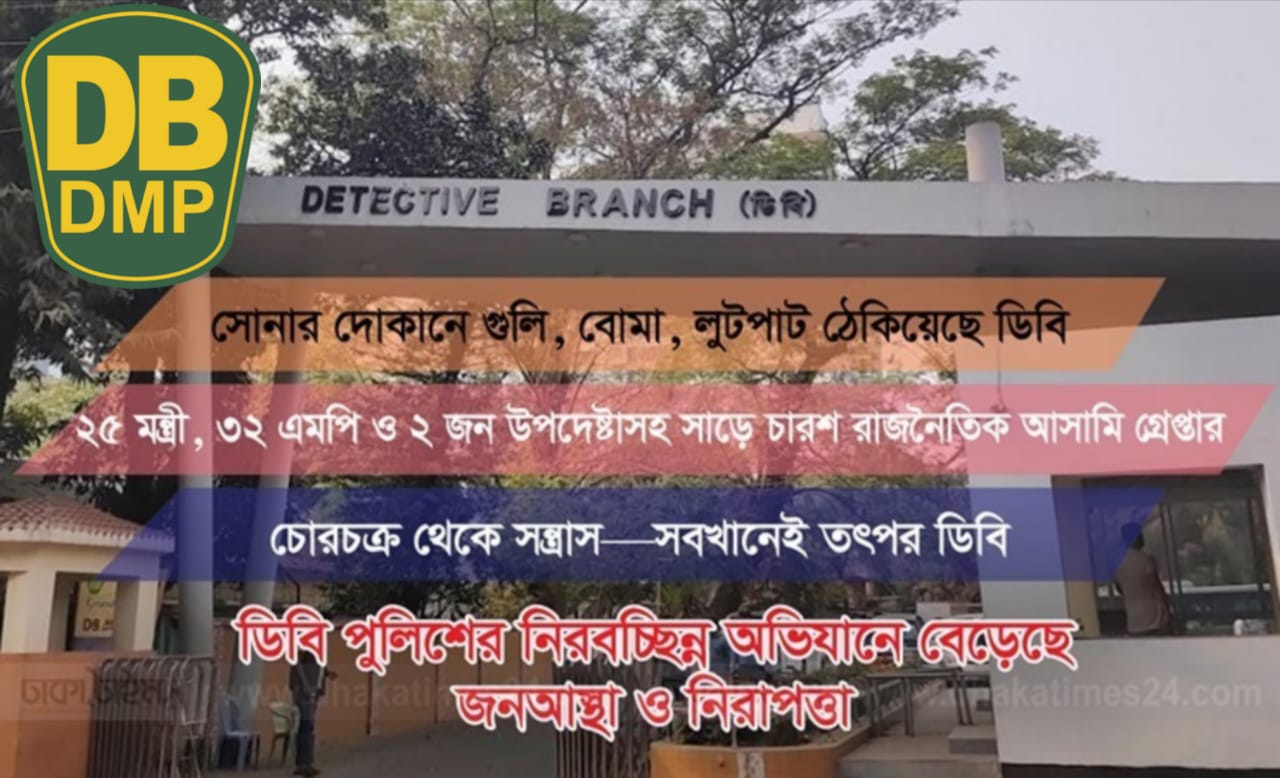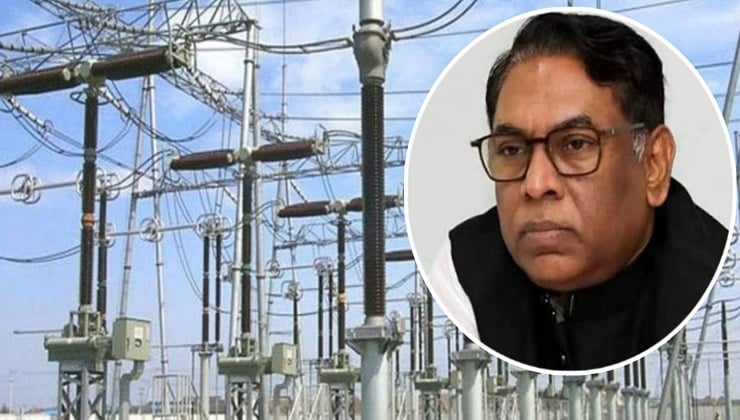মুক্তিযুদ্ধ: কিছু ভাবনা কিছু পর্যালোচনা
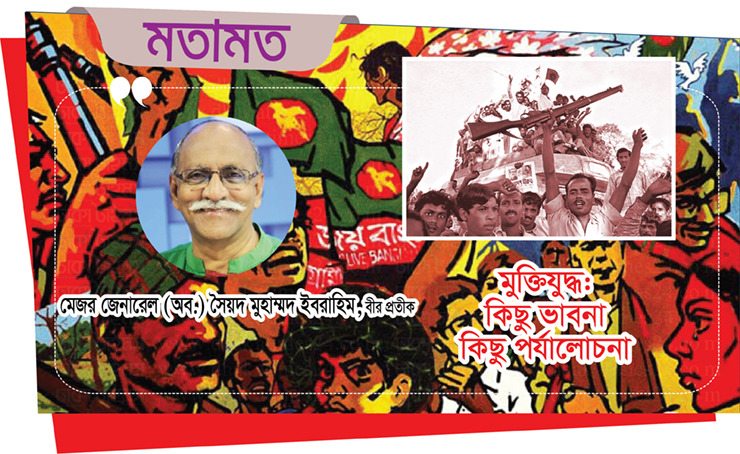
১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের নয়টি মাস কীরূপ ব্যস্ততার ও একাগ্রতার মধ্য দিয়ে কেটেছিল, সেটা একটি কলামের কয়েকটি লাইনের মাধ্যমে প্রকাশ করা মুশকিল। এর থেকেও বড় মুশকিল হলো বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে, একটি প্রশ্নের উত্তর দেয়া। ঐ প্রশ্নটি হলো, মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে কেমন বাংলাদেশ চেয়েছিলাম এবং কেমন বাংলাদেশ এখন পাচ্ছি। তৃতীয় এবং কঠিনতম মুশকিল থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আমি খুব সহজ এবং জনপ্রিয় একটি পন্থা অবলম্বন করছি। পন্থাটি হলো, অন্য কোনো গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি কী বলেছেন সেটা প্রকাশ করা এবং তাঁর মতের সঙ্গে আমার নিজের সংহতি প্রকাশ করা।
ঢাকা মহানগর থেকে প্রকাশিত একটি বহুল প্রচারিত দৈনিক পত্রিকায় একজন প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ ও মুক্তিযোদ্ধার কলাম থেকে আমি কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করছি। কলামের লেখক মুক্তিযোদ্ধার নাম নূরে আলম সিদ্দিকী। উদ্ধৃতি শুরু: “গণতন্ত্র ও মানুষের মৌলিক অধিকারের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি এবং বাঙালি জাতীয় চেতনা তথা জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সবার জন্য রাজনৈতিক সমঅধিকার-এটাই ছিল স্বাধীনতার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। ...আজকে গভীর বেদনার সঙ্গে আমি অনুভব করি মুক্তিযোদ্ধার চেতনা বলতে নতুন প্রজন্মকে সেখানো হচ্ছে, মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে কেবল বিষোদগার। ফলে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শিক অঙ্গীকার নিকষ অন্ধকারে নিমজ্জিত হচ্ছে। সন্দেহাতীতভাবে জাতির জন্য এটি অশনি সংকেত এবং সামাজিক বিপর্যয় সৃষ্টির পূর্বাভাস। পাকিস্তান আমলের ২৩ বছরের রাজনৈতিক পথপরিক্রমা, আন্দোলন, বঙ্গবন্ধুর অমর নেতৃত্বে লাখ লাখ রাজনৈতিক কর্মীর অবিস্মরণীয় আত্মত্যাগ গৌণ হয়ে নয় মাসের যুদ্ধটিই যেন মুখ্য হয়ে উঠেছে। মুক্তিযুদ্ধ প্রসঙ্গে আমার অভিজ্ঞতা, দেশের শতকরা ৯৫ ভাগ লোক মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সঙ্গে গভীর প্রত্যয় সহকারে সম্পৃক্ত ছিল।...” উদ্ধৃতি শেষ।
আজকে এই কলাম লিখতে গিয়ে কলামের মাধ্যমে আমি নূরে আলম সিদ্দিকীর বক্তব্যের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করছি। আমরা এইরূপ বাংলাদেশ চাইনি এবং আজও চাই না। যাহোক, কলামের বক্তব্য যেন কঠোর না হয় তার জন্য আমি সচেষ্ট থাকছি। আমরা যেরূপ বাংলাদেশ চাই তার আংশিক পেয়েছি; যেই অংশটুকু বা যেই মর্মটুকু পাইনি, সেই অংশ বা মর্ম পাওয়ার জন্য বা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আমাদেরকে সংগ্রাম করতে হবে।
একাত্তরের নয়টি মাস ছিল দারুণ ব্যস্ত। বাংলাদেশের ভূখণ্ড ১১টি সেক্টরে বিভক্ত হয়েছিল; যদিও ১০ নম্বর নামে পরিচিত সেক্টরটি সক্রিয় ও সুপরিচিত হয়নি। জুলাই এবং আগস্ট মাসে তিনটি ব্রিগেড আকৃতির বাহিনী সৃষ্টি করা হয়েছিল যার নামগুলো ছিল জেড ফোর্স, এস ফোর্স, এবং কে ফোর্স। আমি যুদ্ধের প্রথম পাঁচ মাস তিন নম্বর সেক্টরের অধীনে দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের একজন অফিসার হিসেবে যুদ্ধ করেছি। পরবর্তী চার মাস আমি একই দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অফিসার হিসেবে এস ফোর্সের সাংগঠনিক কাঠামোর মধ্যে থেকেই যুদ্ধ করেছি। ১ ডিসেম্বর ১৯৭১-এ ভোর রাত সাড়ে তিনটায় আমরা রওনা দিয়েছিলাম আক্রমণস্থলের দিকে। আক্রমণের পূর্ববর্তী স্থানকে সেনাবাহিনীর পরিভাষায় ‘এসেম্বলী এরিয়া’ বলে। সেখান থেকে সাড়ে চারটায় রওনা দিই এবং উপস্থিত হই দ্বিতীয় পর্যায়ের অবস্থানে; যাকে সেনাবাহিনীর পরিভাষায় বলা হয় ‘ফরমিং আপ প্লেইস’ বা এফইউপি। আক্রমণ শুরুর নির্ধারিত ঘণ্টাকে বলা হয় ‘এইচ আওয়ার’। আজমপুর স্টেশনের উত্তরে অবস্থিত পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটি প্রতিরক্ষা অবস্থান দখল করাই ছিল আমাদের আক্রমণের লক্ষ্য। সকাল সাড়ে সাতটার মধ্যে দক্ষিণ দিকে রেললাইন ধরে দুই কিলোমিটার দূরে আখাউড়ার দিকে ধাবমান হলাম। আখাউড়ার যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটেছিল ১৯৭১ সালের ৫ ডিসেম্বরের ফজরের নামাজের পরপর। এরপর অব্যাহত অগ্রযাত্রার মাধ্যমে, দুই-তিন দিন হেঁটে হেঁটে আমরা মেঘনা নদীর পাড়ে আসি; শতাধিক নৌকায় চড়ে মেঘনা নদী পার হই। মেঘনা নদী পার হওয়ার পর পশ্চিম দিকে তথা রাজধানী ঢাকার দিকে আমাদের পদযাত্রা অব্যাহত থাকে। পাকিস্তানিরা পিছনের দিকে হটছিল তো হটছিলই। ১১ ডিসেম্বর ১৯৭১ সন্ধ্যায় আমরা বর্তমান নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলার সদরে অবস্থিত মুড়াপাড়া গ্রামে এসে উপস্থিত হই। মুড়াপাড়া গ্রাম শীতলক্ষ্যা নদীর পূর্ব তীরে অবস্থিত। ১২ ডিসেম্বর সকালে শীতলক্ষ্যা নদী পার হই। উল্লেখ্য, ৪ বা ৫ ডিসেম্বর তারিখ থেকেই আকাশসীমায় পাকিস্তানিদের কোনো যুদ্ধ বিমান দেখা যায়নি। ১২ ডিসেম্বর বিকাল থেকে আমরা শীতলক্ষ্যা পার হয়ে দু-চার মাইল হেঁটে পূবগাঁও ও পশ্চিমগাঁও নামক স্থানগুলোতে অবস্থান নিই। বর্তমানে যেটাকে আমরা ডেমরা বলি, সেখানেই বালু নদী এসে শীতলক্ষ্যা নদীতে পড়ে। ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ বিকাল সাড়ে চারটার সময় আমরা ছিলাম বালু নদীর দক্ষিণ পাড়ে। একইদিন সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় আমরা এসে পৌঁছাই ঢাকা মহানগরের তখনকার আমলের একমাত্র স্টেডিয়ামে; গুলিস্তান সিনেমা হলের নিকট। আমরা বলতে, দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট। সামরিক বাহিনীর কাঠামোগত পরিচয়ে, আমরা ছিলাম এস ফোর্স নামক ব্রিগেডের অধীন এবং এস ফোর্স ছিল ভারতীয় সেনাবাহিনীর ৫৭ মাউন্টেন ডিভিশনের সঙ্গে সংযুক্ত, যুদ্ধের জন্য। মেঘে মেঘে অনেক বেলা হয়েছে। স্বাধীনতার ৫৪ বছর পর পুনরায় মার্চ উপস্থিত।
আজ স্বাধীনতা দিবস। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে এবং জাতীয় ইতিহাসে, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও গৌরবের দিন। ৯৩ হাজার পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর সদস্য এবং আরও অতিরিক্ত কয়েক হাজার সহযোগী সদস্যকে পরাজিত করে মুক্তিযুদ্ধের বিজয় সূচিত হয়েছিল।
সাম্প্রতিক আট বছর ধরে আমি রাজনৈতিক অঙ্গনের একজন সক্রিয় কর্মী, বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টির চেয়ারম্যান। কল্যাণ পার্টির অষ্টম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে গত ৫ ডিসেম্বর শনিবার ঢাকা মহানগরের জাতীয় প্রেস ক্লাবের বড় মিলনায়তনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আলোচনার মূল প্রতিপাদ্য বা থিম ছিল: বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে গুণগত পরিবর্তন আনয়ন। পরিবর্তন কেন প্রয়োজন? পরিবর্তন প্রয়োজন এই জন্য যে, যেই লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়েছিল সেই লক্ষ্য থেকে আমরা দূরে সরে গিয়েছি। সেই লক্ষ্য অর্জন করতে হলে, দেশপ্রেমিক সৎ মেধাবী সাহসী ব্যক্তিগণকে রাজনীতিতে জড়াতে হবে। এটা যদি কাম্য হয় তাহলে ঐরূপ ব্যক্তিদের জড়িত করার নিমিত্তে সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। রাজনীতি নামক কর্মযজ্ঞকে ইতিবাচক ভাবমূর্তিতে জনগণের মানসপটে স্থাপিত করতে হবে। আমরা মনে রাখতে চাই যে, ১৯৪৮ থেকে ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের ২৫ তারিখ পর্যন্ত আজকের বাংলাদেশ তথা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মাটিতে যেই রাজনীতি হয়েছিল, সেটা ছিল গণমানুষের রাজনীতি, সেটা ছিল মাটি ও মানুষের স্বার্থ রক্ষার রাজনীতি। ঐ ২৩ বছরের রাজনীতির চূড়ান্ত পর্ব ছিল সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ। বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ কোনো অরাজনৈতিক ঘটনা নয় বরং ২৩ বছরের দীর্ঘ রাজনৈতিক সংগ্রামের চূড়ান্ত অধ্যায়। বলাই বাহুল্য যে, সেই চূড়ান্ত অধ্যায়টিও পরিচালিত হয়েছিল রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বগণের নেতৃত্বে। সেই রাজনৈতিক নেতৃত্বের শীর্ষতম নেতা ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
চট্টগ্রাম মহানগরের ষোলোশহরে অবস্থিত অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ঢাকা মহানগর থেকে ২২ মাইল দূরের জয়দেবপুর ভাওয়াল রাজাদের রাজপ্রাসাদে অবস্থিত দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, কুমিল্লা সেনানিবাসে অবস্থিত চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, সৈয়দপুর সেনানিবাসে অবস্থিত তৃতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট এবং যশোর সেনানিবাসে অবস্থিত প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশ পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেছিলেন। সকল ব্যাটালিয়ন থেকে একটি স্বতন্ত্র পরিচয় অষ্টম ইস্ট বেঙ্গলের, এই মর্মে যে অষ্টম ইস্ট বেঙ্গলের উপ-অধিনায়ক মেজর জিয়াউর রহমান ২৭ মার্চ তারিখে প্রথমে নিজের নামে এবং কয়েক ঘণ্টা পরেই বঙ্গবন্ধুর নামে, কালুরঘাট রেডিও স্টেশন থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ২৬৬ দিন দীর্ঘ মুক্তিযুদ্ধের এই প্রাথমিক অধ্যায়ের চূড়ান্ত পর্ব ছিল ৪ এপ্রিল তারিখে অনুষ্ঠিত জ্যেষ্ঠ সামরিক কর্মকর্তাদের সম্মেলন। সম্মেলন স্থান ছিল বর্তমান হবিগঞ্জ জেলার মাধবপুর থানা বা উপজেলার তেলিয়াপাড়া চা বাগানের ম্যানেজারের বাংলো। আমার অধিনায়ক তৎকালীন মেজর কে এম সফিউল্লাহর সহযোগী তথা স্টাফ অফিসার হিসেবে আমিও ব্যক্তিগতভাবে ঐ কনফারেন্সে উপস্থিত ছিলাম। ঐ কনফারেন্সের পক্ষ থেকেও প্রধানতম সিদ্ধান্ত ছিল; রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের প্রতি আহ্বান। কী আহ্বান? সামরিক বাহিনী কর্তৃক সূচিত করা বিদ্রোহ যা ক্রমান্বয়ে জনযুদ্ধে রূপ নিতে যাচ্ছে সেটার চূড়ান্ত নেতৃত্ব রাজনীতিবিদগণ কর্তৃক গ্রহণ করা। এর ফলশ্রুতিতে ১০ এপ্রিল ১৯৭১ তারিখে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার গঠনের ঘোষণা এবং ১৭ এপ্রিল তারিখে ঐ সরকারের শপথ গ্রহণ হয়। বাংলাদেশের মানুষ এবং বাঙালি সামরিক কর্মকর্তাগণ যে রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রতি অনুগত ছিলেন তার অন্যতম বহিঃপ্রকাশ হলো মার্চের শেষ সপ্তাহ থেকে শুরু করে ১৭ এপ্রিল তারিখ পর্যন্ত সময়কাল। ১৭ এপ্রিল তারিখ থেকে আনুষ্ঠানিক-রাজনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার যুদ্ধ পরিচালনার চূড়ান্ত দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কেবিনেট মন্ত্রীর পদমর্যাদায়, তৎকালীন সংসদ সদস্য অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল মোহাম্মদ আতাউল গনি ওসমানীকে মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি বা কমান্ডার ইন চিফ নিযুক্ত করা হয়। প্রতিটি সেক্টরে পর্যায়ক্রমে সেক্টর কমান্ডার নিযুক্ত করা হয়েছিল। তারপর ছিল সাব-সেক্টর কমান্ডার। মুক্তিযোদ্ধাগণের একটি অংশকে বলা হতো গেরিলা মুক্তিযোদ্ধা। সার্বিকভাবে মুক্তিযোদ্ধাগণ যুদ্ধ পরিচালনা করতে করতেই পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর শক্তিকে ক্রমান্বয়ে দুর্বল করে ফেলেছিল। অবশ্যই সার্বিক আর্থিক, প্রশিক্ষণ এবং অস্ত্র ও গোলাবারুদের জোগানদাতা ছিল ভারত। ২৬৬ দিন দীর্ঘ মুক্তিযুদ্ধের শেষের ১৩ দিন ছিল যৌথভাবে পরিচালিত যুদ্ধ। যৌথ বাহিনীর অংশীদার ছিল বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাগণ (যার আনুষ্ঠানিক নাম বাংলাদেশ ফোর্সেস বা সংক্ষেপে বিডিএফ) এবং ভারতীয় সামরিক বাহিনী। যৌথ বাহিনীর কমান্ডার ছিলেন তৎকালীন ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ড বা ইস্টার্ন কমান্ডের অধিনায়ক লেফটেনেন্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা। অরোরার সদর দপ্তরে প্রধান স্টাফ অফিসার (সামরিক পরিভাষায় চিফ অব স্টাফ ছিলেন তৎকালীন মেজর জেনারেল জেএফআর জেকব (পরবর্তীতে তিনি ভারতীয় সেনাবাহিনীতে লেফটেনেন্ট জেনারেল এবং একই পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের অধিনায়ক হয়েছিলেন। আনুষ্ঠানিকভাবে যৌথ নেতৃত্বই তথা যৌথ বাহিনীই বিজয় ছিনিয়ে আনে।
এই দিনে জীবিত মুক্তিযোদ্ধাদের অনুভূতি বারবার মনে আসছে। জাতীয় পর্যায়ের রাজনৈতিক ও সামরিক নেতৃত্বের স্মৃতি বারবার মনে আসছে। গত দু-চার বছর ধরে একটি বিপজ্জনক প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। ভারতীয় সংস্কৃতির অঙ্গনের বা বুদ্ধিবৃত্তি অঙ্গনের কেউ কেউ, ভারতীয় সিনেমা জগতের কোনো কোনো মহারথি এইরূপ বক্তব্য বা অনুভূতি প্রকাশ করছেন যে, ১৯৭১ সালে ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে যেই যুদ্ধ হয়েছিল, সেই যুদ্ধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় অথবা প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশ নামক একটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে। এসব ব্যক্তি বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাগণকে এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের শহীদদেরকে অবমূল্যায়ন করছেন, অবহেলা করছেন। এই সকল ব্যক্তি বর্তমান বাংলাদেশের সকল নাগরিকের অনুভূতিকে আঘাত করছেন। এইরূপ অনুভূতি আক্রান্ত একজন ব্যক্তি আমি নিজেও। অতএব আমি প্রতিবাদ করতে বাধ্য। আমার প্রতিবাদের প্রতিপাদ্য হচ্ছে, মানবিক কারণে, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের কারণে, ভূ-রাজনৈতিক লাভ-লোকসানের কারণে ভারত নামক রাষ্ট্র মুক্তিযুদ্ধে আমাদেরকে সহায়তা করেছিল। ভারত নামক রাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীর সদস্যগণ আমাদের স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিয়েছেন, রক্ত ক্ষয় করেছেন, তাদের অর্থনীতি থেকে আমাদেরকে সমর্থন দিয়েছেন এটা সত্য। যাবতীয় ভারতীয় সহযোগিতার জন্য, বাংলাদেশিরা কৃতজ্ঞ। কিন্তু কৃতজ্ঞতার পরিমাণ বা সীমারেখা এইরূপ নয় যে, স্বাধীনতার কৃতিত্ব ছিনতাই করতে দেয়া হবে। আজকে স্বাধীনতা দিবসে এই সত্য স্পষ্টভাবেই প্রকাশ করতে হবে।
মুক্তিযোদ্ধাদের স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করতে হলে মুক্তিযোদ্ধাদের অনুভূতিকে সম্মান করতে হবে; মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে মূল্যায়ন করতে হবে। এই সম্মান ও মূল্যায়ন করার জন্য ক্ষেত্র ও সুযোগ প্রয়োজন। যে কোনো কারণেই হোক না কেন, অথবা যে কোনো পরিস্থিতিতেই হোক না কেন, মুক্তিযুদ্ধ সেখানে হওয়ার অব্যবহিত পরেই, রণাঙ্গনের মুক্তিযোদ্ধাগণ নিজ নিজ পেশায় ফেরত যান। সৈনিকগণ সামরিক বাহিনীতে, পুলিশ সদস্যগণ পুলিশ বাহিনীতে, ছাত্ররা স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে, কৃষক-শ্রমিক ভাইয়েরা কৃষি ক্ষেত্র এবং মিল কারখানায়, চিকিৎসক ও প্রকৌশলী ইত্যাদি পেশাজীবীগণ নিজ পেশায় ফেরত যান। রাজনীতিতে লেগে থাকেন শুধুমাত্র পেশাদার রাজনীতিবিদগণ বা রাজনৈতিক মুক্তিযোদ্ধাগণ। রণাঙ্গনের মুক্তিযোদ্ধাগণ মুক্তিযুদ্ধের অনুভূতি নিজেদের স্বপ্ন ইত্যাদি বাস্তবায়নের জন্য প্রত্যক্ষ কোনো সুযোগ পাননি। স্বাধীনতার কয়েক বছর পর মাত্র, ক্রমান্বয়ে একজন-দুইজন-চারজন করে রণাঙ্গনের মুক্তিযোদ্ধা রাজনীতিতে জড়িত হন। ১৯৭২ এর অক্টোবরে জন্ম নেয়া জাসদ, বাহাত্তরের পাঁচ বছর পর জন্ম নেয়া ইউপিপি, দুটি ক্ষুদ্র উদাহরণ। আওয়ামী লীগে তৃণমূল পর্যায়ে কিছু সংখ্যক রণাঙ্গনের মুক্তিযোদ্ধা থেকে যান। বিএনপি যখন জন্ম নেয় তখন কিছু সংখ্যক রণাঙ্গনের মুক্তিযোদ্ধা বিএনপিতে জড়িত হন, দলটির প্রতিষ্ঠাতা রণাঙ্গনের মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান বীর উত্তমের আহ্বানেও নেতৃত্বে। ২০০০ সালের পরে রণাঙ্গনের মুক্তিযোদ্ধাগণ অধিকতর সংখ্যায় প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে আসেন।
আইজেন হাওয়ার নামক একজন ব্যক্তি প্রথম মহাযুদ্ধে কনিষ্ঠ অফিসার ছিলেন; দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে চার তারকা জেনারেল হন। তিনিই ১৯৫২ সালে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হন। ১৯৬৩ সালে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন যিনি, সেই জন এফ কেনেডিও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে নৌ বাহিনীর কনিষ্ঠ র্যাংকের অফিসার ছিলেন এবং যুদ্ধে আহত হয়েছিলেন। কেনেডির পরে আরও দুইজন প্রেসিডেন্ট তাদের বয়সের ছোটকালে সৈনিক ছিলেন। সৈনিকগণ রাজনীতিতে আসবেন এটাই স্বাভাবিক। তবে সামরিক জীবনে ডিসিপ্লিন এবং রাজনীতির অঙ্গনের সৌজন্যবোধ ও আচার আচরণের বিধিতে পার্থক্য আছে। সাবেক সৈনিক রণাঙ্গনের মুক্তিযোদ্ধা অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল ইবরাহিম বীর প্রতীক, তার দলের মাধ্যমে রাজনীতির অঙ্গনে গুণগত পরিবর্তন আনার চেষ্টায় সংগ্রামরত একজন রাজনৈতিক কর্মী। এই সংগ্রামে স্বাধীনতার মাসে দেশবাসীর শুভেচ্ছা কামনা করছেন। স্বাধীনতা দিবসে ঢাকা টাইমসকে এবং এই কলামের মাধ্যমে ঢাকা টাইমস-এর পাঠককে অভিনন্দন জানাচ্ছি।
মেজর জেনারেল (অব.) সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম, বীর প্রতীক: রাজনীতিবিদ; সভাপতি, বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি।
 ঢাকা টাইমস অনলাইন এর সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিডটি ফলো করুন
ঢাকা টাইমস অনলাইন এর সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিডটি ফলো করুন
মন্তব্য করুন