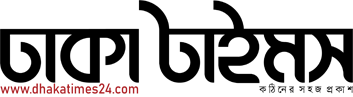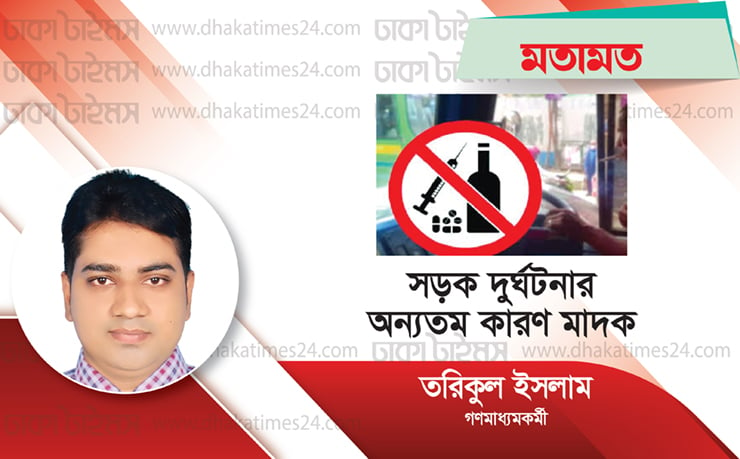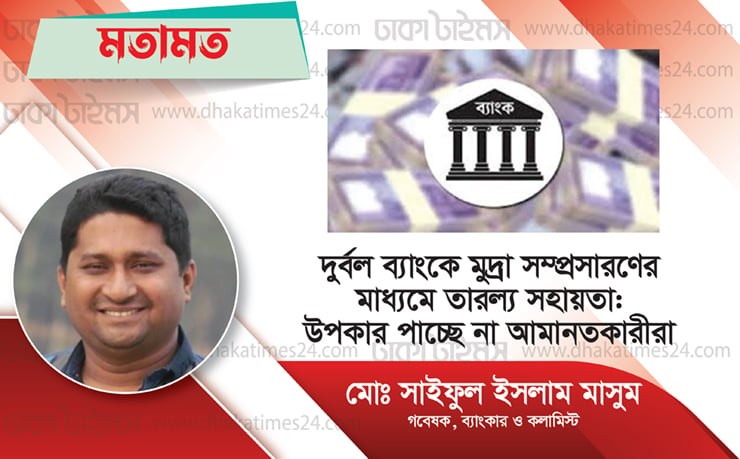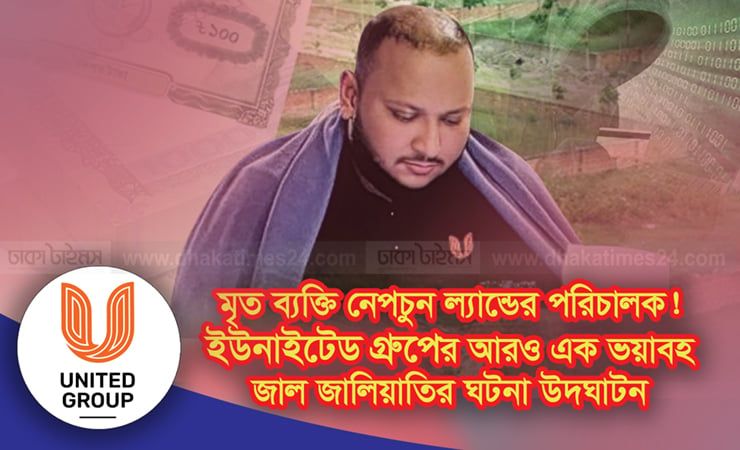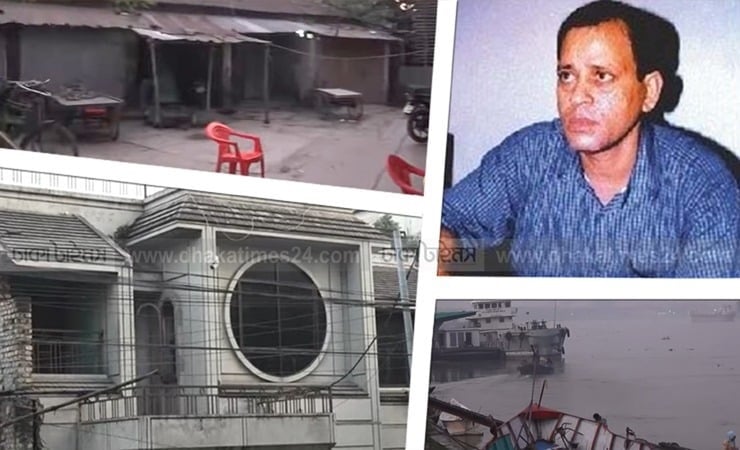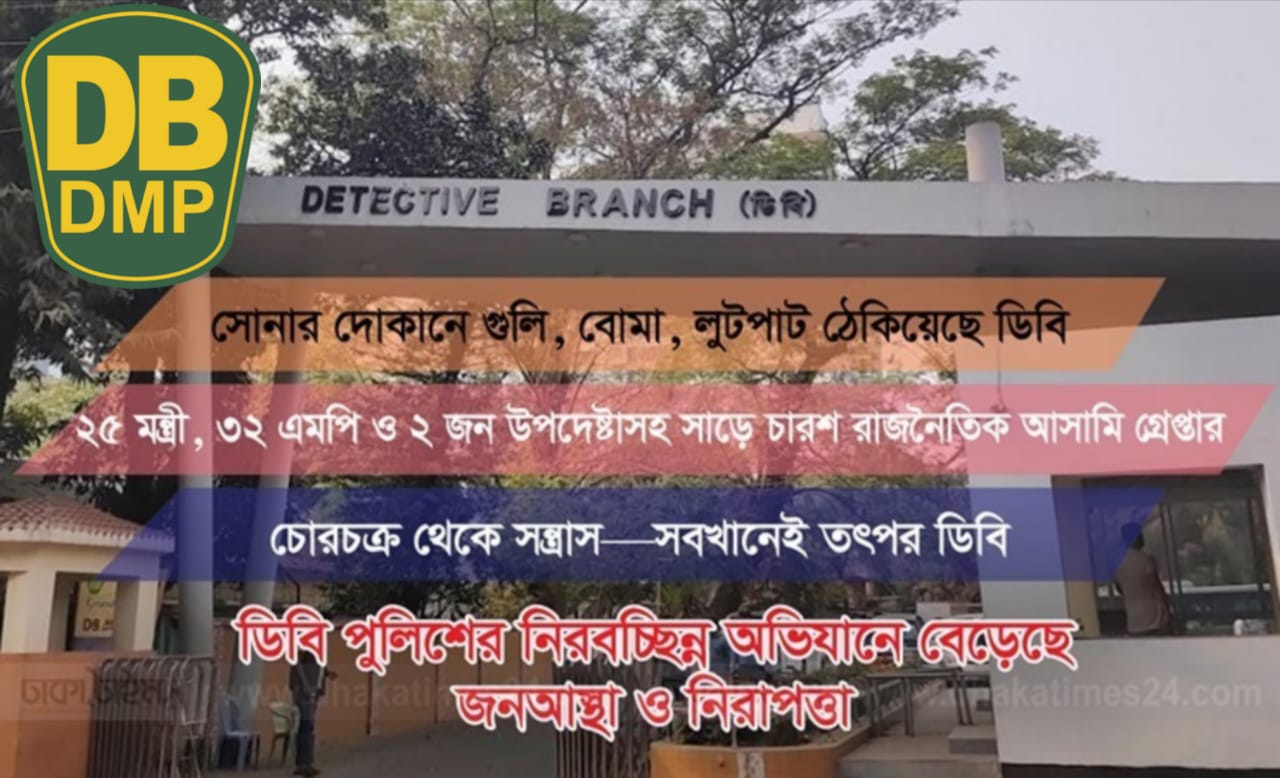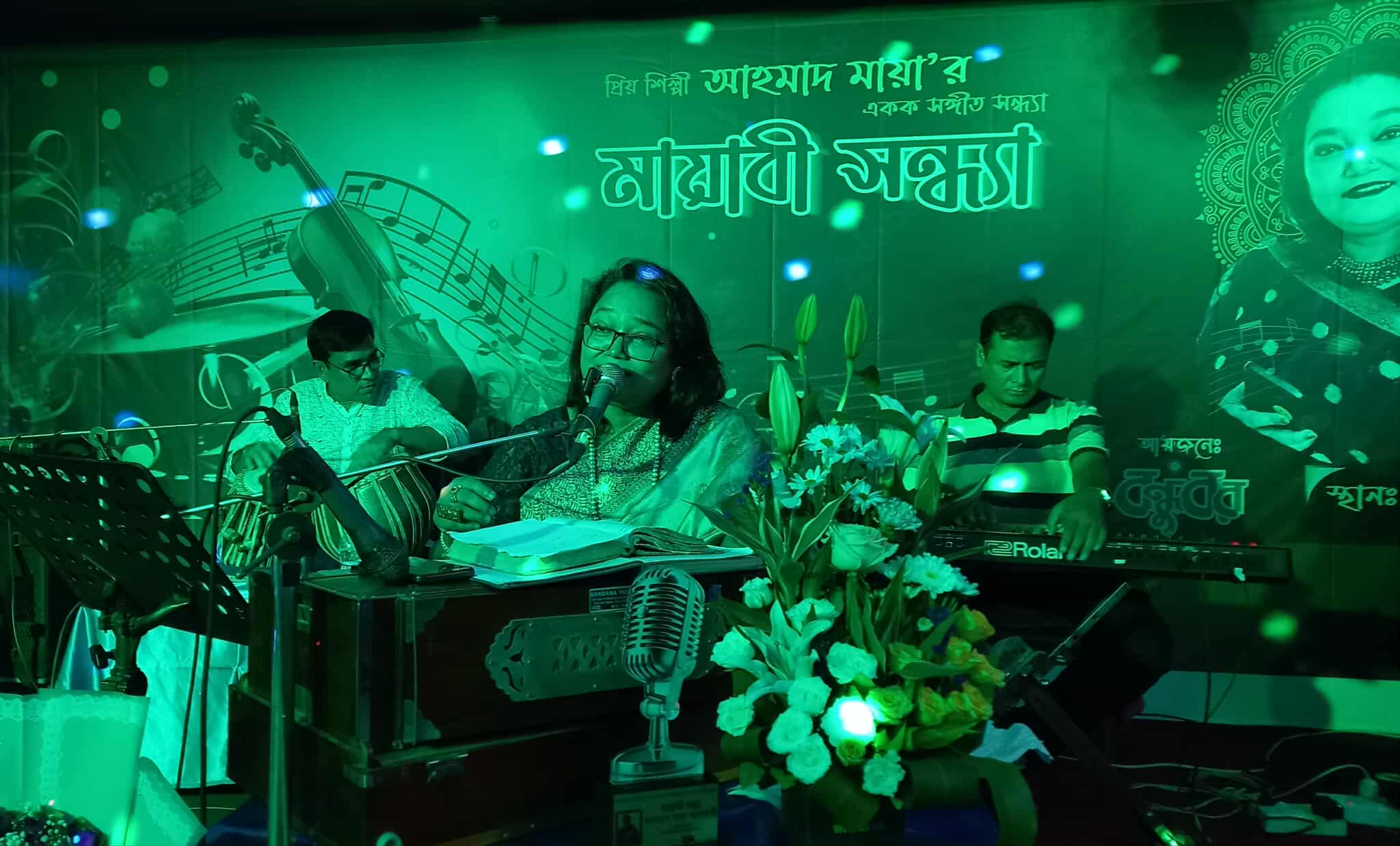ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাবিত গবেষণা জালিয়াতি প্রতিরোধের আইন
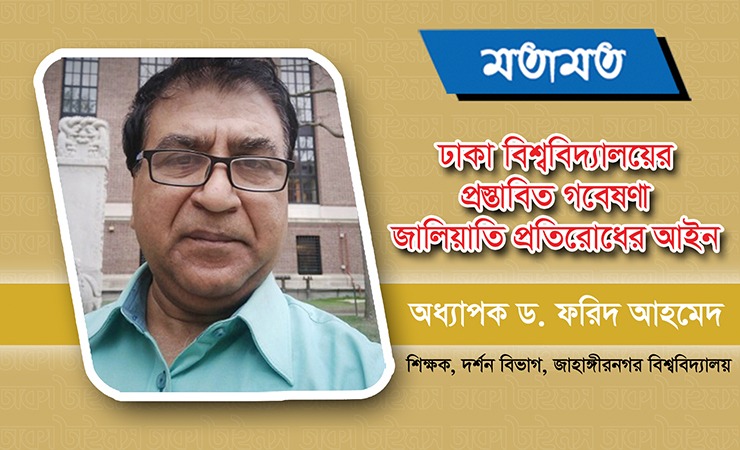
গবেষণা জালিয়াতি, গবেষণা চুরি, গবেষণা নকল, প্লাগিয়ারিজম এবং চন্দ্ররেণুবিদ্যা নিয়ে সম্প্রতিকালে ব্যাপক আড়োলন সৃষ্টি হয়েছে সমাজের বিভিন্ন স্তরে। এসব শব্দ/প্রত্যয় আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমানা পেরিয়ে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী -অভিভাবক -শিক্ষকের আলোচনায় স্থান পেয়েছে। আমরা জেনেছি, বরেণ্য অধ্যাপক জাফর ইকবালের রচনায় ও সম্পাদনায় প্রকাশিত ৭ম শ্রেণীর বিজ্ঞান বইতে দুটি অনুচ্ছেদ পাওয়া গেছে যা নকল। ওই দুটি অনুচ্ছেদ কোনো প্রকার স্বীকৃতি ছাড়া রচয়িতা ন্যাশনাল জিওগ্রাফি থেকে নিয়ে লেখায় সংযুক্ত করেছেন। বিষয়টি জনাব নাদিম মাহমুদ প্রথমআলো পত্রিকায় উপস্থাপন করেছেন। এবং পরবর্তীতে ৭১ চ্যানেলে বিশদ আলোচনা হয়েছে। এবং কোনো প্রকার রাখঢাক না করে অধ্যাপক জাফর ইকবাল স্বীকার করেছেন যে প্লাগিয়ারিজম হয়েছে। এবং এই ঘটনায় তিনি বিব্রত ও লজ্জিত।
প্রতীয়মান হয়, এই ঘটনার পর সরকার, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় নড়েচড়ে বসেছে। অতীতে গবেষণা জালিয়াতির বিষয়টি বিভিন্ন সময়ে সংবাদ মাধ্যমের নজর কেড়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক যখন জাল তথ্য দিয়ে পিএইচডি নেন তখন সংবাদ মাধ্যমে সাড়া পড়ে। এর পর নজরে আসে মিডিয়া ব্যক্তিত্ব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক সামিয়া রহমানের বিষয়। যদিও তিনি আদালত থেকে অভিযোগ থেকে মুক্তি পেয়েছেন। অন্যদিকে ৯৮ % গবেষণা চুরির বিষয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে অত্যন্ত বিব্রতকর পরিস্থিতিতে ফেলে দেয়। তারই সূত্র ধরে বাংলাদেশ হাই কোর্ট বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে দায়িত্ব দেয় একটি নীতিমালা প্রবর্তনের জন্য।
বর্তমান নিয়ম অনুসারে একজন গবেষক তার গবেষণাপত্রে এই মর্মে ঘোষণা দেন যে তিনি যা লিখেছেন তা মৌলিক। তিন আরও ঘোষণা দেন যে, তিনি এই লেখা অন্য কোথায় কোনো ডির্গ্রীর জন্য উপস্থাপন করেননি। এবং গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক অনুরূপভাবে সমর্থন করে কতৃপক্ষকে আশ্বস্থ করেন যে গবেষকের লেখা মৌলিক। এসবের মাধ্যমে গবেষণায় শুদ্ধাচার (integrity ) নীতি বাস্তবায়ন করা হয়। এবং এই শপথ যদি কোনো গবেষক ভঙ্গ করেন সেজন্য এই ধরণের কাজকে একাডেমিক মিসকন্ডাক্ট হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং বিষয়টি নৈতিক স্খলন হিসেবেও বিবেচনা করা হয়। গবেষণায় চুরি একটি মারাত্মক অপরাধ একারণে যে, তিনি কেবল অন্যের লেখা বা উপাত্ত নিয়ে নিজের দাবি করেছেন এমনটি নয়, বরং তিনি দেশ, জাতি, সংশ্লিষ্ট বিভাগ, বিশ্ববিদ্যালয়, ব্যক্তিবর্গ এবং মানবতার সঙ্গে প্রতারণা করছেন। এখানে তিনি সকলের সঙ্গে বিশ্বাস ভঙ্গ করছেন। একজন তত্ত্বাবধায়ক/প্রবন্ধের ক্ষেত্রে একজন রিভিউয়ার সকল শব্দের উৎস সম্পর্কে নাও জানতে পারেন। তিনি ওই গবেষককে বিশ্বাস করেন এবং এই বিশ্বাসভঙ্গের ঘটনা সকলকেই মানসিকভাবে আঘাত করে। এবং মানসিক এই যন্ত্রণা একজন তত্ত্বাবধায়ক/রিভিউয়ারকে শারীরিকভাবে অসুস্থ করে।
এছাড়া যেহেতু গবেষককে ডিগ্রি দেওয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের সামনে উপস্থাপন করা হয় এবং তারা সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ককে বিশ্বাস করেন। একপর্যায়ে একাডেমিক কাউন্সিল, উপাচার্য একটি মানসিক যন্ত্রণার শিকার হন। এভাবে অন্যের ক্ষতি করা অপরাধের পর্যায়ে পড়ে।
আমরা জানি এ ধরনের অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার বিধান প্রচলিত আছে। যেমন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৯৮ শতাংশ গবেষণা জালিয়াতির অভিযোগ আমলে নিয়ে একজন শিক্ষককে শাস্তি দিয়েছে। অন্যদিকে আরেকটি অভিযোগ আমলে নিয়ে সাংবাদিকতা বিভাগের একজন শিক্ষককে শাস্তি দিয়েছে। সেই সঙ্গে অপরাধ বিজ্ঞানের একজন শিক্ষক শাস্তি পেয়েছেন। তবে আদালত থেকে সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক অব্যহতি পেয়েছেন। একটি নিউজ পোর্টাল থেকে জানা যায়, সহযোগী অধ্যাপক আবুল কালাম লুৎফুল কবীরের বিরুদ্ধে পিএইচডি গবেষণা অভিসন্দর্ভের (থিসিস) ৯৮ শতাংশই নকলের অভিযোগ উঠেছিল। তার অভিসন্দর্ভের নাম ছিল ‘টিউবার কিউলোসিস অ্যান্ড এইচআইভি কো-রিলেশন অ্যান্ড কো-ইনফেকশন ইন বাংলাদেশ: অ্যান এক্সপ্লোরেশন অব দিয়ার ইমপ্যাক্টস অন পাবলিক হেলথ (মনিরুল ইসলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ৩১ আগস্ট, ২০২২ ১১:৫৭)’। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এই গবেষককে শাস্তি দিয়েছে। এর আগে সমাজ বিজ্ঞান অনুষদের এবং কলা অনুষদের একজন শিক্ষক শাস্তি পেয়েছেন। সুতরাং, বিদ্যমান আইনটি শাস্তির বিধানকে স্পষ্ট করেছে। তাই মনে প্রশ্ন জাগে:এই আইনটি অতীতে সংঘটিত ঘটনার বিচার করতে ব্যবহার করা যাবে নাকেন? এভাবে যদি শাস্তির বিধান প্রণয়ন করা হয়, তবে অনেক অপরাধী ছাড়া পেয়ে যাবেন।
এখানে আইনের ‘প্রিন্সিপাল অফ নন রেট্রোএক্টিভিটি’ কার্যকর হতে পারে না বলে প্রতীয়মান হয়। ‘প্রিন্সিপাল অফ নন রেট্রোএক্টিভিটি’ একটি অতি বিতর্কিত আইন/নীতি। এই আইন দিয়ে পরিবেশের ক্ষতিকার আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো দায় এড়াতে চেষ্টা করে। আমরা জানি, কীভাবে মাগুরছড়ার পরিবেশ বিনষ্টকারী অক্সিডেন্টাল ও সেভরনকে বিচারের আওতায় আনা হয়েছে। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ‘প্রিন্সিপাল অফ নন রেট্রোএক্টিভিটি’ এখন অচল। সুতরাং, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যদি নিয়ম করে যে, এই আইনটি রেট্রোস্পেক্টিভ নয় তাহলে এই মুহূর্তে যেসব অভিযোগ আছে সেগুলোর কি বিচার হবে না?
গবেষণা চুরি করে যেসব শিক্ষক পদোন্নতি নিয়েছেন তারা রাষ্ট্রের কোষাগার থেকে নিয়মিত বেতন নিচ্ছেন। একজন ছাত্র তার টাকা নেই বলে কনভোকেশনে আসতে পারেনি। আমাদের জানামতে,আর একজন শিক্ষক গবেষণা চুরি করে পদোন্নতি নিয়ে বিগত ছয় মাস কমপক্ষে ১০ হাজার টাকা বেতন অতিরিক্ত নিচ্ছেন! এভাবে তিনি রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে আগামী ৩০ বছরে (পেনশনসহ) প্রায় ৫০ থেকে ৬০ লাখ টাকা আত্মসাৎ করবেন- তার কি বৈধতা পাবে? তার বিচার কি হবে না? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কি এই বিচার করবে না? আইনটি পাঠ করে আমাদের মনে এসব প্রশ্ন মনে জেগেছে। গবেষণা চুরি করে পদোন্নতি নেওয়া রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে অর্থ চুরি এবং তার বিচার না করা চুরিকে বৈধতা দেওয়া। রাষ্ট্রীয় কোষাগারে আছে ভিক্ষুক, গরিব চাষী, ভূমিহীন, গৃহহীন, অসহায় বিধবা, পাথর ভাঙা শিশুর কষ্ট, খেটে খাওয়া মজুরের পানি করা রক্ত-ঘাম।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যে আইন প্রস্তাব করেছে তার ৫.২ ধারার a এবং b তে বলা হয়েছে - ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভান্ডারে রক্ষিত অপ্রকাশিত থিসিস বা অনুরূপ কর্ম চন্দ্র রেণু বিদ্যা (চৌর্যবৃত্তির )র অভিযোগ আনা যাবে না বা আওতা মুক্ত থাকবে। এখানে আরও বলা হয়েছে,ভান্ডারে রক্ষিত সবওইথিসিস থেকে যেসব প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে সেগুলোও আওতা মুক্ত থাকবে। এর অর্থ দাঁড়ায় জাহাঙ্গীরনগর বা অক্সফর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি করে আসা একজন শিক্ষক গবেষণা জালিয়াতির অভিযোগে অভিযুক্ত হবেন।কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি করে যিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করছেন এমন একজন শিক্ষককের বিচার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় করতে পারবে না। এবং এই ধারাগুলো কি বর্তমানে যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে তাদেরকে অব্যহতি দিচ্ছে ? তাহলে কি তারা আগামী ২০ থেকে ৩৫ বছর রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে অবৈধভাবে বেতন নিতে পারবে ? এভাবেই কি রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে ভিক্ষুক, গরীব চাষী, ভূমিহীন, গৃহহীন, অসহায় বিধবা, পাথর ভাঙা শিশুর কষ্ট, খেটে খাওয়া মজুরের পানি করা রক্ত-ঘাম থেকে অর্জিত টাকা লুটপাট চলবে?
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে জাতির বিবেক বলা হয়। এবং সেজন্য একজন প্রাক্তন ছাত্র হিসেবে গর্ব বোধ করি। সুতরাং, জাগরণের প্রত্যাশায় জাতি অপেক্ষায়। আশা করি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ওই অভিযোগুলোর বিচার করবে এবং আগামীতে যদি কোনো গবেষকের বিরুদ্ধে অভিযোগ আসে তবে তার তদন্ত করে ন্যায় বিচার করবে। প্রস্তাবিত আইনটির উপরোক্ত ধারাগুলো বাদে পুরো আইনটি অনেক ভালো একটি আইন। সেজন্য সকলে প্রশংসা পাওয়ার দাবিদার। আশা করি আইনটি পাশের আগে উত্থাপিত বিষয়গুলো বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হবে জাতির বাতিঘর বিতাড়িত হবে দুর্বৃত্ত। জাতি হাসবে ন্যায় বিচারের আলোতে আলোকিত বিশ্ববিদ্যালয় পেয়ে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি আমাদের অনুরোধ আপনারা উত্থাপিত বিষয়গুলোকে বিবেচনা নেবেন যাতে আমরা আগামীতে লজ্জার হাত থেকে মুক্তি পাই।
পুনশ্চ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভান্ডারে রক্ষিত অপ্রকাশিত থিসিস, ডিসার্টেশন, মনোগ্রাফ, রিপোর্ট, পুস্তকের অধ্যায়, পুস্তক, টার্ম পেপার, গ্রাজুয়েট প্রোডাকশন , প্রভৃতি যদি প্লাগিয়ারিজম চেকিং এর আওতামুক্ত থাকে এবং ওই লেখকের উপরোক্ত লেখা থেকে প্রকাশিত প্ৰবন্ধগুলোও প্লেজিয়ারিজম চেকিংয়ের আওতামুক্ত থাকে তবে অপরাধকে আইন করে বৈধতা দেয়া হবে। রুদ্ধ হবে ন্যায় বিচারের পথ। অব্যাহত থাকবে চুরি করা বিদ্যা দিয়ে নেয়া পদোন্নতি বা রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে অবৈধভাবে অর্থ আত্মসাৎ। এভাবে কোনো আইন হতে পারে কি? এবং আইনে আরও বলা হয়েছে ইতিমধ্যে উপরোক্ত অপ্রকাশিত গবেষণা কর্ম থেকে প্রকাশিত প্রবন্ধ/রচনা প্লেজিয়ারিজম চেকিংয়ের আওতামুক্ত থাকে। এতে করে সকল গবেষকের উপর চুরির কালো মেঘ আবৃত করা হবে। এবং সকল গবেষক ও শিক্ষককে সমাজ সন্দেহের চোখে দেখবে যা সৎ গবেষকদের প্রতি অন্যায়, অবিচার, বৈষম্য, বিব্রতকর। এভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সকলকে সন্দেহ তালিকাভুক্ত করতে পারে কি? আশা করা যায়, আমাদের এই উদ্বেগের বিষয়গুলো যথাযথ কর্তৃপক্ষের বিজ্ঞ ও সদয় বিবেচনার স্থান পাবে।
লেখক: অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।
 ঢাকা টাইমস অনলাইন এর সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিডটি ফলো করুন
ঢাকা টাইমস অনলাইন এর সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিডটি ফলো করুন
মন্তব্য করুন