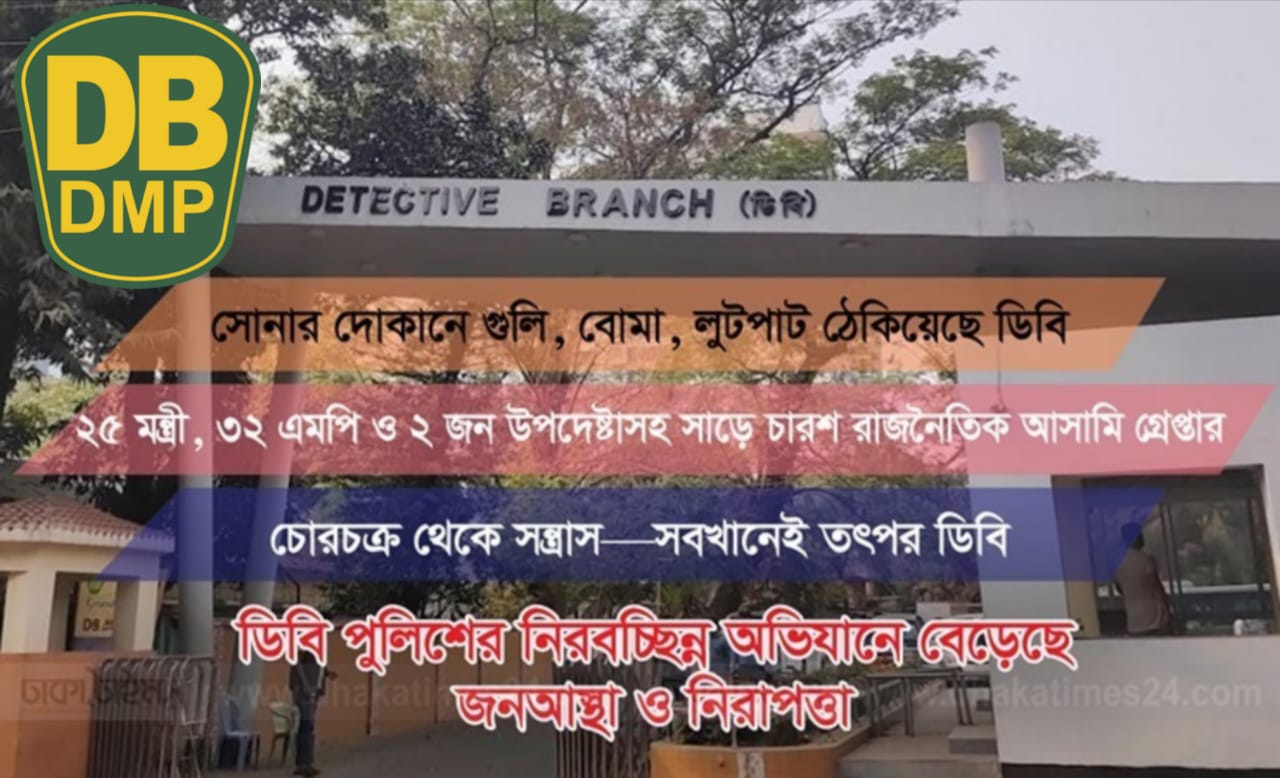উনিশ শতকের মধ্যশ্রেণি, বাংলা বিভক্তি ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯০৫ সালে অবিভক্ত বাংলা বিভক্তি এবং এই বিভক্তির বিরুদ্ধে যে আন্দোলন গড়ে ওঠে তাতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কী ভূমিকা এবং কীরূপ ভূমিকা ছিল তা নিয়ে তর্ক-বিতর্কের শেষ নেই। আমারও এ ব্যাপারে বেশ কৌতূহল। ইতিহাসের ঘটনাকে ধরা যায় কিন্তু সেই সময়কে ধরা দুরূহ। ১৯০৫-১৯১১ এই সময়কে বুঝতে শতাধিক বছর আগে যেতে হবে। সেই সময়টা হলো লর্ড কর্নওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভ করে রবার্ট ক্লাইভ বাংলায় ইংরেজ কর্তৃত্ব স্থাপন করেন। তিনি বাংলায় যে শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন তা দ্বৈত শাসন নামে পরিচিত। এই দ্বৈত শাসনের ফলে বাঙালির দুর্দশা চরম আকার ধারণ করে। উৎপাদন হ্রাস পায় কিন্তু রাজস্ব বৃদ্ধি পেতে থাকে। কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসা ও রাজস্ব বৃদ্ধির ফলে দেশের অর্থনীতি ক্রমশ ভেঙে পড়ে। অতিরিক্ত রাজস্ব আদায়ের জন্য নায়েবে নাজিমগণ কঠোর ব্যবস্থা নেন। ফলে প্রজাদের সীমাহীন দুঃখ-দুর্দশা পোহাতে হয়। ব্যাপক অরাজকতা ও দুর্নীতি বাংলাকে ধ্বংসের প্রান্তে নিয়ে যায়। নবাব ছিলেন ক্ষমতাহীন। এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার ক্ষমতা নবাবের ছিল না।
এই পরিস্থিতিতে ১৭৬৯-৭০ (বাংলা ১১৭৬) সালে এক ভয়াবহ মন্বন্তর দেখা দেয়। যা ইতিহাসে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামে পরিচিত। দুর্ভিক্ষে এক কোটি তথা বাংলার এক তৃতীয়াংশ লোক মারা যায় এবং কৃষি জমির এক তৃতীয়াংশ জঙ্গলে পরিণত হয়। বহু জায়গায় মানুষ মৃতের মাংস খেয়ে বেঁচে থাকার চেষ্টা করেছে। খাদ্যের অভাবে মানুষ চুরি, ডাকাতি, লুণ্ঠন শুরু করে। আইনশৃংখলার চরম অবনতি ঘটে। এই পরিস্থিতিতে কোম্পানি সরাসরি দিওয়ানির দায়িত্ব গ্রহণ করে। কোম্পানির দায়িত্ব হলো রাজস্ব আদায়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা, দিওয়ানি ও বিচার ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করা। দ্বৈত শাসনের ফলে যে অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙে পড়েছিল তা সংস্কার করা। যার প্রেক্ষিতে গভর্নর লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস দ্বৈত শাসন বিলুপ্ত করেন।
১৭৭২ সালের পর থেকেই নতুন ভূমি ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ শুরু হয়। নব্য ব্যবস্থাপনায় জমিদারগণকে ভূমির স্থায়ী মালিকানা দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়। তাদের ধারণা ছিল ভূমি ব্যবস্থাপনায় স্থায়িত্ব এলে জমিদারগণ ভূমিতে পুঁজি বিনিয়োগ করবেন। ফলে ভূমি উন্নত হবে, কৃষিতে উৎপাদন বাড়বে। অর্থনীতি সমৃদ্ধ হবে। ইংল্যান্ডে যেমন ভূস্বামী সমাজ কৃষিশিল্পে বিপ্লব এনেছে তেমনি বঙ্গদেশের জমিদারদের নেতৃত্বে কৃষিবিপ্লব হবে। প্রথমে পঞ্চসনা, পরে দশসালা মেয়াদে ভূমি বণ্টন করা হয়। পরে এই বণ্টনই স্থায়ীভাবে করে দেওয়া হয়। তাই এর নাম চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদার সমাজে অভূতপূর্ব পরিবর্তন আসে। সূর্যাস্ত আইনে নতুন জমিদারী লাভ করে যারা তাদের বেশির ভাগই ছিল সরকার ও জমিদারের কর্মচারী, বেনে, মুৎসুদ্দি, ব্যবসায়ী, মহাজন প্রমুখ। যেমন নড়াইলের জমিদারীর প্রতিষ্ঠাতা রামকৃষ্ণ রায় ছিলেন নাটোর জমিদারের প্রধান গোমস্তা, কলকাতার ঠাকুর জমিদারীর প্রতিষ্ঠাতা গোপীনাথ ঠাকুর ও দ্বারকানাথ ঠাকুর ছিলেন প্রথমে সরকারি কর্মচারী ও পরে ব্যবসায়ী। ঢাকার জমিদার পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা খাজা আলিমুল্লা ছিলেন ব্যবসায়ী। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকালে ছয়টি বৃহৎ জমিদারীর মধ্যে একমাত্র বীরভূমের রাজা ছিলেন মুসলমান বাকি সবাই ছিলেন হিন্দু। ক্ষুদ্র জমিদারদের মধ্যেও বেশিরভাগ ছিল হিন্দু।
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদার সমাজের গঠন ও মানসিকতায় পরিবর্তন আসে। প্রজা ও জমিদারদের মধ্যে পর্যায়ক্রমে মধ্যস্বত্বভোগী সৃষ্টি হয়। এই নতুন জমিদারদের অনেকেই শহরে বসবাস করে পুরাতন পেশায় লিপ্ত থাকে। জমিদারী কার্য পরিচালিত হয় স্থানীয় নায়েব গোমস্তা দ্বারা। জমিদারী পরিচালনার ঝামেলা এড়ানোর জন্য অধিকাংশ অনুপস্থিত জমিদার নানারকম মধ্যস্বত্ব প্রথা সৃষ্টি করে। কৃষকের সঙ্গে জমিদারের সরাসরি সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়।
মুঘল আমলে যারা ছিল স্থায়ী রায়ত বা প্রজা ভূমিতে তাদের স্থায়ী অধিকার ছিল। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমিদার হয় জমির একমাত্র মালিক। রায়ত পরিণত হয় জমিদারের ইচ্ছাধীন প্রজায়। মুঘল শাসনতন্ত্রে জমিদারের পক্ষে খাজনা বৃদ্ধি করা বা রায়তকে জমি থেকে উৎখাত করা ছিল প্রায় অসম্ভব। প্রত্যেক পরগণার জন্য ভূমির গুণ অনুযায়ী খাজনার হার নির্দিষ্ট করা ছিল। তাই অতিরিক্ত খাজনা ধার্য করা জমিদারের পক্ষে ছিল কঠিন। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমিদারই জমির একমাত্র মালিক বলে ইচ্ছামত খাজনা বৃদ্ধি করার ক্ষমতা জমিদার লাভ করে। জমি এখন জমিদারের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। পুরাতন রাজস্ব ব্যবস্থার পরিবর্তন ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলন করে বৃটিশ সরকার বাংলার মুসলমানদের আর্থিক জীবনে তীব্র আঘাত হানে। কোম্পানির কর্তৃপক্ষ জমিদারদের রাজস্ব বৃদ্ধি করায় মুসলমান জমিদাররা জমিদারী রক্ষায় অপারগ হয়। তাদের জমিদারীর অধীনস্থ হিন্দু কর্মচারী অথবা বেনিয়া ও ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করা হয়। জমিদারী বন্দোবস্ত এমন এক বাবু শ্রেণিকে দেওয়া হয় যারা ঘুষ ও অন্যান্য উপায়ে ধনী হয়েছে। (উইলিয়াম হান্টার)
লর্ড কর্নওয়ালিস প্রবর্তিত ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী ভূমি ব্যবস্থার ফলে দেশে যে জমিদার ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির সৃষ্টি হয় পরে তারাই সমাজের ভিত্তি ও অর্থনৈতিক জীবনের মেরুদণ্ড হয়ে দাঁড়ায়। এরা ইংরেজদের সৃষ্ট ভূমি ব্যবস্থা ও সরকারি চাকরির উপর নির্ভরশীল ছিল এবং ধীরে ধীরে তারা ইংরেজি শিক্ষা এবং পাশ্চাত্য জীবন দর্শনের প্রতি আনুগত্যশীল হয়। বৃটিশ শাসনের রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক কাজকর্মের কেন্দ্রস্থল ছিল কলকাতা। ফলে ইংরেজদের জীবনযাত্রা ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সঙ্গে বাঙালিদেরই সর্বাগ্রে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ঘটে। পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে এই দেশে নানাপ্রকার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন শুরু করে। এই সকল অভিজাত ও মধ্যভোগীশ্রেণি থেকে সমাজসংস্কারক, কবি, সাহিত্যিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতার আবির্ভাব ঘটে। তারাই পরবর্তীকালে জাতীয় জাগরণের নেতৃত্ব দেয়।
লর্ড কার্জন ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ কার্যকর করলেও এর বহু আগে থেকেই বাংলা বিভক্তি নিয়ে বিভিন্ন প্রস্তাব ও পরিকল্পনা গৃহীত হয়। ১৮৫৪ সালে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম নিয়ে একজন লেফটেন্যান্ট গভর্নরের অধীনে বাংলা প্রেসিডেন্সি গঠিত হয়। ১৮৫৫-৫৬ সালে বাংলা প্রেসিডেন্সির আয়তন ছিল ২ লক্ষ ৫৩ হাজার বর্গমাইল এবং জনসংখ্যা ৪ কোটি। স্বয়ং লর্ড ডালহৌসি তখন স্বীকার করেন একজন শাসকের পক্ষে এত বড়ো একটা প্রদেশ শাসন করা রীতিমত কষ্ট সাধ্য। ১৮৬৬ সালে উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষ মোকাবিলায় সরকারের ব্যর্থতা অনুসন্ধানের জন্য ভারত সচিব স্যার স্ট্যাফোর্ড হেনরি নর্থকোট ১৮৬৭ সালে একটি কমিটি গঠন করেন। কমিটির প্রতিবেদনে বাংলা প্রদেশের প্রশাসনিক অসুবিধাকে দুর্ভিক্ষের অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এবং বাংলা বিভক্তির প্রস্তাব করা হয়। এভাবে বাংলায় নিযুক্ত কর্মকর্তাগণ নানান অসুবিধার কথা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেন। এই প্রেক্ষিতেই বিভিন্ন সময়ে প্রশাসনিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কারণে বাংলাকে বিভক্তির প্রস্তাব ও পরিকল্পনা করা হয়। বাংলা বিভক্তির কথা তুললেই বাঙালিরা এই বিভক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। লর্ড কার্জন দায়িত্ব গ্রহণ করে প্রশাসনিক সুবিধা ও দক্ষতা বাড়ানোর জন্য বঙ্গভঙ্গের পক্ষে কাজ শুরু করেন। ১৯০৫ সালে তিনি বাংলা প্রদেশ ভাগ করেন। যা বঙ্গভঙ্গ নামে পরিচিত। লর্ড কার্জনের পরিকল্পনা অনুযায়ী ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও আসাম নিয়ে গঠন করা হয় ‘পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ’ এবং ঢাকাকে করা হয় রাজধানী। অপরদিকে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে গঠিত হয় বাংলা প্রদেশ যার রাজধানী করা হয় কলকাতা।
বাঙালি মধ্যবিত্ত হিন্দু সমাজ এই বিভক্তি মানতে পারে না। কলকাতাকেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত হিন্দু শ্রেণি বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা শুরু করে। ১৯০৩ সালে বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব প্রথমবারের মতো প্রকাশিত হলে তারা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে কিন্তু পূর্ব বাংলার মুসলমানরা একে স্বাগত জানায়। তারা তাদের আশা আকাঙ্ক্ষাপূরণের সুযোগ পায়। লর্ড কার্জন এক্ষেত্রে বৃটিশের সাম্রাজ্যবাদী নীতি ‘ভাগ করো এবং শাসন করো’ প্রয়োগ করলেও পূর্ব বাংলার মুসলমানদের জন্য এটা ছিল আশীর্বাদ। এখানকার তফসিলী হিন্দুরাও একে সানন্দে গ্রহণ করেছিল।
পূর্ববাংলা ভারতবর্ষের একটি পশ্চাদপদ প্রদেশে পরিণত হয় আঠার শতকের মাঝামাঝি। মুর্শিদকুলী খান আঠারো শতকের প্রথম দিকে ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে রাজধানী স্থানান্তর করেন। ফলে ভূস্বামী, ব্যবসায়ী ও রাজধানীর ওপর নির্ভরশীল গোষ্ঠী ঢাকা ছেড়ে সেখানে চলে যায়। ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার পর ১৭৭২ সালে মুর্শিদাবাদ থেকে শাসনযন্ত্র কলকাতায় স্থানান্তর করা হয়। অতএব পুর্ববাংলা অবহেলিত থেকে যায়। পুর্ববাংলার জনসংখ্যা বৃদ্ধি, যাতায়াত সমস্যা ও প্রদেশের অন্তর্গত প্রশাসনিক ব্যবস্থার দুর্বলতা, অদক্ষতার ফলে পুর্ববাংলার বিস্তীর্ণ এলাকা দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত থাকে। জনকল্যাণ ও উন্নয়নের জন্য যে অর্থ ব্যয় হতো তা বাস্তব প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। পূর্ব বাংলার যোগাযোগ, পুলিশ ও ডাক ব্যবস্থা অত্যন্ত সনাতন প্রকৃতির ছিল। ফলে চুরি, ডাকাতি ও বেআইনী কাজ হতো এখানে। ১৯০৯ সালে পূর্ববাংলা ও আসাম প্রদেশের আইন পরিষদে বক্তৃতায় সদস্য শামসুল হুদার বক্তব্যে পূর্ববাংলার বাস্তব চিত্র উঠে আসে। তিনি বলেন, ‘বাংলা বিভক্তির আগে বিরাট অঙ্কের অর্থ কলকাতা ও আশেপাশের জেলাগুলোতে ব্যয় হতো। শ্রেষ্ঠ কলেজ, হাসপাতাল ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ভারতের রাজধানীর আশেপাশে করা হতো। আর পূর্ববাংলার মানুষ পেয়েছে উত্তরাধিকারসূত্রে বছরের পর বছর পুঞ্জীভূত অবহেলা ও বঞ্চনা।’
বাঙালি এলিট শ্রেণিভুক্ত লোকদের কোলকাতায় অবস্থান একে সর্বভারতীয় মিলনস্থল হিসেবে গড়ে তোলে। সরকারি পৃষ্ঠ্পোষকতায় পূর্ববাংলা হতে সরবরাহক্তৃ কাঁচামালের বদৌলতে কলকাতার বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। অন্যদিকে দীর্ঘদিনের অবহেলা, উদাসীনতা ও ফলপ্রসূ প্রকল্পের অভাবে পুর্বাঞ্চলের অধিবাসীদের অবস্থা দিন দিন অবনতির দিকে যায়। পূর্ববাংলার অর্থকরী ফসল ছিল পাট। অথচ পূর্ববাংলায় পাটকল তৈরি না হয়ে বেশিরভাগ পাটকল কলকাতার হুগলী নদীর তীরে গড়ে তোলা হয়। এর ফলে পাটের প্রকৃত মূল্য থেকে এখানকার কৃষক যেমন বঞ্চিত হয় তেমনই বেকার সমস্যাও প্রকট হয়।
পূর্ববাংলার অর্থনীতি কৃষিভিত্তিক। এখানে জমিদারী ব্যবস্থা থাকলেও জমিদাররা কলকাতায় অবস্থান করতেন। তাদের মধ্যস্বত্বভোগীরা নিরীহ কৃষকদের ওপর শোষণ চালাতো। জমিদারদের আরাম-আয়েশের জন্য ব্যয়িত অর্থ সংগ্রহ করা হতো পূর্ববাংলার কৃষকদের থেকে। পূবের অর্থ এভাবে পশ্চিমে ব্যয় হতো।
তৎকালে সরকারি চাকরি ও ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের একচেটিয়া প্রাধান্য থাকায় পূর্ববাংলার মুসলিম জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ে। মুসলমানদের প্রতি বৃটিশ সরকারের চরম অবহেলা ছিল। ফলে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা দিন দিন বাড়তে থাকে।
চট্টগ্রাম বন্দরকে কেন্দ্র করে আসাম ও পূর্ব বাংলার বৈদেশিক বাণিজ্যের যে প্রসার হতে পারতো সেদিকে সরকারের দৃষ্টি ছিল না। চট্টগ্রামের উন্নতি হলে ব্যবসা বাণিজ্যের দিক থেকে কলকাতার গুরুত্ব হ্রাস পাবে এই আশঙ্কায় কলকাতা কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দর সম্প্রসারণে কোনো চেষ্টাই করেনি। বাংলাদেশের বড়ো নদীগুলোকে জাহাজ চলাচলের জন্য ব্যবহার করা হয়নি। কলকাতার সঙ্গে উত্তর-পশ্চিম ভারতের সাথে রেল যোগাযোগের জন্য রেলপথ তৈরি করা হলেও পূর্ববাংলার সঙ্গে রেলপথ যোগাযোগ ছিল অবহেলিত। ঢাকা বিভাগ থেকে গণপূর্ত কাজের জন্য ৬ লক্ষ টাকা তোলা হলেও তা ব্যয় করা হয় কলকাতা, বিহার ও উড়িষ্যায়।
ইংরেজ শাসনের শুরু থেকে তাদের বৈষম্যমূলক আচরণের ফলে মুসলিম সমাজ ধীরে ধীরে সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রাধান্য হারাতে থাকে। ফলে ১৯০৫ সালে পূর্ববাংলার মুসলমান সমাজ তাদের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারের আশায় বৃটিশ সরকারের বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব জোরালোভাবে সমর্থন করে। তাছাড়া অনেক আগে থেকেই পূর্ববাংলায় মুসলমান এবং পশ্চিম বাংলায় হিন্দু ধর্মাবলম্বিদের প্রাধান্য লক্ষণীয় ছিল। সংখ্যাগরিষ্ট হলেও পূর্ববাংলার মুসলমানরা ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে হিন্দু জমিদার ও প্রভাবশালীদের হাতে বাধাগ্রস্ত হতো। এজন্য নতুন প্রদেশে নিজেদের জীবনদর্শন অনুযায়ী সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে মুসলমানদের মধ্যে জাগরণ দেখা দেয়।
বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব প্রথম থেকেই হিন্দুদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি করে। নতুন প্রদেশের বিস্তারিত সীমারেখা প্রকাশিত হয় মে মাসে। এবং ১৬ই অক্টোবর থেকে তা কার্যকর হবে, এই সংবাদ হিন্দু নেতাদের মধ্যে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি করে। তারা তাদের পত্রপত্রিকায়, বক্তৃতামঞ্চে একে বাঙালি বিরোধী, জাতীয়তাবাদ বিরোধী, বঙ্গমাতার অঙ্গচ্ছেদ প্রভৃতি বিশেষণে আখ্যায়িত করে। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী তার ‘বেঙ্গলী’ পত্রিকার সম্পাদকীয়তে একে জাতীয় দুর্যোগ এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদের সংকটময় মুহূর্ত বলে বর্ণনা করেছিলেন। ১৯০৫ সালের ৭ই আগস্ট কলকাতা টাউন হলে এক বিরাট জনসভা হয়। সেখানে রাজা, জমিদার, শিক্ষক, উকিল ও অগণিত লোকের ভিড় হয়। তাদের হাতে কালো পতাকায় লেখা ‘সংযুক্ত বঙ্গ’, ‘একতাই শক্তি’, ‘বন্দে মাতরম’ ইত্যাদি বাক্য এবং মুখে শোকের ছায়া। সেখানে প্রস্তাব হলো বঙ্গভঙ্গ রহিত না হওয়া পর্যন্ত এর বিরুদ্ধে আন্দোলন চলবে। সারা দেশে তারা বিলাতি দ্রব্য বর্জন করা হয়।
বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ উপন্যাসে বর্ণিত দেশোদ্ধারব্রতী ‘সন্তান’ বা একদল সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী বাঙালির আদর্শ হলো এবং তাদের সেই বিখ্যাত গান ‘বন্দে মাতরম’ আন্দোলনকারীদের মন্ত্ররূপে গহীত হলো। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রজনীকান্ত সেন এবং সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংগীতে দেশপ্রেমের বন্যা বইতে লাগলো। ‘আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি’, ‘বঙ্গ আমার জননী আমার, ধাত্রী আমার আমার দেশ’, ‘ও আমার দেশের মাটি তোমার ’পরে ঠেকাই মাথা’- এসকল গান ছাত্রদের মনে প্রবল উন্মাদনার সৃষ্টি করলো।
১৯০৫ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর মহালয়ার দিন প্রাতঃকালে কালীঘাটের কালী মন্দিরে প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোক সমবেত হয়। শত শত কণ্ঠে সারাদিন সংকীর্তন করলো এবং বন্দে মাতরম গাইলো। কালী মায়ের নিকট প্রার্থনা করলো যেন বঙ্গবঙ্গ রহিত হয়। দেবীর সম্মুখে একে একে শপথ করলো, তারা বিলাতি বস্ত্র বর্জন করবে, সকল দেব-দেবীর পূর্বে জননী জন্মভূমির পূজা করবে।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও সে সভায় ছিলেন। সভা ভঙ্গের পর দলে দলে লোকজন রবীন্দ্রনাথের নতুন লেখা গান গাইতে গাইতে পথযাত্রা শুরু করলো। ‘ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে ততই বাঁধন টুটবে/ মোদের ততই বাঁধন টুটবে’। এরপর আরেকটি নতুন গান ধরলো ‘বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান/ আমাদের ভাঙ্গাগড়া তোমার হাতে এমন অভিমান’।
১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ আইন কার্যকর হবে। রবীন্দ্রনাথ তার কবিত্বপূর্ণ ভাষায় প্রস্তাব রাখলেন, ঐদিন উভয় বঙ্গের মিলনের চিহ্নস্বরূপ রাখীবন্ধন অনুষ্ঠিত হবে। তারা পরস্পরের হাতে হরিদ্রা বর্ণের সুতা বেঁধে দিবে। রাখি বন্ধনের মন্ত্র হবে ‘ভাই ভাই এক ঠাঁই’। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশের জন্য ‘অরন্ধন’ পালন করার প্রস্তাব দেন। ঐ দিন শিশু ও রোগী ব্যতীত সকলেই উপবাস থাকবে।
৩০ আশ্বিন, ১৬ই অক্টোবর রবীন্দ্রনাথকে পুরোভাগে রেখে গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও জনসাধারণ শোভাযাত্রা করে গঙ্গাতীরে সমবেত হলো। গঙ্গাস্নান করে পরস্পরের রাখি বন্ধন করলো। এই উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথের প্রার্থনা সংগীত ‘বাংলার মাটি বাংলার জল /বাংলার বায়ু বাংলার ফল/ পূণ্য হউক, পূণ্য হউক হে ভগবান’ সর্বত্র গীত হলো। সেদিন ঐ গান গেয়ে বীডন উদ্যানে, সেন্ট্রাল কলেজে ও অন্যত্র বহুস্থানে রাখিবন্ধন হলো। বঙ্গদেশ কেবল জন্মভূমি নহে, আমাদের জননী তথা বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ আমাদের জননীর অঙ্গচ্ছেদের তুল্য স্বদেশি আন্দোলনের এই মূল ভাবনাটি রবীন্দ্রনাথ বিভিন্নভাবে রূপায়িত করেছেন।
‘আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি
তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী’
স্বদেশি আন্দোলনে জাতীয় জীবন যে দেশপ্রেমের প্রবল স্রোতে ভেসে গিয়েছিল-
‘এবার তোর মরা গাঙ্গে বান এসেছে জয় মা বলে ভাসা তরী’ অথবা
‘আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে
ঘরের হয়ে পরের মতন ভাই ছেড়ে ভাই কদিন থাকে?’
অথবা, ‘আমাদের যাত্রা হল শুরু এখন, ওগো কর্ণধার
তোমারে করি নমস্কার।’
আবার ‘বাঙালি ভীরু’ এই অপবাদ মিথ্যা প্রমাণ করতে লিখলেন-
‘আমি ভয় করব না ভয় করব না
দুবেলা মরার আগে মরব না ভাই মরব না’
স্বদেশি আন্দোলন নিখিল ভারতের রাজনীতির ক্ষেত্রে যে বিষম আলোড়ন তুলল তা হিন্দু জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে রূপ নিলো। তার নেতৃত্বে ছিলেন তিলক, অরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র পাল ও লালা লাজপৎ রাত। অরবিন্দ ঘোষ বিপিনচন্দ্র পাল প্রতিষ্ঠিত ‘বন্দে মাতরম’ নামক দৈনিক পত্রিকার পরিচালনার ভার নেন। তিনিই সর্বপ্রথম দেশপ্রেমকে ধর্মের পর্যায়ে উন্নীত করেন এবং জন্মভূমিকে কেবল জননী নয়, একমাত্র উপাস্য দেবীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। তার সেবাই মোক্ষলাভের উপায় বলে প্রচার করেন। ঋষি অরবিন্দ ছিলেন দেবীরূপিনী দেশমাতৃকার সাধক, তেমনই কবি রবীন্দ্রনাথ ছিলেন চাক্ষুষ জননী জন্মভূমির প্রধান চারণ গায়ক। ‘আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে...’ এ গানে কবি কবিত্বময় ভাষায় অরবিন্দের কল্পনা মূর্ত করে তুলেছেন।
এরকম নানাবিধ আলোচনায় কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও স্বদেশি আন্দোলনের অন্য নেতাদের এমনকি সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর উপরও হিন্দুধর্মের যথেষ্ট প্রভাব ছিল।
মারাঠী নেতা বালগঙ্গাধর তিলক ১৮৯৫ সালে মহারাষ্ট্রে বার্ষিক ‘শিবাজী উৎসব’ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯০২ সাল থেকে প্রতি বছর কলকাতায়ও এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ১৯০৪ সালে শিবাজী উৎসব বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়ে বিপুল উন্মাদনা ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। এই উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ ‘শিবাজী উৎসব’ কবিতাটি লেখেন। যতদিন বাংলা ভাষা থাকবে ততদিন এই কবিতাটি হিন্দু জাতিকে প্রেরণা জোগাবে। রবীন্দ্রনাথ এই কবিতায় ইংরেজ ও মুসলমান ঐতিহাসিকদের উদ্দেশ্যে লিখেছেন-
‘বিদেশীর ইতিবৃত্ত দস্যু বলি করে পরিহাস
অট্টহাস্যরবে-
তব পুণ্য চেষ্টা যত তস্করের নিস্ফল প্রয়াস
এই জানে সবে।
অয়ি ইতিবৃত্ত কথা, ক্ষান্ত কর মুখর ভাষণ
ওগো মিথ্যাময়ী
তোমার লিখন পরে বিধাতার অব্যর্থ লিখন
হবে আজি জয়ী।'
অরবিন্দ সম্পর্কে কবি রবীন্দ্রনাথ যা বলেছিলেন, তা অনেক বিপ্লবী নেতার সম্বন্ধেই প্রযোজ্য-
'তোমা লাগি নহে মান
নহে ধন নহে সুখ, কোন ক্ষুদ্র দান
চাহ নাই কোন ক্ষুদ্র কৃপা, ভিক্ষা
লাগি বাড়াওনি আতুর অঞ্জলি।'
স্বদেশি আন্দোলন পর্যায়ক্রমে বিপ্লবাত্মক আন্দোলনে রূপ নেয়। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজ সরকারের পতন ঘটানো। তিনি সেসময় কতগুলো গীতি কবিতা রচনা করেন যাতে বিপ্লবীদের মনোবৃত্তির অপূর্ব প্রকাশ ঘটেছে-
১। সংকল্প বা অঙ্গীকার-
‘শুভ কর্মপথে ধর নির্ভয় গান/ সব দুর্বল সংশয় হোক অবসান।’
২। দুর্গম পথে দ্বিধা সংকুল যাত্রীর উদ্দেশ্যে লিখেছেন-
‘ওরে নুতন যুগের ভোরে/ দিস নে সময় কাটিয়ে বৃথা সময় বিচার করে।’
৩। দ্বিধাগ্রস্ত মনে সাহস সঞ্চারের জন্য তার অভয় বাণী-
‘নিশিদিন ভরসা রাখিস, ওরে মন হবেই হবে/ যদি পণ করে থাকিস, সে পণ তোমার রবেই রবে।’
৪। বিপ্লবীদের প্রধান বাধা স্বজনদের পিছুটান, বন্ধু বান্ধবের বিমুখতা, অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ, দুর্গম পথে সহযাত্রীর অভাব এসব অতিক্রম করার ভরসাবাণী-
'তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে / তা বলে ভাবনা করা চলবে না
ও তোর আশালতা পড়বে ছিড়ে/ হয়ত রে ফল ফলবে না।’
৫। যদি নিতান্তই সঙ্গী না জোটে তবে একলা পথে চলতে হবে-
‘যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চল রে।’
৬। নির্ভীকতার আদর্শ সম্বন্ধে কবির বক্তব্য-
‘আমি ভয় করব না ভয় করব না / দু’বেলা মরার আগে মরব না ভাই মরব না।’
বোমা হামলার মামলায় আলিপুর আদালতের কাঠগড়ায় বন্দিদের সমবেত করা হতো। বিচারে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত এক তরুণ বন্দি কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথের গান গেয়ে উঠলো-
‘সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে/ সার্থক জনম মা গো তোমায় ভালোবাসে।’
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই গীতি কবিতাগুলো সেসময় বিপ্লবীদের মনে বিপুল উদ্দীপনা, শক্তি, সাহস আর সান্ত্বনা জুগিয়েছিল।
বিপ্লবীরা বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্র ছড়াতে থাকে। বাংলা তথা ভারতের রাজনীতিতে সন্ত্রাসবাদের উদ্ভব ঘটে। এর নেতৃত্বে ছিলেন পুলীন দাস ও প্রতুল গাঙ্গুলী। ১৯০৮ সালের পর থেকে সন্ত্রাসবাদীদের কার্যকলাপের বিস্তার ঘটে। বাংলায় বহু গুপ্ত সমিতি গড়ে ওঠে। বিপ্লবীরা এখানে প্রশিক্ষণ নেয়। ১৯০৮ সালে বিপ্লবী ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী এই আন্দোলন করতে গিয়ে জীবন দান করেন।
প্রথম দিকে বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনের সাথে কিছু কিছু মুসলমান যুবক সংশ্লিষ্ট ছিল। পরবর্তীতে হিন্দুদেবী কালীর নামে শপথ গ্রহণ এবং বন্দে মাতরম সংগীত চালু করা হলে মুসলমানরা আন্দোলন থেকে নিজেদেরকে গুটিয়ে নেয়। আন্দোলন হিন্দু জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে রূপ নেয়। তাদের উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু শাসনের পুনরুত্থান। গ্রামাঞ্চলে হিন্দু জমিদার ও মহাজনেরা দরিদ্র মুসলমান কৃষকদের স্বদেশি আন্দোলনে যোগদান এবং বিলাতি দ্রব্য বর্জন করতে বাধ্য করতো। যেসকল মুসলমান জমিদার ও ব্যবসায়ীরা আন্দোলনে সহযোগিতা করতে অস্বীকার করতো তাদের সঙ্গে স্বদেশিদের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। এভাবে বিভিন্ন জায়গায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়।
এই সংকটময় মুহূর্তে পূর্ব বাংলার মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার জন্য এবং নতুন প্রদেশকে টিকিয়ে রাখার জন্য নবাব সলিমুল্লাহ নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। ধনবাড়ির জমিদার নবাব আলী চৌধুরী ও পূর্ব বাংলার উদীয়মান নেতা আবুল কাসেম ফজলুল হক তাকে পূর্ণ সহযোগিতা করেন। তারা পূর্ব বাংলার বিভিন্ন স্থানে সভা করেন এবং নতুন প্রদেশের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করেন এবং নবগঠিত প্রদেশের পক্ষে জনমত গড়ে তোলেন। ১৯০৬ সালে নবাব সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে মুসলমানদের উন্নয়নকল্পে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়।
এদিকে নতুন প্রদেশে পুর্ববঙ্গ ও আসামের জনগণ এ সময় শিক্ষা ও অর্থনীতিসহ বিভিন্নক্ষেত্রে উন্নতি করতে শুরু করে। কিন্তু অচিরেই নতুন প্রদেশের ভাগ্যে নেমে আসে প্রচণ্ড আঘাত। বৃটিশ সরকার কংগ্রেস নেতা এবং বৃটিশ বণিকদের চাপে বঙ্গভঙ্গ রদের সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯১১ সালের নভেম্বর মাসে ভারতের রাজধানী কলকাতা থাকে দিল্লীতে স্থানান্তর করা হয়। তারা মনে করেন এতে কলকাতা সন্ত্রাসবাদীদের হাত থেকে রেহাই পাবে, অপরদিকে দিল্লিতে রাজধানী হওয়ায় উত্তর ভারতের মুসলমানগণ খুশি হবে। ১২ই ডিসেম্বর সম্রাট পঞ্চম জর্জ ঐতিহাসিক দিল্লি দরবারে বঙ্গভঙ্গ রদের কথা ঘোষণা করেন। এর ফলে বাংলা ভাষাভাষী পাঁচটি বিভাগ নিয়ে বাংলাদেশ পুনর্গঠিত হয়। বিহার ও উড়িষ্যাকে বঙ্গদেশ থেকে পৃথক করা হয়।
হিন্দুদের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন শুধু ভাবাবেগপ্রসূত ছিল না। তারা চিন্তা-ভাবনা করেই এই আন্দোলন গড়ে তোলে। এই আন্দোলন তাদের নিকট গভীর তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। বাংলা বিভাগ তাদের জন্য সত্যই দুর্যোগের মতোই ব্যাপার ছিল। তারা বুঝতে পেরেছিল এই অঞ্চলে নতুন ব্যবস্থা কার্যকর হলে অনগ্রসর মুসলিম কৃষক শ্রমিক সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার ও নবজাগরণ দেখা দিবে। ফলে পুর্বের ন্যায় তাদেরকে শোষণ ও নিষ্পেষণ করা যাবে না। শিক্ষাবিস্তারের সাথে নিপীড়িত মুসলমান সমাজের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনাবোধ জাগ্রত হবে এই ভয়ে হিন্দু রাজনৈতিক নেতারা সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ট প্রদেশ তাদের মনে ঈর্ষার উদ্রেক করে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে হিন্দু পুনর্জাগরণ এবং স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী কর্তৃক আর্যসমাজ প্রতিষ্ঠার পর থেকে হিন্দুদের মনে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার বীজ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। তখন এই আন্দোলন নিছক ধর্ম ও সামাজিক সংস্কারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। ক্রমশ তা মুসলিম বিরোধী আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়। হিন্দু নেতৃবৃন্দের কায়েমী স্বার্থ এবং সংকীর্ণ জাতীয়তাবোধই তাদেরকে এত উত্তেজিত ও মারমুখো করে তুলেছিল। জমিদার ও শিক্ষিত মধ্যশ্রেণি ছিল এই আন্দোলনের পুরোভাগে। বৃটিশ শাসনের শুরু থেকে এরাই নানান সুযোগ সুবিধা ভোগ করে আসছিল। জমিদাররা অনেকেই এই অঞ্চলের সম্পদ নিয়ে কলকাতায় তাদের ঐশর্যের ভান্ডার গড়ে তুলেছিল। অথচ নায়েব গোমস্তাদের উৎপীড়নে পূর্ববঙ্গের কৃষকরা জর্জরিত ছিল এবং তাদের আর্থিক সমৃদ্ধি ধ্বংস হচ্ছিল। ঢাকায় রাজধানী স্থাপিত হলে নতুন প্রদেশে নতুন শিল্প কারখানা গড়ে উঠবে এবং নতুন পুঁজিপতির জন্ম হবে, ফলে তাদের একচেটিয়া ব্যবসা এবং মুনাফা নষ্ট হবে এই আশঙ্কায় কলকাতার পুঁজিপতি ও ব্যবসায়ীরা নতুন প্রদেশ গঠনের প্রতি বিরূপ মনোভাবাপন্ন ছিল। শের এ বাংলা এ কে ফজলুল হক একবার বলেছিলেন, ‘Politics of Bengal is in reality economics of Bengal.’ বাংলার অর্থনীতিই বাংলার আসল রাজনীতি। শিক্ষিত মধ্যশ্রেণি আইনজীবী এবং সাংবাদিকরাও অনুরূপ কারণে ভীত ছিল। ঢাকাতে নতুন হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠা হলে তাদের আইন ব্যবসায় ভাটা পড়ার সম্ভাবনা ছিল। কারণ তাদের অধিকাংশ মক্কেল ছিল পূর্ববঙ্গের। ঢাকা থেকে সংবাদপত্র ও সাময়িকী প্রকাশিত হলে কলকাতার সংবাদপত্রের চাহিদা কমে যাবে। তাই অ্যাংলো ও হিন্দু পরিচালিত পত্রিকাগুলো বঙ্গভঙ্গের বিরোধী ছিল। উপর্যুক্ত শ্রেণির লোকেরা নিজেদের শ্রেণিস্বার্থ বজায় রাখার ও প্রাধান্য বজায় রাখার জন্যই বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে মুখর হয়ে ওঠে।
অবশেষে বঙ্গভঙ্গ রদ হয়। বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ায় কংগ্রেস নেতারা এবং হিন্দু সমাজ উল্লসিত হয়। মুসলমান সমাজ ব্যথিত হয়। খুব অল্প সময়ের মধ্যে নতুন প্রদেশে উন্নতি হয়েছিল। মুসলমানদের মধ্যে দ্রুত শিক্ষার প্রসার হচ্ছিল। পাঁচ বছরে মুসলমান ছাত্রসংখ্যা শতকরা ৩৫ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু সেই উন্নতির পথ বন্ধ হয়ে যায়। মুসলমানেরা নিরাশ হয়ে পড়ে এবং বৃটিশ সরকারের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলে। মাওলানা মোহাম্মদ আলী বলেন, ‘মুসলমানগণকে তাদের রাজভক্তির প্রতিদানে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে।’ বঙ্গভঙ্গ রদ করায় বেশি দুঃখ পান নবাব সলিমুল্লাহ। তিনি এত বেশি আঘাত পান যে, তার স্বাস্থ্য ভেঙে যায়, হতাশায় মন ভরে ওঠে। মনের দুঃখে তিনি রাজনীতি থেকে অবসর নেন। পূর্ব বাংলার মুসলমানদেরকে শান্ত করার জন্য বড়োলাট লর্ড হার্ডিঞ্জ ১৯১২ সালের ৩১শে জানুয়ারি ঢাকা আসেন। তিনি নবাব সলিমুল্লাহকে আশ্বাস দেন ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে। নবাব সলিমুল্লাহ ১৯১৫ সালের জানুয়ারি মাসে অকস্মাৎ মৃত্যুবরণ করেন। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। পরবর্তীকালে এই বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে বাংলার মুসলমান মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণির সৃষ্টি হয়। কিন্তু বঙ্গভঙ্গ রদ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে সরকারের বিশ্বাসঘাতকতায় তাদের মন থেকে ততদিনে বৃটিশপ্রীতি মুছে যায় এবং মুসলমানদের মধ্যে রাজনীতি চেতনাবোধ তৈরি হতে থাকে।নীলুফার ইয়াসমিন: লেখক, গবেষক ও শিক্ষক
 ঢাকা টাইমস অনলাইন এর সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিডটি ফলো করুন
ঢাকা টাইমস অনলাইন এর সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিডটি ফলো করুন
মন্তব্য করুন