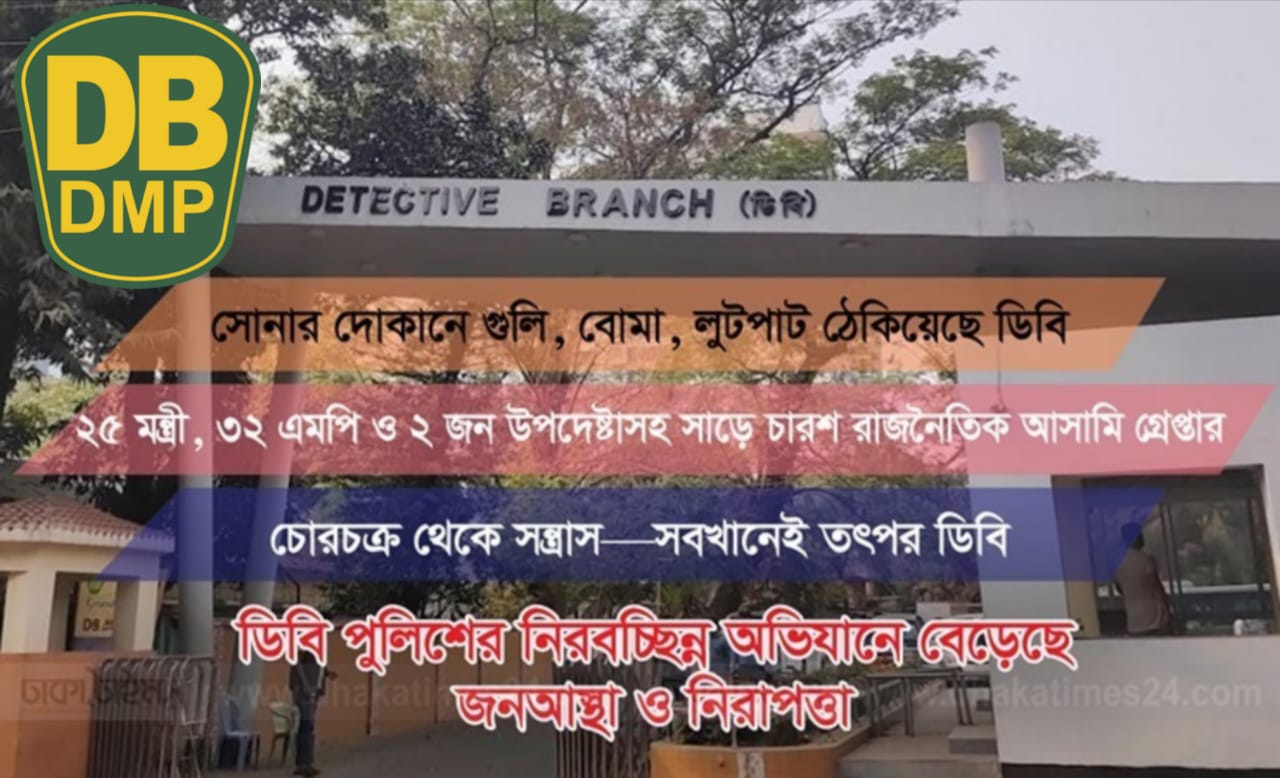নিজেকে জানা ও ভালো থাকার জন্য আবৃত্তি

আবৃত্তি শুধু প্রয়োগ শিল্প নয়, আবৃত্তি নিত্যজীবন মানোন্নয়নের সহজ বিধানও। আবৃত্তি সুস্থ সুন্দর জীবনের পথ দেখায়।
লালন সাঁইয়ের পদে আছে-
‘শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ, এই পঞ্চে হয় নিত্যানন্দ
যার অন্তরে সদা আনন্দ, নিরানন্দ জানে না সে।
প্রেম পাথারে যে সাঁতারে তার মরণের ভয় কী আছে।
স্বরূপ মরণে সদা মত্ত যারা ঐ কাজে।’
আবৃত্তি কী?
নিত্যসত্যকে বিশ্বাস ও প্রেম দিয়ে উচ্চারণই আবৃত্তি। রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শকে আমরা শব্দের মাধ্যমে বোধের কাছে নিয়ে যাই এবং অখণ্ড বোধকে উচ্চারণে সজীব করে তুললেই আবৃত্তি হয়। অতএব আবৃত্তি শুধু কণ্ঠ দিয়ে নয়, আমরা আবৃত্তি করি পঞ্চভূত ও পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে।
আবৃত্তি শব্দের গভীরে আছে একটি উপসর্গ, একটি ধাতু এবং একটি প্রত্যয়। ধাতু, শব্দ বা অব্যয়ের যেসব বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে, তাকে প্রত্যয় বলে।
ধাতুর পরে যে প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে তাকে বলে কৃৎ প্রত্যয়। যেমন: √ধর্+আ=ধরা, √ডুব্+উরি=ডুবুরি, √দৃশ্+য=দৃশ্য।
শব্দের পরে যে প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে তাকে তদ্ধিত প্রত্যয় যেমন: বাঘ+আ=বাঘা, সোনা+আলি =সোনালি, সপ্তাহ+ইক=সাপ্তাহিক।
আবৃত্তির গভীরে গিয়ে পাওয়া যায় আ+√বৃৎ+তি (ক্তি)=আবৃত্তি। আ, অর্থাৎ সম্যকভাবে, পরিপূর্ণভাবে, সর্বতোভাবে। √বৃৎ ধাতুর মূল অর্থ দাঁড়ায় বিদ্যমান। যা কিছু চিরন্তন, বিদ্যমান- যা নিত্যউচ্চারণীয়, যা বারবার উচ্চারণে আমাদের সকল ইন্দ্রিয় সজীব ও অনুভূতিপূর্ণ থাকে, যা উচ্চারণে শরীর ও মন থেকে সকল বিষ ঝরে গিয়ে অমৃত যুক্ত হয়- তাই আবৃত্তি। একটু সহজ করে বললে দাঁড়ায়- শব্দের রূপ-রস-গন্ধ ও স্পর্শকে বোধপ্রাঞ্জল সজীব উচ্চারণই আবৃত্তি।
নিত্য আবৃত্তি করলে আত্মপরিচয়ে অবিচল থাকা যায়। নিত্য আবৃত্তিতে আত্মোন্নয়ন হয়। আবৃত্তিকে সকলের সামনে নিয়ে এলে সর্বজনীন কল্যাণে নিজেকে যুক্ত করা যায়।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন- “আমি বেশ বুঝতে পারছি, আমি ক্রমশ আপনার মধ্যে আপনার একটা সামঞ্জস্য স্থাপন করতে পারব- আমার সুখ-দুঃখ, অন্তর-বাহির, বিশ্বাস-আচরণ, সমস্তটা মিলিয়ে জীবনটাকে একটা সমগ্রতা দিতে পারব। শাস্ত্রে যা লেখে তা সত্য কি মিথ্যা বলতে পারি নে; কিন্তু সে-সমস্ত সত্য অনেক সময় আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী, বস্তুত আমার পক্ষে তার অস্তিত্ব নেই বললেই হয়। আমার সমস্ত জীবন দিয়ে যে জিনিসটাকে সম্পূর্ণ আকারে গড়ে তুলতে পারব সেই আমার চরম-সত্য। জীবনের সমস্ত সুখ-দুঃখকে যখন বিচ্ছিন্ন ক্ষণিকভাবে অনুভব করি তখন আমাদের ভিতরকার এই অনন্ত সৃজনরহস্য ঠিক বুঝতে পারি নে- প্রত্যেক কথাটা বানান করে পড়তে হলে যেমন সমস্ত পদটার অর্থ এবং ভাবের ঐক্য বোঝা যায় না; কিন্তু নিজের ভিতরকার এই সৃজনশক্তির অখণ্ড ঐক্যসূত্র যখন একবার অনুভব করা যায় তখন এই সৃজ্যমান অনন্ত বিশ্বচরাচরের সঙ্গে নিজের যোগ উপলব্ধি করি; বুঝতে পারি- যেমন: গ্রহ-নক্ষত্র-চন্দ্রসূর্য জ্বলতে জ্বলতে ঘুরতে ঘুরতে চিরকাল ধরে তৈরি হয়ে উঠেছে, আমার ভিতরেও তেমনি অনাদিকাল ধরে একটা সৃজন চলছে; আমার সুখ-দুঃখ বাসনা-বেদনা তার মধ্যে আপনার-আপনার স্থান গ্রহণ করছে। এই থেকে কী হয়ে উঠবে জানি নে, কারণ আমরা একটি ধূলিকণাকেও জানি নে। কিন্তু নিজের প্রবহমান জীবনটাকে যখন নিজের বাইরে অনন্ত দেশকালের সঙ্গে যোগ করে দেখি তখন জীবনের সমস্ত দুঃখগুলিকেও একটা বৃহৎ আনন্দসূত্রের মধ্যে গ্রথিত দেখতে পাই- আমি আছি, আমি হচ্ছি, আমি চলছি, এটিকে একটা বিরাট ব্যাপার বলে বুঝতে পারি- আমি আছি এবং আমার সঙ্গে সঙ্গেই আর-সমস্তই আছে, আমাকে ছেড়ে এই অসীম জগতের একটি অণু-পরমাণুও থাকতে পারে না, আমার আত্মীয়দের সঙ্গে আমার যে যোগ, এই সুন্দর শরৎপ্রভাতের সঙ্গে তার চেয়ে কিছুমাত্র কম ঘনিষ্ঠ যোগ নয়- সেইজন্যই এই জ্যোতির্ময় শূন্য আমার অন্তরাত্মাকে তার নিজের মধ্যে এমন করে পরিব্যাপ্ত করে নেয়। নইলে সে কি আমার মনকে তিলমাত্র স্পর্শ করতে পারত? নইলে সে কি আমি সুন্দর বলে অনুভব করতেম? আমার সঙ্গে অনন্ত জগৎ-প্রাণের যে চিরকালের নিগূঢ় সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধের প্রত্যক্ষগম্য বিচিত্র ভাষা হচ্ছে বর্ণগন্ধগীত। চতুর্দিকে এই ভাষার অবিশ্রাম বিকাশ আমাদের মনকে লক্ষ্য-অলক্ষ্যভাবে ক্রমাগতই আন্দোলিত করছে, কথাবার্তা দিনরাত্রিই চলছে।
যে শক্তি আমার জীবনের সমস্ত সুখ-দুঃখকে সমস্ত ঘটনাকে ঐক্যদান তাৎপর্যদান করিতেছে, আমার রূপরূপান্তর জন্মজন্মান্তরকে একসূত্রে গাঁথিতেছে, যাহার মধ্য দিয়া বিশ্বচরাচরের মধ্যে ঐক্য অনুভব করিতেছি, তাহাকেই জীবনদেবতা নাম দিয়া লিখিয়াছিলাম-
‘ওহে অন্তরতম,
মিটেছে কি তব সকল তিয়াস
আসি অন্তরে মম?
দুঃখ-সুখের লক্ষ ধারায়
পাত্র ভরিয়া দিয়েছি তোমায়,
নিঠুর পীড়নে নিঙাড়ি বক্ষ
দলিতদ্রাক্ষা-সম।
কত যে বরন, কত যে গন্ধ,
কত যে রাগিণী, কত যে ছন্দ,
গাঁথিয়া গাঁথিয়া করেছি বয়ন
বাসরশয়ন তব..।’”
আবৃত্তি করার জন্য প্রথমত লাগে প্রাণ। প্রাণ মানে বায়ু। বায়ু গ্রহণ করার পর যদি বাক্প্রত্যঙ্গকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে সেই বায়ু ঠিক ঠিকভাবে মুখ থেকে বেরিয়ে আসে তাতেই আবৃত্তি প্রাণময় হয়। বায়ু বা বাতাস এবং আবৃত্তি একে অন্যের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। বায়ুর সঙ্গে আরও আছে ক্ষিতি-অপ-তেজ এবং ব্যোম। আবৃত্তির গভীরে যাবার আগে জানতে হবে পঞ্চমহাভূত।
পঞ্চমহাভূত:
ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম্
১. ক্ষিতি (ভূমি) :-মাটি থেকে- হাড়, মাংস, ত্বক, রগ, পশম।
২. অপ (জল) :- জল থেকে- শুক্র, রক্ত, মজ্জা, মল ও মুত্র।
৩. তেজ (অগ্নি) :- আগুন থেকে- ক্ষুধা-তৃষ্ণা, নিদ্রা, আলস্য, ভ্রান্তি।
৪. মরুৎ (বায়ু) :- বাতাস থেকে- ধারণ, চলন, সংকোচন, প্রসারণ, ক্ষেপণ।
৫. ব্যোম্ (আকাশ) :- আকাশ থেকে- কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, লজ্জা।
আবৃত্তির সঙ্গে ক্ষিতি-অপ-তেজ-মরুৎ-ব্যোম মিলে মিশে আছে এবং এর সঙ্গে আরও আছে ইন্দ্রিয় শক্তি। যে সকল অঙ্গ বা শক্তি দিয়ে পদার্থের বা বাহ্য বিষয়ের উপলব্ধি তথা জ্ঞান আসে এবং কর্ম করা যায় তাকে আমরা বলি ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয়কে মূল তিন ভাগে দেখতে পাই-
জ্ঞান: চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক
কর্ম: বাক্, হস্ত, পাদ, পায়ু, উপস্থ
অন্তর: চেতন, মন, বুদ্ধি, অহংকার, চিত্ত
পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়:
চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক
১. চক্ষু বা চোখ। চোখ দিয়ে সত্যকে দর্শন করা যায়।
২. কর্ণ বা কান। কান দিয়ে সত্যকে শ্রবণ করা যায়।
৩. নাসিকা বা নাক। নাক দিয়ে সত্যকে গ্রহণ করা যায়।
৩. জিহ্বা দিয়ে সত্যকে প্রকাশ করা যায়।
৫. ত্বক বা চামড়া। ত্বকের মাধ্যমে সত্যকে অনুভব করা যায়।
পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়:
বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ- এই পাঁচটি কর্ম আহরণকারী ইন্দ্রিয় বা কর্মেন্দ্রিয়।
১. বাক্ বা মুখ। বাকের মাধ্যমে খাবার গ্রহণ ও মনের ভাব প্রকাশ করা যায়, আদেশ নিষেধ ও উপদেশ করা যায়।
২. পাণি বা হাত। পাণি বা হাত দিয়ে কোনো কিছু ধারণ করা যায়। হাত দিয়ে খাদ্য গ্রহণসহ নিত্য কাজ করা যায়।
৩. পাদ বা পা। পা দিয়ে আমরা চলাচল করি।
৪. পায়ু বা মলদ্বার। প্রতিটি জীব মল ত্যাগকারী।
৫. উপস্থ বা মূত্রদ্বার। উপস্থ দ্বারা মৈথুন প্রশান্তি ও বংশবৃদ্ধি হয়।
অন্তরিন্দ্রিয়:
১. চেতন: অনুভূতিযুক্ত প্রাণযুক্ত [সং. √চিৎ+অন]। চেতন ক্রিয়াশীল অবস্থায় চেতনায় উন্নীত হয়।
২. চিত্ত: কেন্দ্রীভূত শুদ্ধ চেতনার সমষ্টি। প্রজ্ঞাযুক্ত চেতনা। লাভ, ক্ষতি, সুখ, দুখ, মান, অপমান, প্রশংসা, নিন্দা, জগতের মুখ্য চিত্ত আন্দোলক।
৩. বুদ্ধি: মস্তিষ্কের যুক্তিযুক্ত অংশ, বিচক্ষণতা, উদ্ভাবনী শুক্তি, নিরূপণ ও বিশ্লেষণ শক্তি, সত্য ও অসত্য নির্ণয়ের ক্ষমতা, মেধা।
৪. অহংকার: অহং, অহম্ [অহঙ্, অহম্] = আমি। আমিত্ব; অহংকার। আত্মচেতনা; অহংজ্ঞান। আমিত্বকে আবিষ্কার করে সুবুদ্ধি কিন্তু আমিত্বকে জাহির করে কুবুদ্ধি।
৫. মন: দেহ ও কর্মের সৃষ্টিকর্তা মন, মনের সৃষ্টিকর্তা মায়া। মন নানা প্রকার পদার্থের সংহতি। মন জড়বস্তুর উচ্চতম সৃষ্টি।
আবৃত্তি করলে আত্মোন্নয়ন হয়। আমরা মূলত কবিতা আবৃত্তি করি। কবিতার গভীরে থাকে শুদ্ধতম সত্যের উপলব্ধি। সত্যের গভীরে পৌঁছতে পারলেই আবৃত্তির সুফল পাওয়া যায়। আবৃত্তির আগে নিজেকে ভাবতে মানসিকভাবে প্রস্তুত করতে হয়। আর এই প্রস্তুতির জন্য চৌদ্দটি কাজ করা দরকার-
১. শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান না-হওয়া।
২. দম্ভ না-থাকা।
৩. অহিংসা অর্থাৎ শরীর, মন ও বাণীর দ্বারা কাউকে কখনও দুঃখ না-দেওয়া।
৪. অন্যকে ক্ষমা করার মানসিকতা।
৫. সরল শরীর, মন ও বাণী।
৬. জ্ঞান প্রাপ্তির উদ্দেশে গুরুর (জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ) কাছে গিয়ে তাঁর সেবা ও আজ্ঞাপালন করা।
৭. শরীর ও অন্তঃকরণের শুদ্ধি।
৮. নিজের লক্ষ্যে অবিচল থাকা।
৯. মনকে নিয়ন্ত্রণে রাখা।
১০. ইন্দ্রিয় বিষয়ে কোনো অনুরাগ না-থাকা।
১১. দুঃখের মূল কারণ সুখের ইচ্ছা থেকে মুক্ত হওয়া।
১২. আসক্তি ত্যাগ করা।
১৩. অনুকূলতা ও প্রতিকূলতার প্রতি অবিচল থাকা।
১৪. প্রতিদিন অন্তত একবার একলা সাধনা।
আবৃত্তির জন্য প্রাথমিক অনুশীলন:
আবৃত্তিকারে প্রস্তুতির জন্য স্বরধ্বনি-ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ ঠিক হতেই হবে। তাছাড়া উচ্চারণে অ কখন ও হয়, এ কখন এ্যা হয় এসব জানার জন্য বাংলা উচ্চারণের অন্তত ৬৯টি নিয়ম জানতে হয়। আবৃত্তির প্রাথমিক শিক্ষার্থীর কিছু জ্ঞান এবং ধারণা থাকা খুব জরুরি-
১ শুদ্ধ উচ্চারণ
২ বাক্যের সঠিক ভাগ
৩ মাত্রা, স্বর, স্বরশক্তি ও সময়জ্ঞান
৪ সুর ও স্বর সম্পর্কিত ধ্যান-ধরণা
৫ কণ্ঠস্বরের সঠিক ব্যবহার
৬ কণ্ঠের শ্রবণ উপযোগিতা
শুধু আবৃত্তিই নয়, গান, অভিনয়, উপস্থাপনাসহ কণ্ঠনির্ভর সব শিল্পের জন্যই কণ্ঠের সঠিক সাবলীল ব্যবহার করতে হলে থাকা চাই কণ্ঠের অনুশীলন। নিচের বিষয়গুলো সামনে রেখে শিক্ষার্থীরা অনুশীলন করলে দারুণ ফল পাবে।
শুদ্ধ উচ্চারণ:
যে-কোনো রচনা পাঠের প্রথম এবং প্রধান লক্ষ সুস্পষ্ট উচ্চারণ করে প্রত্যেকটি ধ্বনি আবেগময় কণ্ঠে শ্রোতার কানে পৌঁছে দেওয়া। তার জন্য চাই শুদ্ধ উচ্চারণ। শুদ্ধ উচ্চারণের মাধ্যমে একটি শব্দ তার প্রকৃত ধ্বনি ও অর্থের ব্যঞ্জনা লাভ করে। তাছাড়া অশুদ্ধ উচ্চারণ একটি শব্দের অর্থও পাল্টে দিতে পারে। শুদ্ধ উচ্চারণের জন্য বাক্যন্ত্রকে সচল ও জড়তামুক্ত রাখা দরকার। বারবার অনুশীলনের মাধ্যমে এবং সেই সঙ্গে জিভ এবং কানকে সচেষ্ট ও সজাগ রেখে সুস্পষ্ট উচ্চারণ করার ক্ষমতা অর্জন করতে হয়। উচ্চারণ সুস্পষ্ট হচ্ছে কি না তার বিচার করে কান।
স্পষ্ট উচ্চারণের জন্য আরও একটি সতর্কতা দরকার, বাক্যের শেষ পদ যেন কখনোই একেবারে নিচুস্বরে উচ্চারিত না হয়। বাক্যের শেষ শব্দটি সবসময়ই একটু ঝোঁক দিয়ে শেষ করতে হবে। উচ্চারণ যদি পরিষ্কার না হয় তাহলে আবৃত্তি শুনতে ভালো লাগে না। তাই ছোটোবেলা থেকেই স্পষ্ট উচ্চারণের অভ্যাস থাকা দরকার। যে-কোনো শব্দ উচ্চারণ করার আগে খেয়াল করতে হবে শব্দটি কটি ধ্বনি আছে। কোন্ ধ্বনি কতটুকু জোর দাবি করছে, সে অনুপাতে শব্দটি উচ্চারণ করতে হবে। যেমন-
‘যাত্রীরা রাত্তিরে হতে এল খেয়া পার
বজ্রেরি তূর্যে এ গর্জেছে কে আবার’
এবারে গুনে দেখো, প্রথম শব্দ যাত্রীরা- এতে কটি ধ্বনি আছে। আমরা এবার ভেঙে ভেঙে উচ্চারণ করি- যাতত্রিরা (যাত+ত্রি+রা)। বানানে আছে তিনটি বর্ণ আর উচ্চারণেও আছে তিনটি ধ্বনি। আমরা যদি এই শব্দটির ভুল উচ্চারণ করি তাহলে শব্দটি শুনতে লাগবে- যাতরিরা (যাত+রি+রা)। এখানে ত-এ র-ফলা (ত্র) উচ্চারণ করা হয়নি। খুব সতর্ক হয়ে প্রতিটি অক্ষরের উচ্চারণ ধরে ধরে করতে হবে।
সাধারণত আমরা যা বলি, তা লিখি না, যা লিখি, তা বলি না। মনে রাখতে হবে পৃথিবীর যে-কোনো ভাষার বানান আর উচ্চারণ এক হয় না। আমরা বানান লিখি স্মৃতি থেকে আর উচ্চারণ করি শুনে শুনে। বানানের সঙ্গে উচ্চারণে হুবহু মিল তেমন ঘটেই না। যেমন: অভিনয়। অভিনয়-এর অ-এর উচ্চারণ না করে আমরা ও-এর উচ্চারণ করি। তার কারণ আর কিছুই নয়। এর একটা কারণ আছে। শব্দের প্রথমে অ আছে, কিন্তু পরে আছে ‘ই'ধ্বনি- তাই উচ্চারণের সময় ওই অ ও হয়ে যাচ্ছে। একরকমভাবেই উচ্চারিত হচ্ছে- অতি=ওতি, যদি =যোদি, নদী=নোদী।
ঠিক একইভাবে শব্দের প্রথম অ-এর পরে যদি উ, ঊ, ঋ, ক্ষ, য-ফলা (য্য ) থাকে এবং শব্দটি যদি না-বোধক না হয় তাহলে সেসব শব্দের প্রথম অ ও হয়ে যাবে। যেমন- কভু=কোভু, বধূ=বোধু, মসৃণ=মোসসৃন, কক্ষ=কোকখো, অন্য=ওন্নো ইত্যাদি।
এই যে ই আর উ, অ-কে ও করে দিচ্ছে- এটা ঘটছে কীভাবে? অ- বলে পরক্ষণেই ই বা উ বলতে হলে জিভকে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় এগিয়ে-পিছিয়ে যেতে হয়- জিভ এই পরিশ্রমটা করতে চায় না, তাই পরে ই বা উ উচ্চারণ করতে হবে এটা সে যেই জানতে পারে অমনি সে চেষ্টা করা অ-টাকে ও-এর কাছাকাছি নিয়ে যাবার। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে না-বোধক শব্দে এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। যেমন- অসীম, অরূপ, অতুলনীয়, অক্ষত, অন্যায় ইত্যাদি।
উচ্চারণের অনেক অনেক নিয়ম রয়েছে। সেসব নিয়ম জেনে ছোটোদের পক্ষে উচ্চারণ শেখা বেশ কঠিন। আমরা আপাতত বিশেষ কোনো শব্দের সঠিক উচ্চারণ জানার জন্য বড়োদের সাহায্য চাইব। তাছাড়া এই লেখায় বেশকিছু শব্দের সঠিক উচ্চারণের তালিকা দেওয়া হয়েছে।
বাক্যের সঠিক ভাগ:
আমরা কথা বলার সময় একটি বাক্যকে কেটে-কেটে উচ্চারণ করি। একেবারে অনেক বাক্যই বলা সম্ভব নয়। যেমন-
‘খাঁচার পাখি ছিল সোনার খাঁচাটিতে
বনের পাখি ছিল বনে’
এই বাক্য দুটি একবারে উচ্চারণ করা বেশ কঠিন, আবার অর্থ প্রকাশের জন্যও তা জটিল। তাই আমরা একেকটি বাক্যকে-পঙ্ক্তিকে কয়েক ভাগে ভাগ করে উচ্চারণ করি। আবার বাক্যকে কোথায় কোথায় ভেঙে অর্থপূর্ণ করে আবৃত্তি করা সম্ভব সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে। যেমন-
‘খাঁচার পাখি / ছিল সোনার খাঁচাটিতে
বনের পাখি / ছিল বনে’
বাক্য ভেঙে উচ্চারণের ফলে উচ্চারণ জড়িয়ে যায় না। আবৃত্তিও হয়ে ওঠে শ্রুতিমধুর।
মাত্রা, স্বর, স্বরশক্তি ও সময়জ্ঞান:
আমাদের মুখ বিবরের নিচে থাকে স্বরযন্ত্র। আমাদের স্বর উৎপাদনের শ্বাসনালীতে থাকে স্বরতন্ত্রী। এর আকৃতি অনেকটা উল্টো ভি-এর মতো। ভি-এর কালো রেখা দুটিই স্বরতন্ত্রী। বুকের ভেতর থেকে বাতাস টেনে স্বরতন্ত্রীকে কাঁপাতে দরকার শক্তির। আর এই শক্তি হচ্ছে বাতাস। আমাদের ফুসফুসে ধরে রাখা বাতাস এসে আঘাত করে স্বরতন্ত্রীকে। এর থেকেই ধ্বনির সৃষ্টি। কিন্তু একটা ব্যাপার ছেলে আর মেয়েদের স্বরতন্ত্রীর মধ্যে সামান্য পার্থক্য আছে। ছেলেদের স্বরতন্ত্রী লম্বায় বড়ো হয়। ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের স্বরতন্ত্রী সবসময়েই ছোটো হয়। তাছাড়া ছেলেদের স্বরতন্ত্রী মেয়েদের স্বরতন্ত্রীর চেয়ে একটু কম পুরু হয়। লম্বা ও চওড়ার এই পার্থক্য থেকেই ছেলে-মেয়ের স্বরের তারতম্য ঘটে। এছাড়া আরো একটি কারণ হচ্ছে, টেস্টোস্টোরেন নামে একরকম হরমোন ছেলেদের কণ্ঠস্বরকে পালটে দেয়। কিন্তু এই হরমোন মেয়েদের শরীরে তৈরি হয় না বলে তাদের কণ্ঠস্বর প্রায় একই থেকে যায়।
আবৃত্তির সময় স্বরতন্ত্রী কেঁপে ওঠে। কাঁপানোর সময় স্বরতন্ত্রী সংকুচিত হলে এবং উঁচু পর্দার স্বর প্রসারিত হলে নিচু পর্দার স্বর সৃষ্টি হয়। অনুশীলনের সময় কবিতাটি যখন আবৃত্তি করা হবে বা যিনি শেখাবেন তাঁর স্বরের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। আবৃত্তিতে কোন কথাটার উপর তিনি জোর দিচ্ছেন, একটা কথা বা বাক্যের উপর তিনি কতক্ষণ থামছেন সেই সময়জ্ঞান অবশ্যই থাকা দরকার। তা না হলে- আবৃত্তি খুব দ্রুত করলে, আবার খুব ধীরে করলেও শ্রোতার পক্ষে কবিতার আবেদন পৌঁছানো খুব কঠিন।
সুর ও স্বর সম্পর্কিত ধ্যান-ধারণা:
কণ্ঠের উঁচু বা নিচু গতির একটা বৈশিষ্ট্য আছে। একেই বলা হয় সুর। আবৃত্তিতে স্বর নিয়ন্ত্রণের সময় এই সুরও নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। আবৃত্তির সুর হবে আবেগময় আর স্বর হবে স্বাভাবিক। গলার স্বর শুধু শুধু ওপরে নিলে চলবে না, আবার গলাটা শুধু নিচের দিকে রাখলেও আবৃত্তির শ্রুতিগ্রাহ্যতা নষ্ট হবে। কবিতার ভাব ও রস বুঝে গলার স্বরের অবস্থান ঠিক করতে হবে।
কণ্ঠস্বরের সঠিক ব্যবহার:
আবৃত্তি করার সময় কণ্ঠস্বরের সঠিক ব্যবহার অবশ্যই করতে হবে। যেমন স্বরের উত্থান, পতন এবং কম্পন বা দোলন ইত্যাদির সঠিক ব্যবহার খুব জরুরি।
মনে করো, / যেন বিদেশ / ঘুরে (স্বাভাবিক স্বর)
মাকে নিয়ে / যাচ্ছি অনেক / দূরে। (স্বাভাবিক স্বর)
এমন সময় / হারে রে রে / রে রে' (উঁচু স্বর)
ওই-যে কারা / আসতেছে ডাক / ছেড়ে! (উঁচু স্বর)
কণ্ঠের শ্রবণ উপযোগিতা:
আবৃত্তিকে শ্রবণ উপযোগী করে তুলতে হলে নিচু গলায় করলে চলবে না। কণ্ঠকে প্রয়োজনমতো উচ্চাগ্রামে তুলে শ্রোতার কানে পৌঁছে দিতে হবে। আবার কণ্ঠকে ওপরে তুলতে গিয়ে যেন চিৎকার-চেঁচামেচির মতো না শোনায় সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে, না হলে আবৃত্তি মোটেই শ্রুতিমধুর হবে না।
সঠিক উচ্চারণের জন্য ব্যায়াম:
বাক্যন্ত্রের যে-কোনো অংশ দুর্বল হলে স্পষ্ট উচ্চারণ করা সম্ভব হয় না। গলা, নাক, জিহ্বা, ঠোট, দাঁত, চোয়াল ও তালু- এই সাতটি হচ্ছে বাক্যন্ত্র বা কথা বলার যন্ত্র। স্পষ্ট উচ্চারণের জন্য বাক্যন্ত্রকে কার্যক্ষম করে তুলতে হবে। স্বরোৎপাদন করে বাক্যন্ত্র এবং ফুসফুস। ফুসফুসে প্রচুর বাতাস বোঝাই করা হয়। এই বাতাস হচ্ছে উচ্চারণের মূল। এই বাতাস স্বরযন্ত্রের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গিয়ে বাঁশির মতো স্বরোৎপাদন করে।
শিথিলকরণ:
অনেকটা যোগ-ব্যায়ামের ধ্যানাসনের মতো। এই আসন করা-কালীন আসনকারীর কোমর থেকে দেহের নিম্নভাগ পদ্মের আকৃতি নেয়, এজন্য একে পদ্মাসন বলা হয়।
প্রথমে দুটো পা সামনে ছড়িয়ে বসতে হবে। ডান পায়ের হাঁটু থেকে মুড়ে বাম ঊরুদেশে রাখতে হবে। বিপরীতভাবে বাম পা হাঁটু থেকে মুড়ে ডান ঊরুর ওপরে রাখতে হবে। এই সময় কোমর থেকে মাথা পর্যন্ত সোজা ও এক সরলরেখায় থাকবে। এবার দুটি হাত সোজা অবস্থায় হাঁটুর কাছে রাখতে হবে। চোখ থাকবে বন্ধ ও শ্বাস-প্রশ্বাস থাকবে স্বাভাবিক। এই অবস্থায় এক মিনিট থাকতে হবে। এই ব্যায়ামের ফলে মনের একাগ্রতা, ম্মৃতিশক্তি বাড়ে এবং সেই সঙ্গে স্নায়ুগুলোকে শিথিল হতেও সাহায্য করে।
সিংহাসন:
এই আসন করার সময় অভ্যাসকারীর দেহাকৃতি সিংহের মতো দেখায় বলে একে সিংহাসন বলা হয়। প্রথমে হাঁটু দুটি দুপাশে সরাতে হবে। যতক্ষণ ঊরুর সন্ধিস্থলে অর্থাৎ কুচকিতে বেশ চাপ পড়ে, ততক্ষণ সরাতে হবে। এবার পায়ের গোড়ালি সরিয়ে নিতম্ব মাটিতে রেখে দুটি পায়ের বুড়ো আঙুল পরস্পর যুক্ত করে দিতে হবে। এবার সাধ্যমতো দুটি চোয়াল ফাঁক করে এবং জিহ্বা সাধ্যমতো মুখ থেকে বের করতে হবে। নাকের ডগায় দৃষ্টি রাখতে হবে। এবার দুটি হাত হাঁটু বা জানুর ওপর রাখতে হবে। এ সময় মেরুদণ্ড সোজা থাকবে। এভাবে স্থিত হয়ে নাক দিয়ে শ্বাসগ্রহণ করতে হবে সাধ্যমতো ১৫-১৬ সেকেন্ড ধরে মুখ দিয়ে শব্দ সহকারে শ্বাস ছাড়ো। দম ছাড়ার সময় যেন স্বরতন্ত্রী কাঁপে, সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। আবার নাক দিয়ে শ্বাস নিয়ে ফুসফুস ভর্তি করে কিছুক্ষণ পর আবার মুখ দিয়ে ছাড়তে হবে। এভাবে ৫-৬ বার অভ্যাস করতে হবে। এই ব্যায়ামের ফলে গলার সমস্ত পেশী সবল হয়। কণ্ঠস্বরও মধুর হয়। টনসিলের দোষত্রুটিও দূর করে।
শ্বাসপ্রশ্বাসের জন্য ব্যায়াম:
শ্বাসের প্রধান যন্ত্রের নাম ফুসফুস। আমাদের বুকের দু'পাশে দুটো ফুসফুস আছে। বুক ও পেটকে আলাদা করার জন্য পেশী দিয়ে ঘেরা ডায়াফ্রাম বলে একটি পর্দা আছে। আমাদের ফুসফুস দুটি গলার হাড় থেকে ওই ডায়াফ্রাম পর্যন্ত চলে গেছে। আমরা যখন স্বাভাবিকভাবে শ্বাসকার্য চালাই তখন ফুসফুসের কর্মক্ষমতার অর্ধেকেরও কম অংশ ব্যবহৃত হয়। এ কারণেই আমাদের ফুসফুসের একটা বড়ো অংশ সারা জীবনই নিষ্ক্রিয় থেকে যায়। ফলে অধিকাংশ মানুষই ডায়াফ্রাম ও ফুসফুসের পূর্ণক্ষমতা ব্যবহার করার পরিবর্তে ফুসফুসের শুধু ওপরের অংশের সাহায্যে শ্বাস নেয় ও ছাড়ে।
গভীর করে শ্বাসপ্রশ্বাস নিলে ফুসফুসের সমস্ত অংশকেই সক্রিয় করে তোলা যায়। এই ব্যায়ামটি আয়ত্ত করতে পারলে উচ্চারিত প্রতিটি শব্দকে ইচ্ছেমতো নিয়ন্ত্রণ করা যায়; আর সবাইকে খুব সহজে শোনানোও যায়।
মেরুদণ্ড সোজা রেখে দাঁড়াতে হবে। এরপর হাত দুটো পেটের উপর এমনভাবে রাখতে হবে যাতে দুহাতের আঙুলের মাথাগুলো ছুঁয়ে যাওয়ার অবস্থায় থাকে। এবার ধীরে ধীরে গভীরভাবে শ্বাসগ্রহণ করতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব ততক্ষণ শ্বাস গ্রহণ করতে হবে। এই সময় পেটটা ফুলে উঠবে আর দু'হাতের আঙুলগুলো একে অপর থেকে কিছুটা দূরে সরে যাবে।
এবার হাত দুটো দিয়ে পেটের উপর চাপ দিতে হবে আর বাতাস ধীরে ধীরে মুখ দিয়ে বার করে দিতে হবে। পেটটা আবার আগের অবস্থায় ফিরে আসবে এবং আঙুলগুলো আবার পরস্পরকে ছোঁয়ার অবস্থায় চলে আসবে।
এভাবে বেশ কিছুদিন অভ্যাস করার পর ফুসফুসের তলদেশ ঘন চাপের সাহায্য নিয়ে কোনো শব্দ উচ্চারণ করার চেষ্টা করতে হবে। এই ব্যায়ামটি আয়ত্ত করতে পারলে উচ্চারণশক্তি বেড়ে যাবে, উচ্চারণের শ্রুতিগ্রাহ্যতা বাড়বে, স্বরগ্রামের গভীরতাও বেড়ে যাবে আর কণ্ঠে সুর তৈরিতেও দারুণ কাজ দেবে।
 ঢাকা টাইমস অনলাইন এর সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিডটি ফলো করুন
ঢাকা টাইমস অনলাইন এর সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিডটি ফলো করুন
মন্তব্য করুন