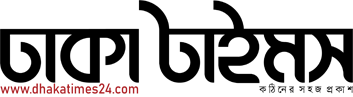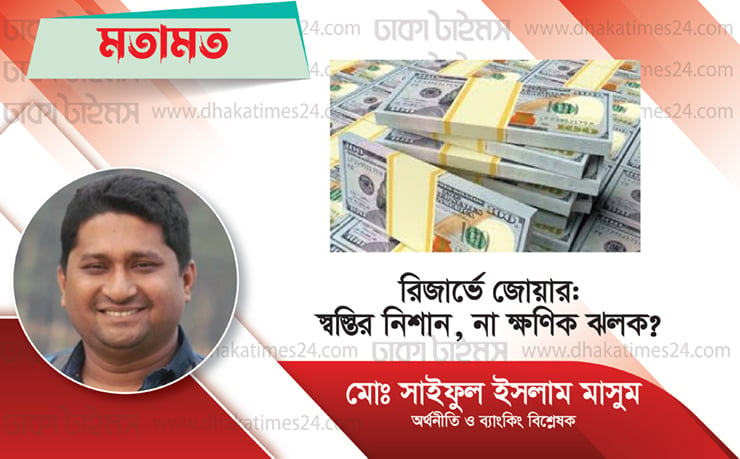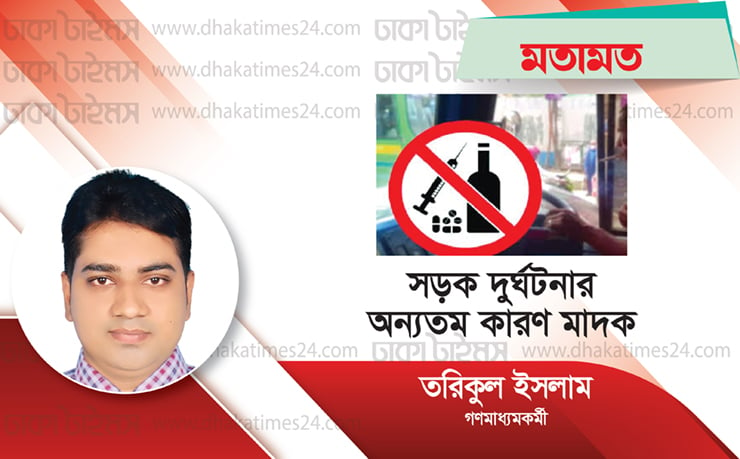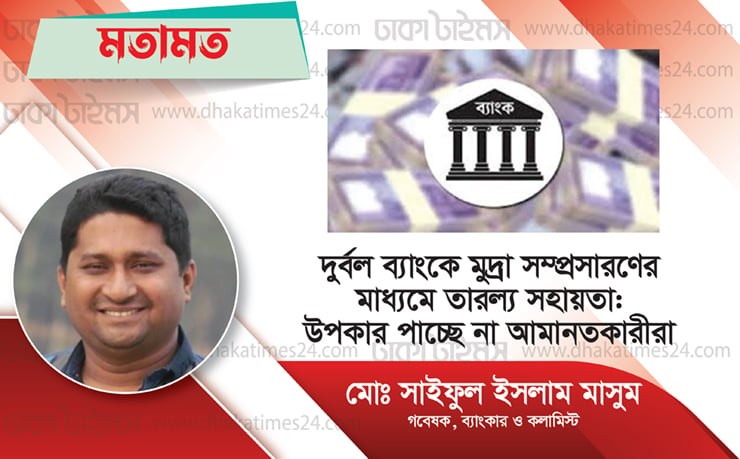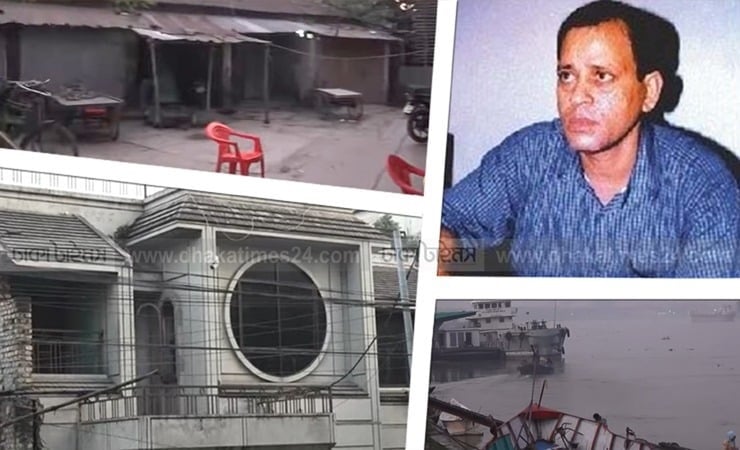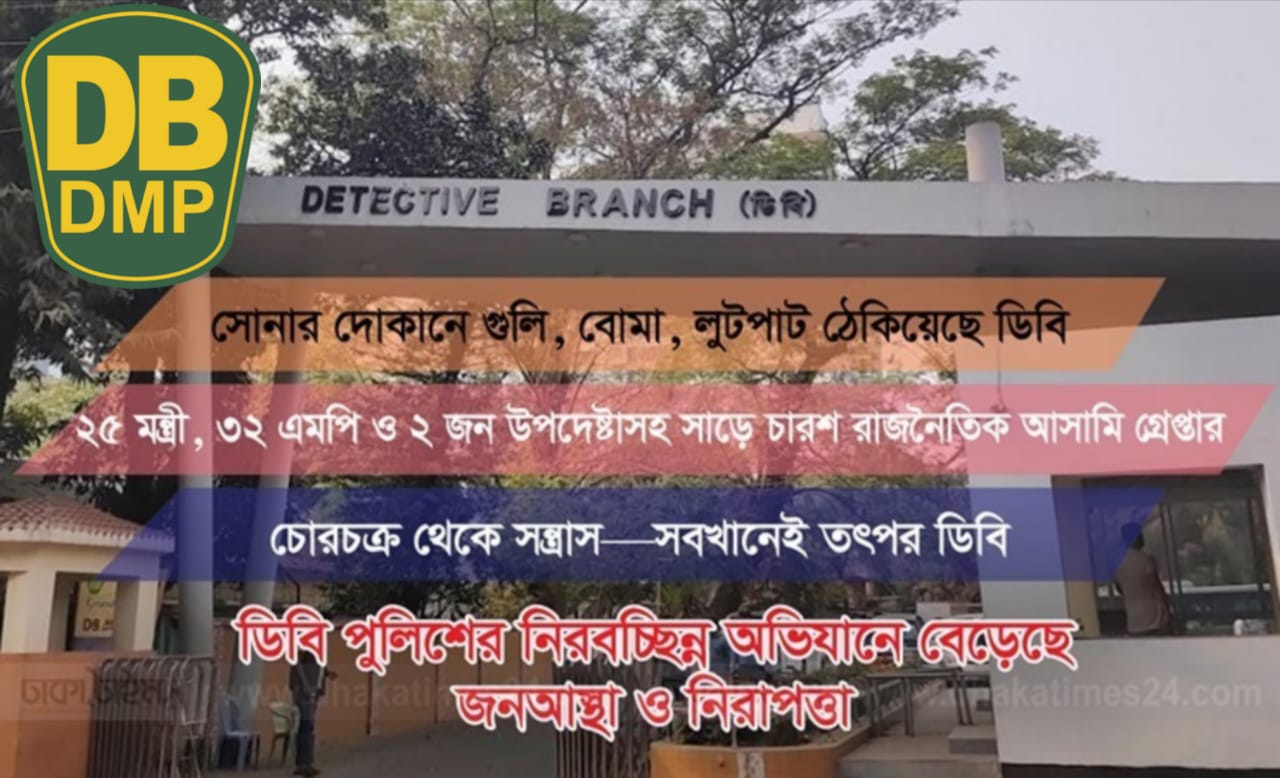আনন্দবাদী রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন
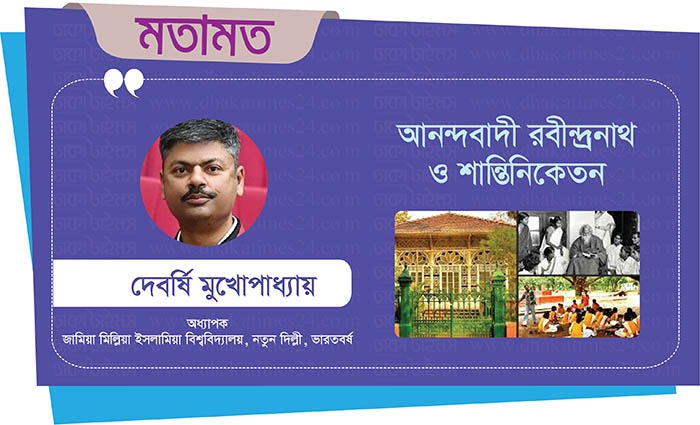
আজকাল গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিয়ে লিখতে গেলে অনেক রকম ভাবনা-চিন্তার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। আলোচনা এবং প্রশংসার মাঝের ফাঁকটি যেন সর্বদা বজায় থাকে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়। তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান, লেখার পরিপার্শ্ব অথবা ভাবনার সমকালীনতা যেন কোনো অনুচ্ছেদেই নিপাট নিটোল এক আনন্দবাদী কবিমনকে স্বাভাবিক প্রকাশ ও তাঁর বিশ্লেষণকে মেঘাচ্ছন্ন করে না ফেলে সেদিকে এক সর্বান্তঃকরণ প্রচেষ্টা থাকবে। গুরুদেবের ১৬৩তম জন্মদিবস উপলক্ষে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত নানা ভাবের ও স্বাদের লেখা পড়তে পড়তে মনে হলো, অসংখ্য কাজের মধ্যে অনন্ত ছুটি নিয়ে বসে থাকা, এক পাহাড় শোকের আবহে অসীম আনন্দের সীমানায় বাস করা এই মানুষটির অন্তস্থলে এখনো কিছু বিশ্ব মানবতার আশীর্বাণী লুকিয়ে আছে যা আমাদের জীবনের পাথেয় হয়ে উঠতে পারে এবং সে জন্যেই হয়তো রবীন্দ্রনাথ আজও সমকালীন।
সালটা ছিল ১৯০৭, সদ্য আদরের শমী, শমীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে কঠিন কলেরায় হারিয়েছেন কবি। সন্তানের মৃত্যু পিতার কাছে শক্তিশেল সম। দুঃখ সাগরের পাড়ে বসে কবি শোনালেন আশার বাণী, তিনি লিখলেন- “আজ জ্যোৎস্না রাত্রে সবাই গেছে বনে,
বসন্তের এই মাতাল সমীরণে।
আমার এ ঘর বহু যতন করে
ধুতে হবে, মুছতে হবে মোরে।
আমারে যে জাগতে হবে,
কী জানি সে আসবে কবে
যদি আমায়, যদি আমায় পড়ে তাহার মনে
বসন্তের এই মাতাল সমীরণে।”
পুত্রশোকের আবহের মধ্যে থেকেও ঝরনার উদ্দাম বারিধারার মতো কবিও তাঁর পিতৃসত্তাকে অর্গল মুক্ত হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন। তাঁর লেখার ছত্রে ছত্রে ফুটে ওঠে আনন্দের কথা, নিকষ কালো গুহার অন্তহীন শোকের আঁধারও যেন পায় আনন্দের অভ্যাস, বসন্তরাগে মুহূর্তে প্রাণ ফিরে পায় মানবজীবন। বিশ্বভারতীর প্রাক্তনী হওয়ার সুবাদে রবীন্দ্র আবহে বেড়ে ওঠার, শান্তিনিকেতনের মুক্ত বাতাসে শ্বাস নেওয়ার এবং রবীন্দ্রচিন্তায় দীক্ষিত হওয়ার এক অনন্য সুযোগ পেয়েছি। সেই ভারহীন এক আনন্দমুখর ছেলেবেলা আজও আমাদের পিছন ফিরে ডাকে। ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁর প্রিয় রবির মধ্যে রোপণ করেছিলেন অবয়বহীন পরমাত্মার পূজার বীজমন্ত্র। আত্মা অবিনশ্বর এবং ঈশ্বর একবেমদ্বিতীয়াম (এক এবং অদ্বিতীয়)। কিন্তু মৃত্যু? আমরা সামাজিক জীব। মৃত্যু কি আমাদের বেদনা দেয় না? হতাশ করে না? হতোদ্যম হয়ে মানুষ ভাঙা মনে দিকশূন্যপুরের দিকে হাঁটা দেয় না? জীবনের কৃতিত্ব কিন্তু সাধারণ থেকে অসাধারণত্বের দিকে চলতে শেখা। আর যখন কবি লেখেন,
“আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহদহন লাগে,
তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে।”
এক শীর্ণতোয়া নদীর মতো এক শিরশিরে প্রশান্তির গভীর আভাস মনের গহিনে অনুধাবন করি। পাঠভবনে পড়াকালীন দেখতাম যেকোনো শোকসভায় কবির লেখা একটি বিশেষ গান গাওয়া হতো,
“তোমার অসীমে, প্রাণ মন লয়ে, যত দূরে আমি ধাই”। সেই সমস্ত শব্দের মানে বোঝার ক্ষমতা তখন ছিল না, আর এখন যখন কিছুটা হলেও বুঝতে পারি তখন মনে হয় এই মানুষটির মনের ব্যাপ্তি কতটা বিশাল হলে মৃত্যুর মধ্যেও আনন্দকে খুঁজে নিতে পারে।
এবার কিছুটা বিষয়ান্তরে যাওয়া যাক। আজ যখন রবীন্দ্রনাথের আনন্দসত্তার আলোচনায় বসেছি, তখন তাঁর শিক্ষা ভাবনার বিষয়ে একটু আলোকপাত না করলে আলোচনাটি সম্পূর্ণ হবে না। শিশুরা প্রকৃতির কোলে বেড়ে উঠবে, শিক্ষা যেন স্মরণশক্তির পরীক্ষায় পর্যবসিত না হয় আবার শিক্ষার ব্যবহারিক আঙ্গিকটি যেন ছেলেমেয়েদের নাগালের বাইরে না থেকে যায় সেদিকে কবির প্রখর দৃষ্টি ছিল। অথচ সেই সময় উপযুক্ত বই ছিল অমিল, বাংলা ভাষায় তো আরোই নেই। রচিত হলো বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয়ের পর, আরেকটি সার্থক শিশুপাঠ্য সহজ পাঠ। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এই দুটি বইয়ের অবদান অনস্বীকার্য। বাংলা মাধ্যমে পড়াশোনা করা ছাত্রছাত্রীদের কাছে “জল পড়ে, পাতা নড়ে” দিয়ে শুরু করে “তাল গাছ এক পায়ে দাঁড়িয়ে, সব গাছ ছাড়িয়ে” এবং আরো পরে “কুমোর পাড়ার গরুর গাড়ি” এই ছড়া এবং কবিতাগুলো এক শ্রুতিমধুর পরিপার্শ্ব তৈরি করতো, আজকের তথ্যপ্রযুক্তির যুগে তথ্যমূলক সামাজিক বীক্ষণ হয়তো আমাদের সাধারণ জ্ঞান বাড়াতে সাহায্য করে কিন্তু অন্তর্লীন আনন্দের প্রতিভাস হয়ে উঠতে পারে কি? আজকের এই বিশেষ দিনটিতে এই প্রশ্নের উত্থাপন মনে হয় যথার্থ। এই আনন্দমুখর আবহই শান্তিনিকেতনের শিক্ষাব্যবস্থাকে স্বতন্ত্র করে তুলেছিল যার দ্যোতক ছিলেন স্বয়ং কবিগুরু। আজ যখন বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের আনন্দহীন লেখাপড়ার দুর্নিবার ঘূর্ণিপাকে পাক খেতে দেখি, বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় সাময়িক ব্যর্থতা জীবনের পরীক্ষায় ভেঙে পড়তে দেখি, পারিপার্শ্বিকের চাপে মন খারাপের শিকার হতে দেখি, কেউ কেউ যখন ভয়ংকর পরিণতির রাস্তা বেছে নেয়, মনে হয় আমরা কি ঠিক এই ব্যবস্থাটাই চেয়েছিলাম? গুরুদেব লিখেছিলেন, “আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে, নইলে মোরা রাজার সনে মিলবো কি সত্ত্বে?”। কত সোজা কথা কিন্তু গভীরতায় অন্তহীন। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে এক বিজয়ী সত্তা থাকে যাকে আমরা সযত্নে লালন করি আগামীর জন্যে, সেই আত্মবিশ্বাস থেকে ব্যক্তির তথা জাতির চরিত্র গঠন হয়।
রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনের আলোকচ্ছটায় আরো একটি বিশেষ ঘটনা হয়তো আমাদের নজর এড়িয়ে যাচ্ছে। ১৯২২ সালে কবি যে শান্তিনিকেতনের অদূরে সুরুলে পল্লী পুনর্গঠনের কাজ শুরু করেছিলেন আজ তার শতবর্ষ পূর্ণ হলো। পল্লী চর্চার ব্যবহারিক দিকটি কবিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল এবং সেই উদ্দেশ্যে শান্তিনিকেতনের পাশাপাশি তৈরি করেন শ্রীনিকেতন যা কি না পল্লীশিক্ষায় নিয়োজিত থেকে প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করে কৃষি ও বিভিন্ন হাতে-কলমে শিক্ষার মাধ্যমে গ্রামীণ জনজীবনকে স্বনির্ভর হওয়ার শিক্ষা প্রদান করবে। পুঁথিগত ও প্রথাগত শিক্ষার বাইরে বেরিয়ে, একমাত্রিক পরীক্ষা নির্ভর প্রস্তুতির বাইরেও যে একটা আনন্দমুখর, প্রকৃতির সান্নিধ্যে বেড়ে ওঠা বহুমাত্রিক শিক্ষার জীবনশৈলী আছে, সেই অমোঘ সত্যটি আজ মনে হয় ব্যবহারে আনার প্রয়োজন।
গুরুদেবের জন্মদিবস উপলক্ষে এই বিশেষ দিনটিতে শুধু তাঁর গান, কবিতা অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে তাঁকে স্মরণ না করে বরং তাঁর চিন্তা ও আদর্শকে নিজের ভিতরে ও পরিপার্শ্বে সঞ্চারিত করাই হয়তো তাঁর জন্মদিনের আমাদের শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধার্ঘ্য।
লেখক: অধ্যাপক, জামিয়া মিল্লিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, নতুন দিল্লি, ভারতবর্ষ
 ঢাকা টাইমস অনলাইন এর সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিডটি ফলো করুন
ঢাকা টাইমস অনলাইন এর সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিডটি ফলো করুন
মন্তব্য করুন