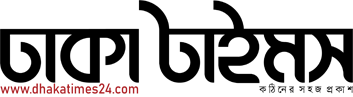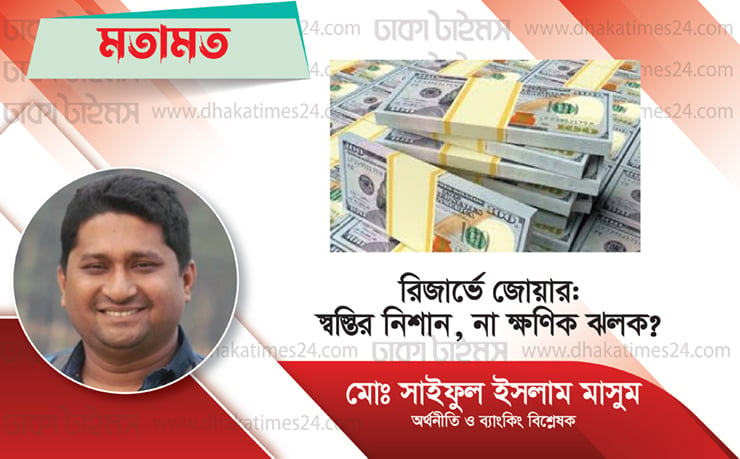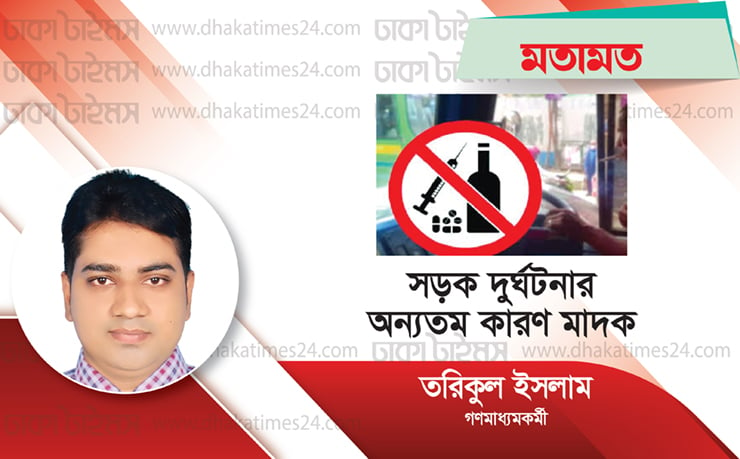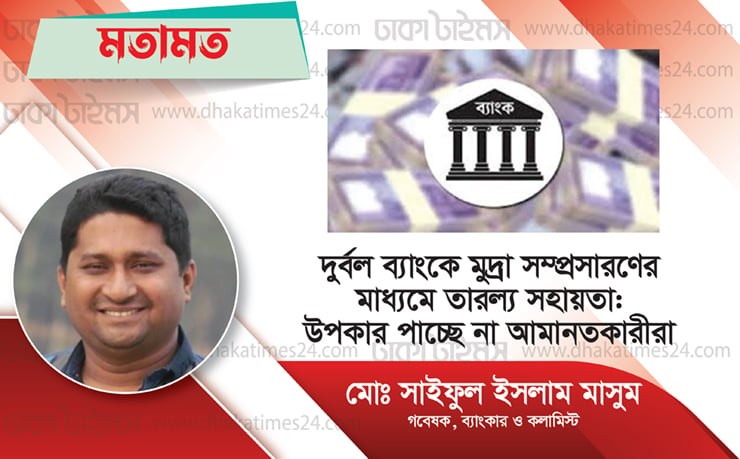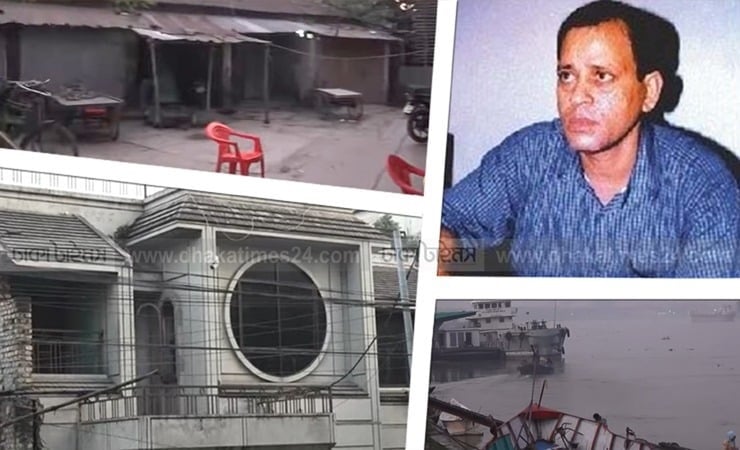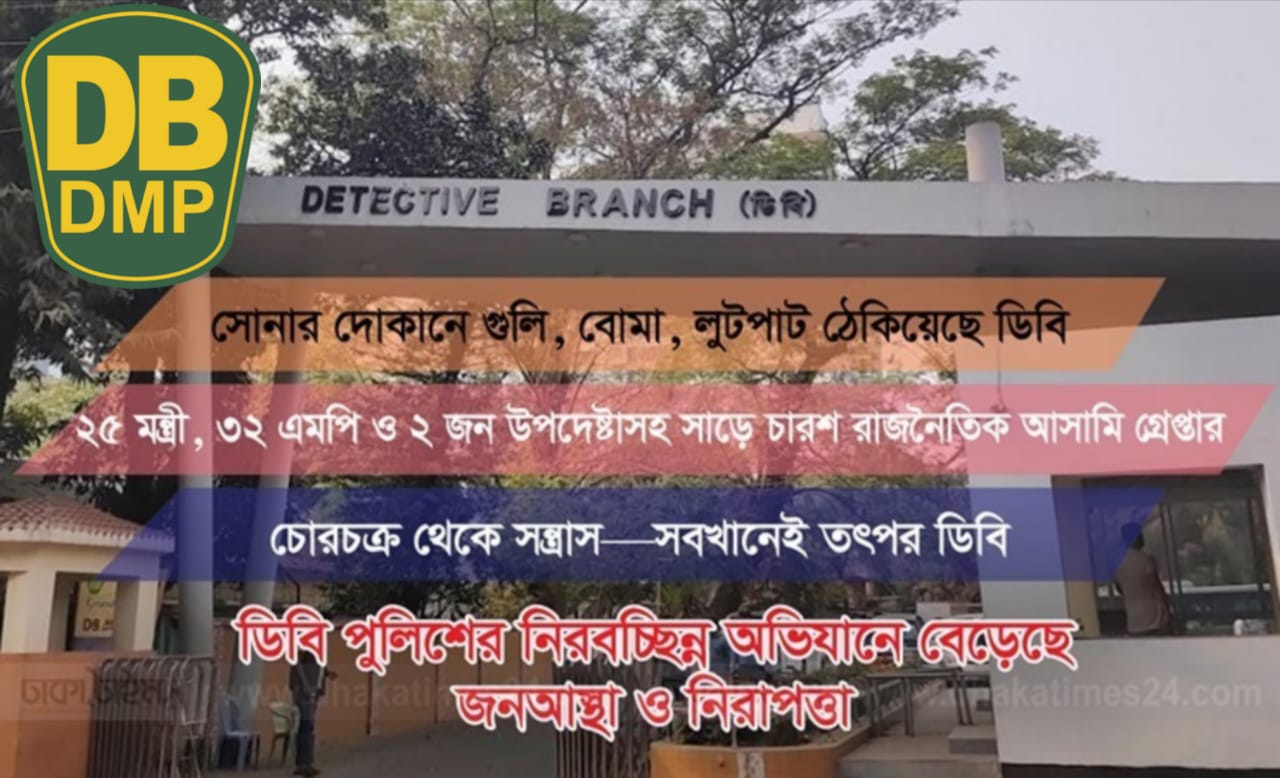জাতীয় আয় কই যায়?

৩০ জুন জাতীয় সংসদে পাস হয়ে গেল ২০১৯-২০ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট। সংসদে এবারের পাস করা জাতীয় বাজেটটি দেশের ইতিহাসে একটি বড় আকারের বাজেট। মুদ্রাস্ফীতি এবং ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার কারণে বাজেটের আকার বড় হওয়াটাই স্বাভাবিক। এই বাজেটে জিডিপির প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে আট শতাংশের উপরে। এই লক্ষ্যমাত্রা পূরণ না হলেও কমপক্ষে জিডিপির গ্রোথ ৭.৫ শতাংশ তো হবেই। বাজেটে অনুসারে দেখা যায় মূল্যস্ফীতি হওয়ার সম্ভাবনা ৫-৬ শতাংশ। আর এধরনের মূল্যস্ফীতিটা একটা স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার মধ্যেই পড়ে। দেশের মাথা পিছু আয় ১৯০৯ ডলার । যা টাকার অংকে দাঁড়ায় এক লাখ ৫২ হাজার ৭২০ টাকা। অর্থ্যাৎ প্রতি মাসে মাথা পিছু আয় ১২ হাজার ৭২৭ টাকা। সেই হিসেবে দেশ মধ্যম আয়ের দেশ হওয়ার পথে ধাবিত।
দেশের সার্বিক মূল্যস্ফীতির পর্যবেক্ষণ করলে নানা প্রশ্ন আসে। তবে মূল্যস্ফীতির বিষয়টি নিরীক্ষণ করলে দেখা যায়, গত বিশ বছরে যে যে দ্রব্য বা সেবার ক্ষেত্রে মূল্যস্ফীতি ঘটেছে তা হলো, পরিবহন ভাড়া, চিকিৎসা ব্যয়, শিক্ষা, কৃষি পণ্য উৎপাদনের উপকরণ, বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি প্রভৃতির ক্ষেত্রে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, রেলের বা বাসের ভাড়া গত বিশ বছরে বেড়েছে ১০০ শতাংশেরও বেশি। অপর দিকে গত বিশ বছরে কৃষি উৎপাদনের উপকরণের দাম বাড়লেও বাড়েনি কৃষির উৎপাদিত পণ্যের মূল্য। গত বিশ বছর আগেও ধানের দাম ৬০০-৬৫০ টাকা বর্তমানেও ধানের দাম (গ্রামের হাটে) একই। ২০ বছর আগে কৃষক পর্যায়ে এক কেজি শসার মূল্য ছিল ৬-৮ টাকা বর্তমানেও তাই (কৃষক পর্যায়ে)। এক কেজি কাচা মরিচ ৪০-৬০ টাকা এখনো তাই।
কৃষক পর্যায়ে কৃষক তার উৎপাদিত পণ্যের বিক্রির ক্ষেত্রে তেমন কোনো পরির্বতন পায়নি বা হয়নি। কিন্তু কৃষির পণ্য উৎপাদনের উপকরণের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে গত বিশ বছরে দফায় দফায়। কৃষি উৎপাদনের উপকরণের মূল্য বৃদ্ধির অজুহাতটাকে মূল্যস্ফীতির প্রভাব বলে বলা হয়েছে, কিন্তু সেই হারে কৃষককে ভর্তূকিও দেয়া হয়নি। গত সপ্তাহে গোদাগাড়ির চর আষাঢ়ীদহ গ্রামের হাটে এককেজি পটল বিক্রি হয়েছে ৮-১০ টাকায়। ওই পটল রাজধানীর কারওয়ানবাজার বিক্রি হচ্ছে ৩৫-৪০ টাকায়।
দামের এই ব্যবধানকে নানা যুক্তি দিয়ে দেখানো যায়। কেউ বলবেন মধ্যস্বত্ব ভোগীর দৌরাত্ম আবার কেউ বলবেন সিন্ডিকেট আবার কেউ বলবেন পরিবহন খরচ, এ ধরনের নানা যুক্তি চলে আসছে স্বাধীনতার পর থেকেই। তবে প্রায় অর্ধশতাব্দীতেও কৃষকের ন্যায্যতা মেলেনি। সরকার ২০১৯-২০ সালের বাজেটে সিএনজির মূল্য ৪০ থেকে বাড়িয়ে ৪৩ টাকা করেছেন। হিসাবে দেখা যায়, সিএনজির মূল্য বৃদ্ধি পেল ৭ দশমিক ৫ শতাংশ। সিএনজির মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় পরিবহন খাতের ব্যয় বাড়বে। পরিবহন সেক্টরের নিয়ন্ত্রকরা বলছেন, এই মূল্য বৃদ্ধিটার প্রভাব পড়বে ভোক্তাদের ওপর। অর্থ্যাৎ পরিবহন ভাড়া বাড়বে। এই পরিবহন ভাড়া বাড়ার প্রভাবে চর আষাঢ়ীদহ গ্রামের কৃষকের উৎপাদিত পটলের দাম আরেক দফা কমবে। কারণ পাইকাররা কারওয়ান বাজারের বিক্রি মূল্যের সাথে পরিবহন ভাড়া সমন্বয় করতে গিয়ে কৃষকের কাছ থেকে কম মূল্যে কিনবে।
সুতরাং পানি ভাটির দিকে যায়, এই পানি গড়িয়ে যাওয়ার সূত্রের মতো দ্রব্যমূল্যের প্রভাবটির করাল থাবায় নিপতিত হবে গ্রামের প্রান্তিক কৃষক। দেশের বাজেটের আকার বা কলেবরে প্রমাণ হয় দেশের উন্নতি বা উন্নয়ন হয়েছে। দেশের প্রথম বাজেটের ১৯৭২-৭৩ থেকে ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেটের আকার বেড়েছে কয়েক হাজার গুণ। জীবনযাত্রার মানও বেড়েছে হাজার গুণ। তবে কাদের জীবনযাত্রার মান বাড়ল নীরিক্ষণ করলে দেখা যাবে কৃষকের অবস্থা দিন দিন খারাপ হচ্ছে। ১৯৭২-৭৩ সালে একজন কৃষক তার মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণের লক্ষে যে অর্থ উপার্জন করতে পারতো এখন কি তা করতে পারছে। টাকার অংকে কৃষকের আয় বেড়েছে। কিন্তু ভোগের পরিসীমার নিরিখে মাপতে গেলে ১৯৭২-৭৩ সালের চাইতে অনেক কমে গেছে কৃষকের ভোগ বিলাস। বরেন্দ্র এলাকার পাঁচ সদস্য (মা বাবা তিন সন্তান) বিশিষ্ট প্রান্তিক পর্যায়ের কৃষক (বর্গাচাষি) পরিবারে সাথে কথা বলে জানা যায়, এ বছর পরিবারটি ধান পেয়েছে ৭০ মন। নিজেদের সারা বছরের খাওয়া দাওয়ার পর বিক্রি করতে পারবে ২০-২৫ মন ধান। শসা বিক্রি করেছে তিন মণের মতো। ঢেড়স বিক্রি করেছে ১০ মন। আম ২০-২৫ মন। সরিষা যা হয়েছে তা দিয়ে তেল খরচ চলবে। এই পরিবারটির আয়ের মূল্য বা প্রধান উৎস হলো এই উৎপাদিত পণ্য।
এখন হিসাব করলে দেখা যাবে, ধান থেকে পাবে (সরকার নির্ধারিত মূল্য অনুযায়ী) ৭০ হাজার টাকা। শসা বিক্রি এক হাজার টাকা। ঢেড়স বিক্রির চার হাজার টাকা। আম বিক্রির ৩০ হাজার টাকা। মোট প্রাথমিক হিসাবে আয় হবে এক লাখ পাঁচ হাজার টাকা। এখানে উৎপাদন খরচ বাদ দেয়া হয়নি। উৎপাদন খরচ বাদ দিলে তা তিন ভাগের দুই ভাগ হয়ে যাবে মোট আয়। তাহলে পরিবারটির আয় দাঁড়াবে ৭০ হাজার টাকা। মাথা পিছু আয় হিসাবে পরিবারটির মাথাপিছু আয় হবে ১৪ হাজার টাকা।
জাতীয় হিসাবে মাথা পিছু আয় হলো এক লাখ ৫২ হাজার ৭২০ টাকা। যদিও জাতীয় আয় হিসাবের সময় অন্যান্য আনুসাঙ্গিক কিছু বিষয় ধরা হয়। মোট জাতীয় আয় থেকে এই কৃষক পরিবারটি আয় ১১ গুণ কম। অর্থ্যাৎ এই কৃষক পরিবারটির চেয়ে জাতীয় মাথা পিছু আয় ১১ গুণ বেশি।
বিভিন্ন তথ্যানুসন্ধানে দেখা গেছে দেশের মোট জনংখ্যার ৬৫ শতাংশ সরসারি কৃষির ওপর নির্ভরশীল। আর এই ৬৫ শতাংশ কৃষকের মধ্যে বর্তমানে ৭০ শতাংশই প্রান্তিক বা মধ্য পর্যায়ের কৃষক যাদের বাৎসরিক ধান উৎপাদন কোনোক্রমেই ১০০ মণের অধিক নয়। দেশের জিডিপির হিসাবে যে বিরাট অংকের টাকা আয় হচ্ছে সে টাকা তাহলে কোথায় যায়? শাক সবজি ও ধান বাদে অন্যান্য কৃষিপণ্য উৎপাদন এখন আর মাধ্যম বা প্রান্তিক পর্যায়ের কৃষকের হাতে নেই। যেমন ডিম, হাস-মুরগি, মাছ, মাংস এই ধরনের কৃষিপণ্য উৎপাদন করছে ধনী ব্যবসায়ীরা। মূল্যস্ফীতির হিসাবে এই পণ্যগুলোর দাম দফায় দফায় বাড়ছে। বিশ বছর আগে এক কেজি গরুর মাংসের দাম ছিল ৮০-১০০ টাকা। বর্তমানে এক কেজি গরুর মাংসের দাম ৫০০-৬০০ টাকা। অনুরূপ হিসাব করলে দেখা যাবে ডিম, পোলট্রি মুরগি, মাছের দাম বিশ বছরে বেড়েছে পাঁচ গুণ। বিশ বছরের অনুরূপ হিসাবে দেখা যাবে শসা, ঢেড়স, মুলা, গাজর, বেগুনের মূল্য গত বিশ বছরে কয়েক গুণ বাড়াতো দূরের কথা মূল্যের তেমন একটা হেরফেরও হয়নি বরং কমেছে। অপরদিক গুণ হিসাবে কি ধানের মূল্য বেড়েছে গত বিশ বছরে? আদৌও বাড়েনি। ধানসহ শাক-সবজির দামের তেমন একটা পরির্বতন হয়নি। এ ধরনের অপরিবর্তিত মূল্যের কৃষিপণ্যের উৎপাদকদের আয়েরও বিশ বছরে হেরফের হয়নি। তারা তিমিরেই আছে। অপরদিকে তাদের জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়েছে। মূল্যস্ফীতির কারণে দেশের কৃষক পরিবারগুলোর ব্যয় বেড়েছে নানা খাতে, তাদের সন্তানদের স্কুলের বেতন, সন্তানদের শিক্ষা উপকরণের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে, বেড়েছে সংসারের চিকিৎসা ব্যয়।
বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গেছে, খাদ্যপণ্যের মূল্য স্থিতিশীল থাকার কারণে দেশের মূল্যস্ফীতি পাঁচ থেকে ছয় শতাংশের মধ্যে আছে বা থাকে। যাদের কায়িক শ্রমে দেশের সামষ্টিক মূল্যস্ফীতি স্থিতিশীল থাকছে তাদেরকেই বইতে হচ্ছে মূল্যস্ফীতির বিরাট বোঝা। দেশে খাদ্যপণ্যের দাম কম হওয়ায় এদেশে বিশ্বের যেকোনো দেশের চাইতে কম মূল্যে শ্রমিক পাওয়া যায় আর এই কম দামে শ্রমিক পাওয়ার জন্য বাংলাদেশে ঘটেছে পোশাক শিল্পের প্রসার। পোশাক শিল্প বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের ক্ষেত্রে একটি অন্যতম খাত। এই খাতটি যাদের উৎপাদিত পণ্যের কম মূল্যের জন্য সৃষ্টি হলো তাদের প্রতি সরকারে দৃষ্টিভঙ্গিটা বিমাতা মতো। কারণ এদেশের প্রান্তিক পর্যায়ের কৃষক সরকারের বেধে দেয়া ধানের দামে ধান বিক্রি করতে পারছে না। প্রান্তিক পর্যায়ের কৃষকের কাছ থেকে ধান কেনার জন্য সরকারের কোনো উদ্যোগ নেই। কৃষকদের কাছ থেকে বারবার দাবি উঠেছে ইউনিয়ন পর্যায়ে ধান ক্রয়কেন্দ্র স্থাপন করার। কিন্তু চলতি বাজেটেও ইউনিয়নভিত্তিক ধান কেনার উদ্যোগের কথা তেমনভাবে প্রতিফলিত হয়নি।
অপরদিকে দেখা যায়, খেলাপি ঋণীদের প্রণোদনা দেয়াসহ ঋণখেলাপিদের জন্য সরকারের গৃহীত নানা উদ্যোগ। নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, দেশের সমষ্টিক আয় বাড়ছে বিভিন্ন ধরনের শিল্প কারখানা সৃষ্টি এবং বিদেশি বিনিয়োগের জন্য। দেশের কৃষিপণ্যের দাম কম হওয়ায় সস্তা শ্রম পাওয়া যায় আর এই কারণেই শিল্পকারখানাসহ বিদেশি বিনিয়োগ বাড়ছে। তাই যাদের জন্য আজ দেশের আয়ের এই বৈপ্লবিক পরির্বতন তারা হলো এদেশের প্রান্তিক এবং মধ্যম পর্যায়ের কৃষক।
যদিও দেশের মোট জিডিপির হিসাবে কৃষির অবদানটা খুবই কম, তবে বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায়, কৃষির অবদানটা দেশের মূল অর্থনীতির ফাউন্ডেশন। দেশের বর্তমান উন্নয়নের ধারাটি অব্যাহত রাখতে হলে কৃষকের ভাগ্যের উন্নয়ন ঘটাতে হবে। তাই কৃষক পর্যায়ের সরকারি প্রণোদনা বাড়ানো দরকার। ধানসহ অন্যান্য কৃষি পণ্য গুলো ভর্তুকি দিয়ে সরকারের কেনা উচিত। কৃষক আছে বলেই দেশের শিল্প কলকারখানা বেড়েছে। তাই কৃষকই জাতীয় আয়ের মূল্য প্রাপ্যদার।
লেখক: কলামিস্ট
 ঢাকা টাইমস অনলাইন এর সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিডটি ফলো করুন
ঢাকা টাইমস অনলাইন এর সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিডটি ফলো করুন
মন্তব্য করুন