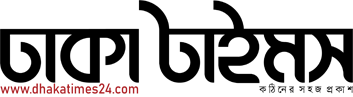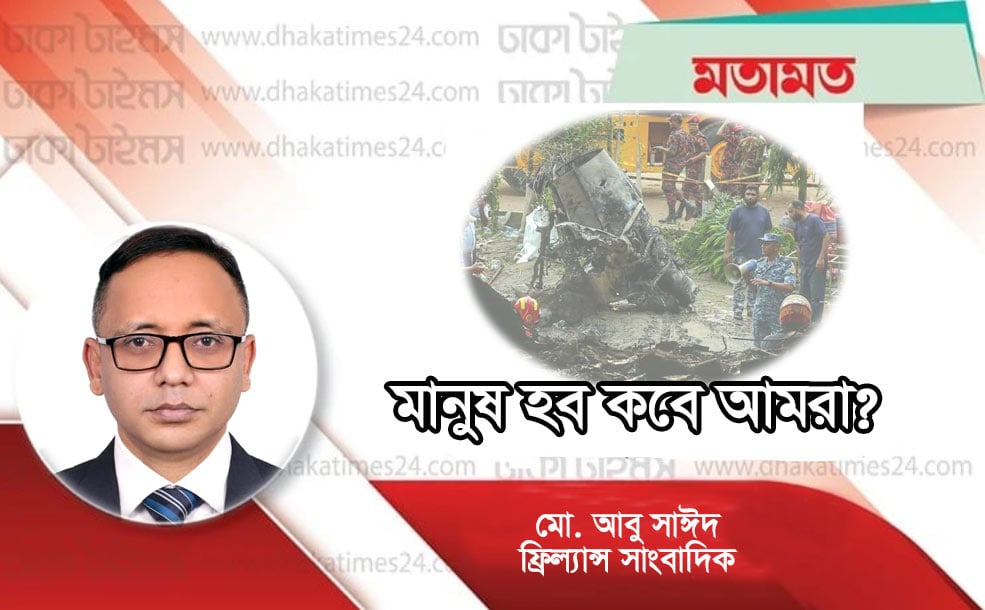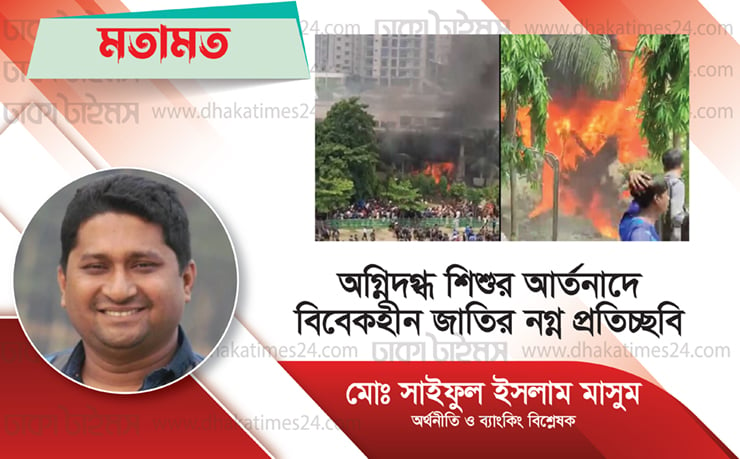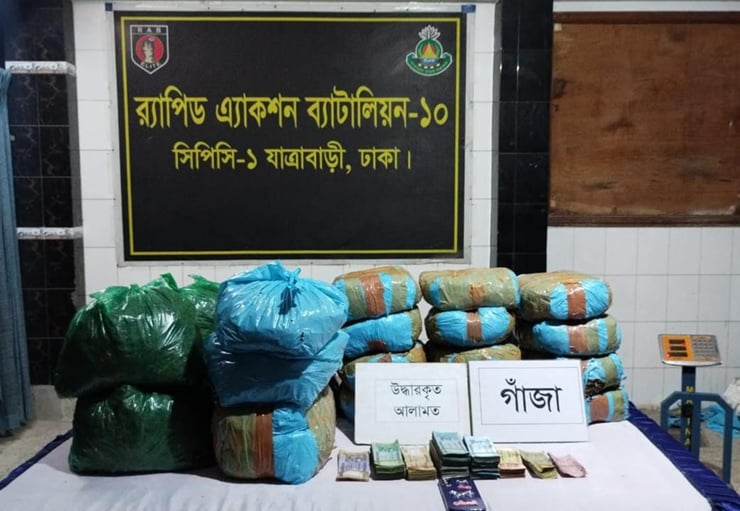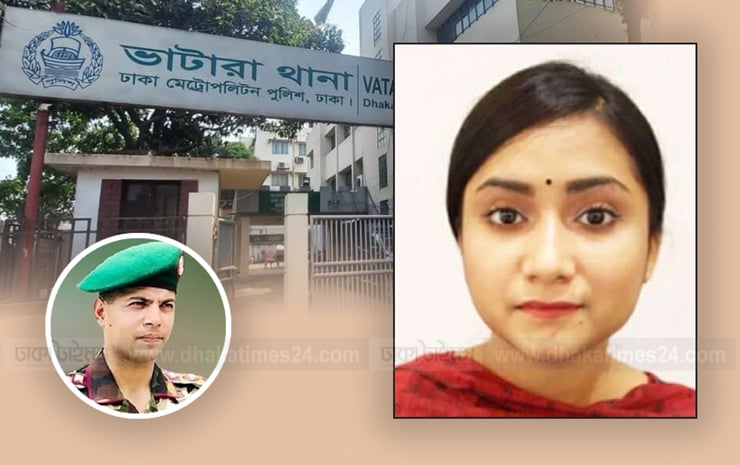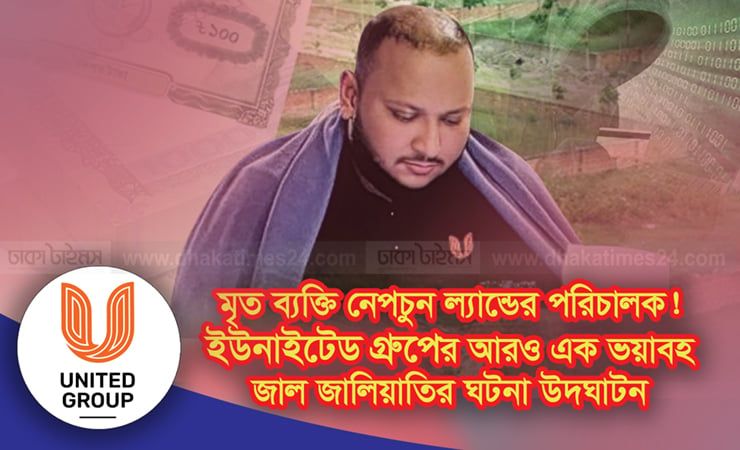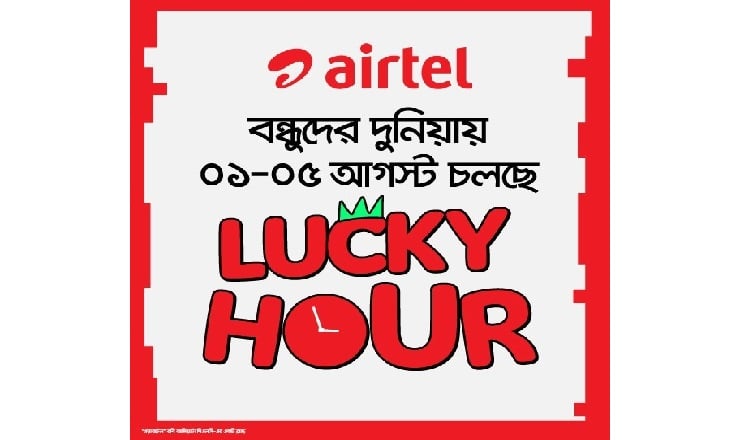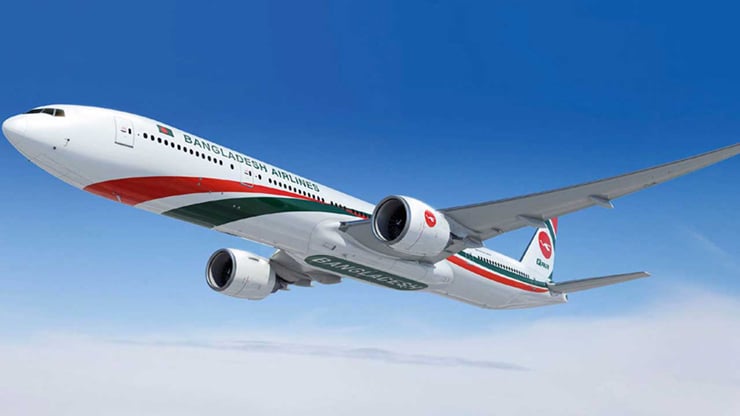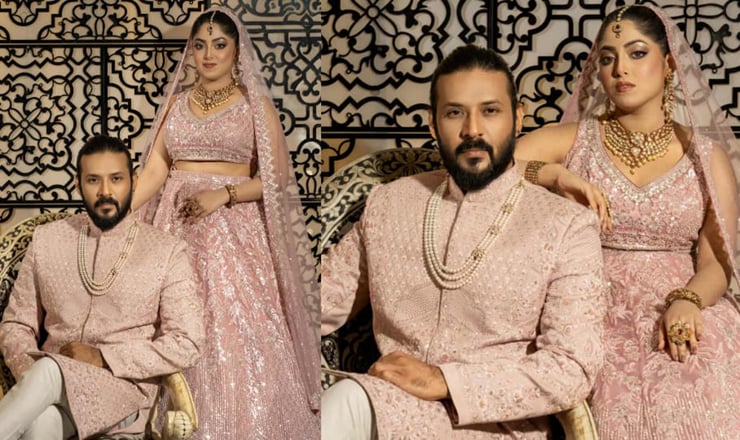বাংলা ভাষা ও একুশে ফেব্রুয়ারি: আন্তর্জাতিক মর্যাদার এক অনন্য স্মারক

‘আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি।’ এমন মনপ্রাণ আকুল করা হৃদয়মথিত আবেগ-অনুভূতির প্রকাশ বিশ্বের ভাষাভিত্তিক কোনো জাতির আছে কি না সেটা যাচাই না করেও নির্দ্বিধচিত্তে গৌরবের শিরোভূষণ পরতে পারে ভাষাভিত্তিক তেপান্ন বছর বয়সী এই বাংলাদেশ জাতিরাষ্ট্রের হাজার বছরের বাঙালি জাতি। শুধু ভাষার জন্য একটি ভূখণ্ডের আপামর মানুষের প্রাণপণ আন্দোলন-সংগ্রাম এবং শেষাবধি ভাষা সংগ্রামীদের মধ্যে কতিপয়জনের বুকের তাজা রক্তের ফোয়ারায় রঞ্জিত হয়ে রাজপথ পিচ্ছিল করে দেওয়ার ঘটনা বিশ্বের বুকে একেবারেই বিরল। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের আসাম ও শ্রীলঙ্কার একটি অঞ্চলে মাতৃভাষার জন্য প্রতিবাদমুখর হওয়ার ঘটনার কথা জানা গেলেও মাতৃভাষা প্রতিষ্ঠায় জীবন দেওয়ার ঘটনা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের এই বাঙলা অঞ্চলেরই একমাত্র ঘটনা। সেদিক থেকে এই অদ্বিতীয় ঘটনার জন্য তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান তথা বর্তমান বাংলাদেশ ভূখণ্ডের এই সমবেত নাগরিকরা এক অনন্য উচ্চতায় আরোহণ করেছে নিঃসন্দেহে। সেদিনের সেই রক্তরঞ্জিত অর্জন সমকালীন বিশ্বে এতটাই আলোড়িত ও প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিল যে- তা এখন আন্তর্জাতিক দিবসের মর্যাদায় উন্নীত হয়েছে। বাঙালি জাতির অর্জিত গৌরবান্বিত এই প্রাপ্তি আজ বিশ্বের সকল দেশই গ্রহণ করেছে সাদর আমন্ত্রণে- এমনকি যে দেশটি জোর করে চাপিয়ে দিয়েছিল তাদের নিজস্ব ঔপনিবেশিক এক অপেক্ষাকৃত দুর্বল ভাষা- তারাও তা শর্তহীন গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে।
বাঙালির একুশে ফেব্রুয়ারি- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। এটা কি ভাবা কম শক্তির কাজ যে- একদা বাঙালির একটি অর্জন আজ বিশ্বের তাবড়-তাবড় শক্তিশালী জাতিও অকুণ্ঠচিত্তে গ্রহণ করে তাদের মাতৃভাষার মর্যাদাকে সমুন্নত রাখতে চেষ্টা করছে। যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরের হে মার্কেটে নিরীহ শ্রমিকদের ওপর এক নারকীয় নৃশংস ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর যেমন আজ বিশ্বব্যাপী পহেলা মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস হিসেবে পালন করা হয় সারা বিশ্বে; ঠিক তেমনি ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ঢাকার রাজপথে মাতৃভাষা আদায়ের লক্ষ্যে ঘটে যাওয়া নৃশংস ঘটনা-উত্তর অর্জনটিও আজ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে বিশ্বের সকল জাতিরাষ্ট্রের মধ্যে। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের এই আন্তর্জাতিক ও অনন্য-বিরল অজর্নটি মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠাকালীন মুহূর্ত থেকে হয়নি; এর জন্য কতিপয় বাঙালির দীর্ঘ সময় ধরে চেষ্টা ও লেগে থাকার অধ্যবসায়কে স্বীকার করে নিতে হয় আমাদের। সন্দেহ নেই, একুশে ফেব্রুয়ারি একটি জীবন্ত সত্তা। এই জীবন্ত সত্তার জাতীয় দিবস থেকে আন্তর্জাতিক দিবসের মর্যাদায় উন্নীত হওয়ার যে গৌরবগাথার অনন্য ঘটনা এখন সেটির প্রেক্ষাপট-বিবরণ দেওয়া যেতে পারে।
১৯৫২ সালের প্রায় ছেচল্লিশ বছর পর, ১৯৯৮ সালের ৯ই জানুয়ারি কানাডার ভ্যাঙ্কুভারনিবাসী বসবাসরত ভাষাপ্রেমিক ও সংস্কৃতিবান বাঙালি মুক্তিযোদ্ধা জনাব রফিকুল ইসলাম এক চিঠি লেখেন জাতিসংঘের তৎকালীন মহাসচিব কফি আনানের কাছে। এতে তিনি ১৯৫২ সালে ভাষা শহিদদের অবদান ও আত্মদানের কথা উল্লেখ করেন, সেইসাথে মহাসচিবকে প্রস্তাব করেন ২১শে ফেব্রুয়ারিকে ‘মাতৃভাষা দিবস’ হিসেবে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য। সে সময় জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেলের প্রধান তথ্য কর্মচারী হিসেবে ছিলেন বাংলাদেশি নাগরিক জনাব হাসান ফেরদৌস। এ চিঠিটি তার নজরে এলে জাতিসংঘের অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রের কাছ থেকেও একই ধরনের প্রস্তাব আনার ব্যবস্থা করার জন্য তিনি সুপারিশ করেন। রফিকুল ইসলাম মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন বিধায় তিনি আন্তর্জাতিকভাবে মাতৃভাষার মর্যাদা আদায়ের লক্ষ্যে এই সময়ে এক অন্যরকম যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন সহযোদ্ধা আব্দুস সালামকে সাথে নিয়ে। তারা বিভিন্ন দেশের বহুভাষাভাষী সদস্য সম্বলিত "A Group of Mother Language of The World" নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। এবার সেই সংগঠনের পক্ষ থেকে কফি আনানকে চিঠি লেখা হয় এবং চিঠির একটি কপি ইউএনও'র ক্যানাডিয়ান অ্যাম্বাসেডর ডেভিড ফাওলারের কাছে প্রেরণ করা হয়। প্রায় একবছর অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর ১৯৯৯ সালের প্রথমদিকে রফিকুল ইসলাম এবং আব্দুস সালাম ইউনেস্কোর ভাষা বিভাগের জোশেফ পডের সাথে সাক্ষাতে জোশেফ তাদেরকে ইউনেস্কোর আনা মারিয়ার সাথে কথা বলতে সুপারিশ করেন। আনা মারিয়ার অবদান আমাদেরকে অবশ্যই কৃতজ্ঞতাভরে স্মরণ করতে হবে; তিনি যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে ব্যাপারটাকে দেখেন। ১৯৯৯ সালের এপ্রিল মাসে জনাব রফিকুল ইসলাম এবং জনাব সালামকে জানানো হলো- ‘তোমাদের প্রস্তাবিত এই বিষয়টি খুবই ইন্টেরেস্টিং। ইউনেস্কো এই ধরনের প্রস্তাব পেলে তা আলোচনা করে থাকে। বিষয়টি অক্টোবরে প্যারিসে অনুষ্ঠাতব্য ইউনেস্কো সম্মেলনে উত্থাপন করতে হবে এবং তা কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে হলে চলবে না; কোনো সদস্য রাষ্ট্র কর্তৃক এই প্রস্তাব উত্থাপিত হলে তা বিবেচনা করা হবে।’
এরপর জনাব রফিকুল ইসলাম এবং জনাব আব্দুস সালাম বিষয়টির সবিস্তার ব্যাখ্যা বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠান। এই স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সে সময় বাংলাদেশের শিক্ষামন্ত্রী এম এ সাদেক এবং শিক্ষা সচিব কাজী রকিবুদ্দিন, অধ্যাপক কফিলউদ্দিন আহমেদ, মশিউর রহমান (প্রধানমন্ত্রীর সেক্রেটারিয়েটের তৎকালীন ডিরেক্টর), সৈয়দ মোজাম্মেল আলি (ফ্রান্সে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত), ইকতিয়ার চৌধুরী (কাউন্সিলর), তোজাম্মেল হক (ইউনেস্কোর সেক্রেটারি জেনারেলের শীর্ষ উপদেষ্টা) সহ আরও অনেকেই প্রস্তাবটির স্বপক্ষে আরো ২৯টি দেশের সমর্থন আদায়ে জোর প্রচেষ্টা চালান। হাতে সময় ছিল একদমই কম। ১৯৯৯ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর ছিল আনুষ্ঠানিকভাবে ইউনেস্কোর প্রস্তাব উত্থাপনের শেষ দিন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তখন পার্লামেন্টে। তাকে ফোন করে অনুরোধ করা হলো তিনি যেন প্রস্তাবটি সই করে ফ্যাক্স করে দেন ইউনেস্কোর দপ্তরে। বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ত্বরিত সিদ্ধান্ত দেন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের। ‘ভাষা এবং সংস্কৃতির বিভিন্নতা সংরক্ষণ’ সম্পর্কিত ইউনেস্কোর নীতিমালার আলোকে গঠিত প্রস্তাবনা বাংলাদেশ থেকে ইউনেস্কোর অফিসে অফিসিয়াল সময়সীমা শেষ হবার মাত্র একঘণ্টা আগে ফ্যাক্সবার্তায় পৌঁছায়।
অতঃপর ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর আসে সেই ঐতিহাসিক দিন। এই দিনে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের বিজ্ঞান, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা ইউনেস্কোর প্যারিস অধিবেশনে (২৬শে অক্টোবর-১৭ই নভেম্বর) একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে গ্রহণের প্রস্তাব (নম্বর ৩০ সি/ডি/আর-৩৫) উত্থাপন করা হয় সভার প্রথমেই। ইউনেস্কোর অধিবেশনে যোগদানকারী বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের সদস্য শিক্ষামন্ত্রী জনাব সাদেক, ফ্রান্সে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত সৈয়দ মোয়াজ্জেম আলী ও ইউনেস্কো মহাপরিচালকের বিশেষ উপদেষ্টা জনাব তোজাম্মেল হকের কূটনৈতিক প্রজ্ঞা, দক্ষতা ও বিচক্ষণতা এ ব্যাপারে মূল্যবান অবদান রাখে। ১৮৮টি দেশ কোনো ধরনের বিরোধিতা ছাড়া সাথে সাথেই সমর্থন জানায়। এরপর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৩০তম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে বাংলাদেশসহ সাতাশটি দেশের সমর্থনে সর্বসম্মতিক্রমে একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতি পায়। এর ফলে ২০০০ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি থেকে দিবসটি সারা বিশ্বব্যাপী জাতিসংঘের সদস্য দেশসমূহে যথাযথ মর্যাদায় পালিত হচ্ছে। বলার অপেক্ষা রাখে না- সারা বিশ্বে আজ সকলেই জানতে পারছে বাঙলা ভাষার জন্য বাংলা অঞ্চলের কিছু মানুষ জীবন দিতে বন্দুকের গুলির সামনে দাঁড়িয়েছিল। তাদের বুকের তাজা রক্তের বিনিময়েই বাঙালির মাতৃভাষা সেদিন প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। সেদিন যারা বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়েছিল মাতৃভাষাকে রক্ষার জন্য সেই কীর্তমান পুরুষ সালাম-বরকত-রফিক-শফিক-জব্বারের আত্মত্যাগের কাহিনীও জানতে পারছে সকলে। পাশাপাশি বহু ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের শাশ্বত ইতিহাস জানতেও অনেকে আগ্রহী হয়ে ওঠছে।
বাংলা ভাষা একটি প্রাদেশিক ভাষা হওয়ার দরুন এর ওপর শাসক শ্রেণির কর্তব্যক্তিরা কখনোই খুববেশি সুনজর দেননি; সব সময়ই একটা বিমাতাসুলভ আচরণ করে গেছেন তারা। ভাষার সঙ্গে ভূখণ্ডগত ভৌগোলিক সীমানা সবসময়ই ওতপ্রোতোভাবে জড়িত। আমরা জানি, ১৯৪৭ সালে দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভাগ হলো ব্রিটিশ ভারত; সৃষ্টি হলো ভারত ও পাকিস্তান। পাকিস্তান আবার দুটি খণ্ডে বিভক্ত- পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তান। আশ্চর্যের বিষয় যে- এই দুই ভূ-খণ্ডের ভেতর ভৌগোলিক দূরত্ব ছিল ১৮০০ কিলোমিটার; আর ভাষা ও সংস্কৃতির ব্যবধান ছিল আকাশ-জমিন। অনেকগুলো জাতিসত্তা নিয়ে সৃষ্ট তৎকালীন পাকিস্তানের মাত্র ৬ শতাংশের ভাষা ছিল উর্দু, যেখানে ৫৪ শতাংশ মানুষের মাতৃভাষা ছিল বাংলা। অথচ অবাক হওয়ার ব্যাপার যে- শাসকগোষ্ঠী সংখ্যালঘু হয়েও সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষার ওপর দখলদারিত্বের চেষ্টা চালায় অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে। তারা প্রতিষ্ঠা করতে চায়- সংখ্যালঘুর ভাষাই হবে একমাত্র রাষ্ট্রীয় ভাষা।
১৯৪৮ সালে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঘোষণা দেন- ‘উর্দু এবং উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা’। বাঙালির ওপর অযাচিত চাপিয়ে দেওয়া এই অশালীন বক্তব্যে তখন বিক্ষোভে ফেটে পড়ে পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ জনগণ; বাংলা ভাষার রাষ্ট্রীয় ও সমমর্যাদার দাবিতে সে সময় সর্বাত্মক আন্দোলন দানা বাধতে শুরু করে- ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারিতে যার চরম ও চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটে রাজপথে বুকের তাজা রক্ত গড়িয়ে পড়ার মধ্য দিয়ে।
মূলত বাঙালির আত্ম-পরিচয়ের ভৌগোলিক সীমানায় ভাষাচেতনার যে গভীর ও তৃণমূল শেকড়, তারই ইতিহাস ও সূত্র ধরে পূর্ব বাংলার রাজধানী ঢাকায় মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর বক্তব্যেরও আগে ১৯৪৭ সালের নভেম্বর- ডিসেম্বরে একটি ভাষা-বিক্ষোভ হয়। ‘তমদ্দুন মজলিস’ নামের একটি সংগঠন পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কী হবে- ‘বাংলা নাকি উর্দু’- এই নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকে, সেখানেই সর্বপ্রথম বাংলাকে উর্দুর পাশাপাশি পাকিস্তানের একটি রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা করার দাবি জানানো হয়। তমদ্দুন মজলিশের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক আবুল কাশেম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কী হওয়া উচিত সে ব্যাপারে একটি সভা আহ্বান করেন এবং সেখানেই বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার ব্যাপারে পাকিস্তান সরকারের কাছে নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় আন্দোলন করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উল্লেখ্য, সে সময়ে সরকারি কাজকর্ম ছাড়াও সকল ডাকটিকেট, পোস্টকার্ড, ট্রেন টিকেটের গায়ে কেবলমাত্র উর্দু এবং ইংরেজিতে লেখা থাকতো।
বাংলা ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার সূত্র ধরে এমন একটি নাজুক পরিস্থিতিতেই ভাষা-বিস্ফোরণের মতো ঘটনাটি ঘটতে শুরু করে- যার চুড়ান্ত পরিণতি দেখা যায় বাহান্নের একুশে ফেব্রুয়ারিতে। এটা বলা মোটেও অসংগত নয় যে- এই ভাষা আন্দোলনই বিভিন্ন ধাপে সর্বাত্মক মুক্তির আন্দোলনে রূপ নিয়ে শেষাবধি স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রেক্ষাপট হয়ে দাঁড়ায়। আজ বাংলা ভাষা বিশ্বের দরবারে একটি অনন্য মর্যাদার ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। এ ভাষা প্রতিষ্ঠায় যে আত্মত্যাগ ও দীর্ঘ সংগ্রাম রয়েছে বাঙালির সেই আত্মত্যাগ ও সংগ্রামের শক্তিতেই এই ভাষা বিশে^র দেশে দেশে মাতৃভাষা রক্ষার ও সমুন্নতি দান করার শক্তি জোগাবে।আলী হাসান: সাংবাদিক, কলাম লেখক ও সংস্কৃতিকর্মী
 ঢাকা টাইমস অনলাইন এর সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিডটি ফলো করুন
ঢাকা টাইমস অনলাইন এর সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিডটি ফলো করুন
মন্তব্য করুন