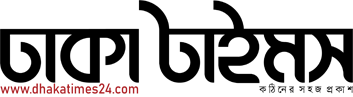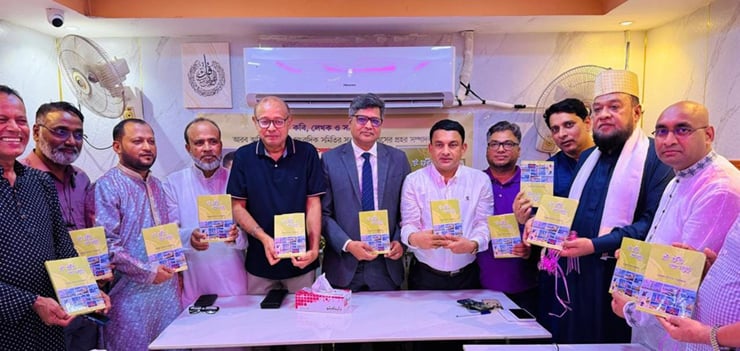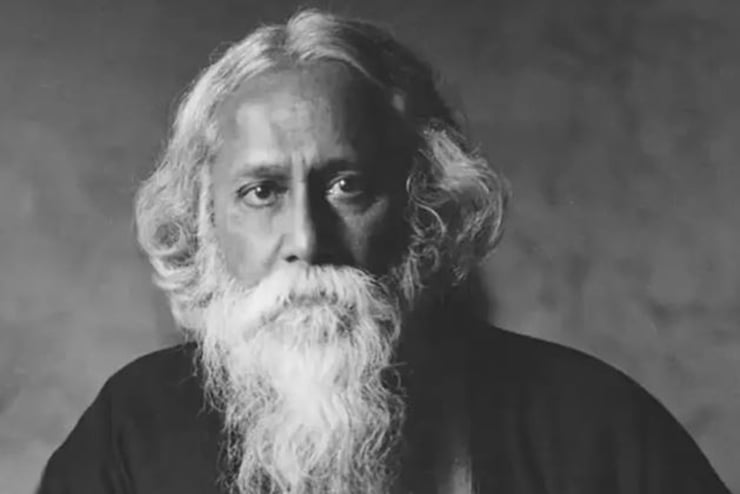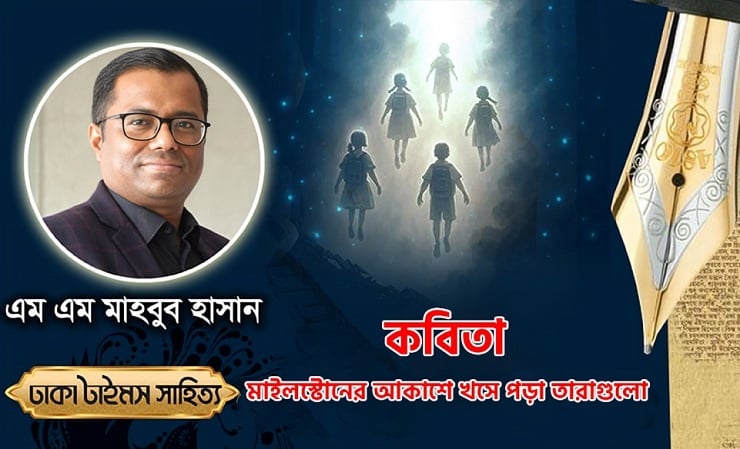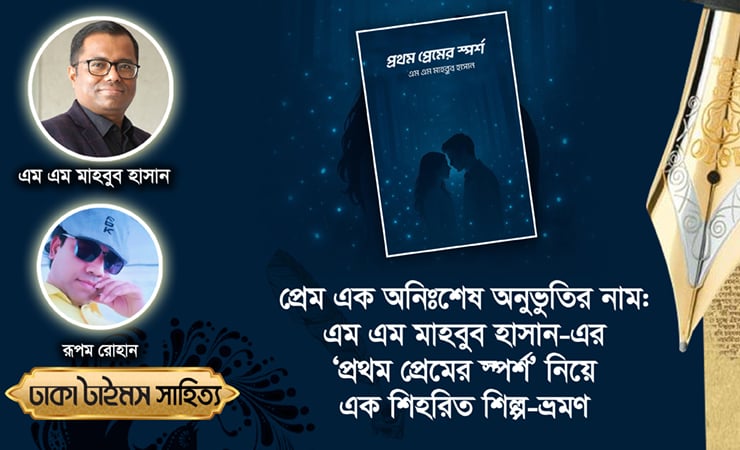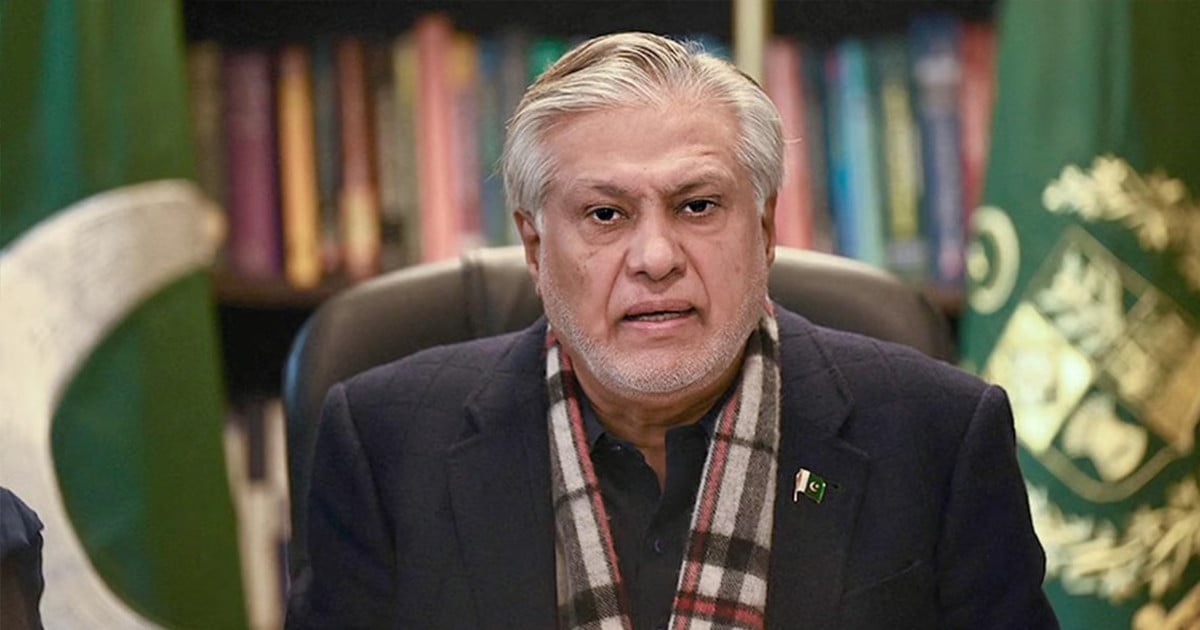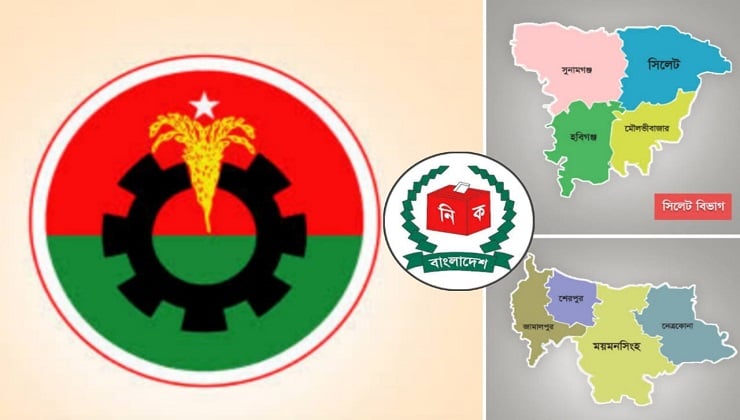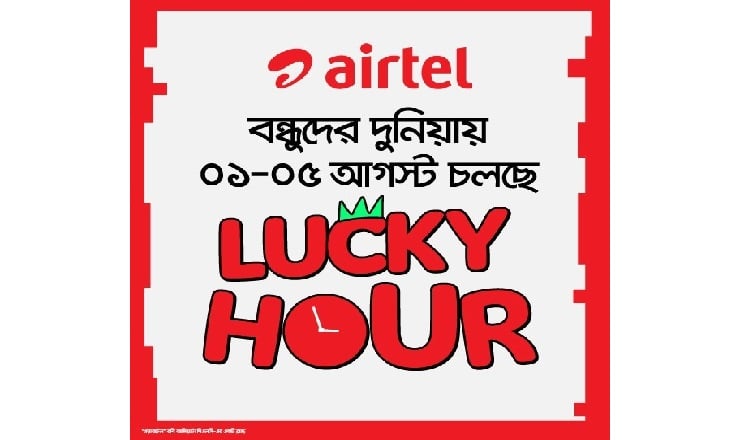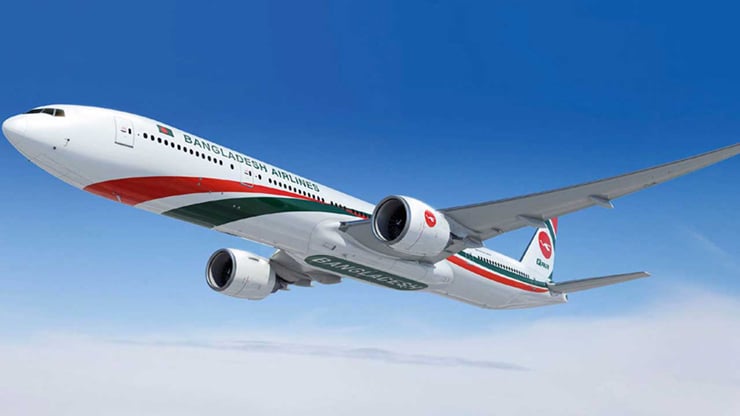কবির সাধনা
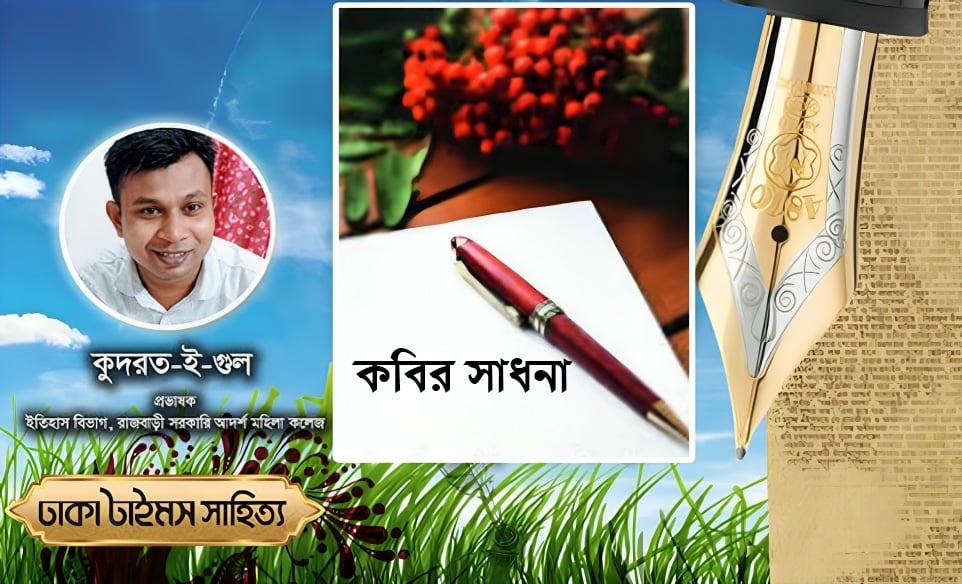
'উঠন্তি মুলো পত্তনে চেনা যায়' এমন একটা প্রবাদের সাথে চিনপরিচয় আছে মানুষের। বাবা তার ছেলের চালচলন, হাবভাব, লেখালেখির প্রতি ঝোঁক দেখে বলেছিলেন, 'তুই কবি হবি'। আজন্ম যিনি সেই মন্ত্রের সাধনায় ছিলেন মশগুল। আন্ত একটা জীবন গুজার করলেন কবিতার সাধনায়। কলা যায়, সাহিত্য সাধনায়। নানা প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও যার মূল উদ্দেশ্যই ছিল সাহিত্য অঙ্গনে ফুল ফোটানো। তাই তো বর্তমান ফরিদপুর ভৎকালীন বৃহত্তর যশোরের অজপাড়াগাঁয়ে জন্মগ্রহণ করেও এই লাইনের স্বনামধন্য মানুষের সাথে গড়ে তুলেছেন সখ্য। নিজের প্রতিভার দ্যুতি ছড়িয়ে তাদের করেছেন মুগ্ধ এবং কেড়েছেন নজর। হ্যাঁ, বলছিলাম এমনই একজন আপাদমস্তক কবিসাধক কবিরত্ন এম এ হকের (১৯২৯-২০০৬) কথা। যিনি স্থানীয়দের কাছে 'কবি সাহেব' ও 'কবিরত্ন'নামেই পরিচিত ছিলেন।
কবির বেড়ে ওঠা মূলত একটি মুসলিম পরিবারে। কবির বাবা ছিলেন বলা যায় চারণ কবি। মুখে-মুখে বেঁধে ফেলতেন ছড়া, জারি-সারি গান। এলাকায় কোন রকম দুর্যোগ-দুর্বিপাক আসলে বা গণসচেতনতামূলক কোন বিষয় এসে হাজির হলে সাথে সাথে বেঁধে ফেলতেন জারি-সারি গান। নিজে সুর করে সন্ধ্যায় পাড়া-মহল্লায় গায়ক দিয়ে তা গাওয়ানোর ব্যবস্থা করতেন। এ কারণে তাঁর বাবার ছিল সুখ্যাতি। তিনি মূলত এ আবহের মধ্যে বেড়ে ওঠেন এবং রক্তে তা মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। তিনিও লিখতে থাকেন ছড়া-কবিতা। তা দেখে কবিকে উৎসাহিত করেন বাবা। সেখান থেকেই তার লেখার হাতেখড়ি। এছাড়া তিনি কিশোর বয়সে হয়েছিলেন সুফি মতবাদের কবি আশরাফ আলী খানের দ্বারা প্রাণিত। কেননা, কবি আশরাফ আলী খানের বাড়ি ছিল কবির গ্রামের পাশেই পানাইল গ্রামে।
এরপর কবি ম্যাট্রিক পাশ করে ভর্তি হন খুলনার বি.এল কলেজে। যেখানে পেয়েছিলেন ডক্টর এনামুল হক, শহীদ বুদ্ধিজীবী মুনীর চৌধুরী এবং ঐতিহাসিক কে আলীর মতো শিক্ষক। তিনি এঁদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসেন এবং তাঁদের অনুপ্রেরণায় লেখায় আরো বেশি মনোনিবেশ করেন। এই কলেজ থেকে পাঠ চুকিয়ে আসেন গ্রামে এবং শিক্ষকতা পেশাকে বেঁছে নেন পরিকল্পিতভাবেই। ইচ্ছে করলে অফিসের চাকরি নিতে পারতেন। কিন্তু শিক্ষকতাকে পেশা হিসাবে নিলেন নিজের সাহিত্য সাধনাকে বেগবান করার জন্য। পড়ালেখার সুযোগ যাতে আরো বেড়ে যায়। তাছাড়া, ঐ মহান শিক্ষকদের কাছ থেকেও অনুপ্রেরণার আলো বুকে নিয়ে এ পেশাকে নেশার মতো গ্রহণ করেন।
আর একটি বিষয় বিশেষভাবে নাড়া দেয়া এবং চিন্তাকে থাক্কা দেয়ার মতো। তা হল, তাঁর বই পড়ার বিস্তার এবং গভীরতা। তিনি সারাক্ষণ বই পড়ার মধ্যে ডুবে থাকতেন। আর লিখে যেতেন হরদম। এমনকি তিনি দূর-দূরান্ত থেকে বই ধার করে এনে পড়তেন। তাঁর পাণ্ডিত্য এতো গভীর ছিল যে, মনে হতো তিনি যেন একটা ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি। তাঁর পাণ্ডিত্যের রোশনাই চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। তিনি ধর্ম বিষয়ে পাণ্ডিত্যের স্বাক্ষর রেখেছিলেন। তিনি মুসলিম ধর্মসভায় বিশেষ বক্তা হিসাবে যেমন ওয়াজ করতেন, তেমনি হিন্দু ধর্মসভায় বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য দিতেন। এলাকায় তিনি যুক্তিবাদী' হিসাবেও পরিচিত পান।
এক সময় গ্রামে বিচারগান, পালা গানের বিশেষ চল ছিল। তিনি বিভিন্ন বিচার গানের বিচারক হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। যেখানে সে সময়কার দেশবরেণ্য বিচারগানের শিল্পীদের সাথে পরিচিত হন। ফলে তার লেখায় সেই সব আধাত্মাবাদী চেতনা লক্ষ্য করা যায়। তিনি বিভিন্ন জেলায় কবি গানের আসরে রাতের পর রাত আসর জমিয়েছেন আর ঘুরে বেড়িয়িছেন অবিরল। সেখান থেকে তাঁর বন্ধুত্ব হয় কবিয়াল বিজয় সরকারের সাথে। বিশিষ্ট পল্লীগীতি, মর্শিদী, বিচার ও জারিগান শিল্পী হাজেরা বিবির সাথে তাঁর সখ্য গড়ে ওঠে। নানা সময়ে তিনি হাজেরা বিবির বিচার গানের বিচারক ছিলেন।
তিনি পল্লিকবি জসীমউদ্দীন ও সনেটকার সুফী মোতাহার হোসেনের বিশেষ স্নেহভাজন হয়ে ওঠেন। তাঁর প্রতিভার স্মৃতি দিয়ে তাঁদের মুগ্ধ করেন এবং বিশেষ সান্নিধ্য অর্জন করেন। কবি তাঁর রচিত 'স্মৃতিকথা' গ্রন্থে তা উল্লেখ করেছেন। তাঁরা দুজন কবির রচিত 'এপার-ওপার' গানের বইয়ে ভূমিকা লিখে দেন। এবং জসীমউদ্দীন কবিকে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বিভিন্ন লোকজ সাহিত্য সংগ্রহের পরামর্শ দেন।
এর ভিতর দিয়ে বেজে ওঠে মুক্তিযুদ্ধের দামামা। তিনি মহান মুক্তিযুদ্ধে কলমযোদ্ধা হিসেবে হিসেবে ছিলেন স্বরাট। স্থানীয় পর্যায়ে মুক্তিযোদ্ধাদের গান রচনা ও সুর করে দিয়েছেন। লিখেছেন মুক্তিযুদ্ধের উপর নানা কবিতা। যা রণাঙ্গণে মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে উঠেছিল। যা এখনো স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধারা স্মৃতিচারণ করেন।
এছাড়াও কবি পত্রিকা সম্পাদনায় মনোনিবেশ করেন। মহাকবি মাইকেল মধুসূদনের ওপর 'মধুস্মরণে' নামে একটি পত্রিকা সম্পাদনা করেন। যেখানে তাঁর সম্পদনার মুন্সিয়ানার পরিচয় মেলে। তিনি ফরিদপুর এবং যশোরের নানা উপজেলার কবিদের নিয়ে গড়ে তোলেন 'শুকতারা
সাহিত্যগোষ্ঠী'। তিনি হন তার প্রতিষ্ঠাতা। প্রতি বছর কবিদের নিয়ে সাহিত্যসভার আযোজন করতেন। যা স্থানীয়ভাবে কবিদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলে। এর পাশাপাশি সামাজিক কর্মকাণ্ডের সাথে নিজেকে রেখেছেন যুক্ত। তিনি এলাকায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠায় অনন্য ভূমিকা রাখেন।
তিনি তার সাহিত্যিক জীবনে রচনা করেছেন বেশ কিছু গ্রন্থ। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো- শুকতারা (কাব্যগ্রন্থ), পথদিশারু (কাব্যগ্রন্থ), কাতাল পথিক (কাব্যগ্রন্থ) এপার-ওপার (লোকগানের সংকলন), কচি মনের খোরাক' (দ্রুতপঠন গল্প), দরদে নবী' (ইসলামিক গান), হক বচন (ছন্দবদ্ধ বাগধারা), দেশের গান (দেশাত্মবোধক গানের সংকলন), দাদুর ছড়া (শিশু সাহিত্য), 'স্মৃতিকথা', 'মুক্তির গান' (কবিতা)।
স্বীকৃতি হিসাবে যশোর সাহিত্য সংঘ' থেকে 'কবিরত্ন' উপাধিতে ভূষিত হন। এছাড়া প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁ কর্তৃক সংগৃহিত বাংলা উন্নয়ন বোর্ডে কবিতা এবং জীবন বৃত্তান্ত সংকলনে স্থান পায়। এবং তাঁর রচিত 'কচি মনের খোরাক' গ্রন্থটি ১৯৭১ সালের পূর্বে পাকিন্তুন শাসনামলে যশোর শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক প্রাথমিক স্তরে দ্রুত পঠন হিসেবে অন্তর্ভুক্ত ছিল। কবি সাহাদৎ হোসেন কর্তৃক 'যশোরের লোককবি' সংকলনে কবির সংক্ষিপ্ত জীবনীসহ করিতা সংকলিত আছে। এছাড়া, বৃহত্তর ফরিদপুরের কবিদরে তালিকায় কবির নাম অন্তর্ভুক্ত আছে। এছাড়াও তিনি যে একজন কৃতী শিক্ষক ছিলেন তার স্মারকচিহ্ন হিসেবে বেশ কয়েকবার শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের মর্যাদা অর্জন করেন।
হয়ত তিনি কেন্দ্র থেকে ছিলেন আপাত সংযোগহীন। বলা যায়, কেন্দ্রের আলো পড়েনি তাঁর উপর। হয়ত কেন্দ্র কখনোই প্রান্তকে সেভাবে গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয়নি। এটাকে বলা যায় কেন্দ্রমুখী রোগ। কিন্তু জাতীয় সাহিত্য-সংস্কৃতি বলে যে একটা বিষয় আছে, তা শুধু কেন্দ্রের প্রতিনিধিত্বই করে না। তা কেন্দ্র-প্রাপ্ত এই দুই জ্বরের সজীব বন্ধনেই গড়ে ওঠে। যদি তা-ই হয়, তাহলে প্রান্তে যাঁদের মনীষ্য আছে, সমাজে যাঁদের অবদান আছে, তাদের সসম্মানে তুলে আনলে আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির চরিত্র উৎকর্ষের দিকে যাবে এবং জাতি উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি অর্জন করবে। অবশ্যই এ প্রকল্প হাতে নেওয়ার উৎকৃষ্ট সময় এসেছে বলে মনে করি। কবির এই প্রয়াণ দিবসে জাতীয় সাহিত্য-সংস্কৃতি মুক্তি পাক এই কামনা জারি থাক।
লেখক: প্রভাষক, ইতিহাস বিভাগ, রাজবাড়ী সরকারি আদর্শ মহিলা কলেজ।
 ঢাকা টাইমস অনলাইন এর সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিডটি ফলো করুন
ঢাকা টাইমস অনলাইন এর সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিডটি ফলো করুন
মন্তব্য করুন