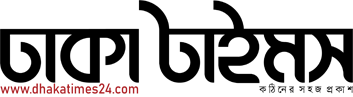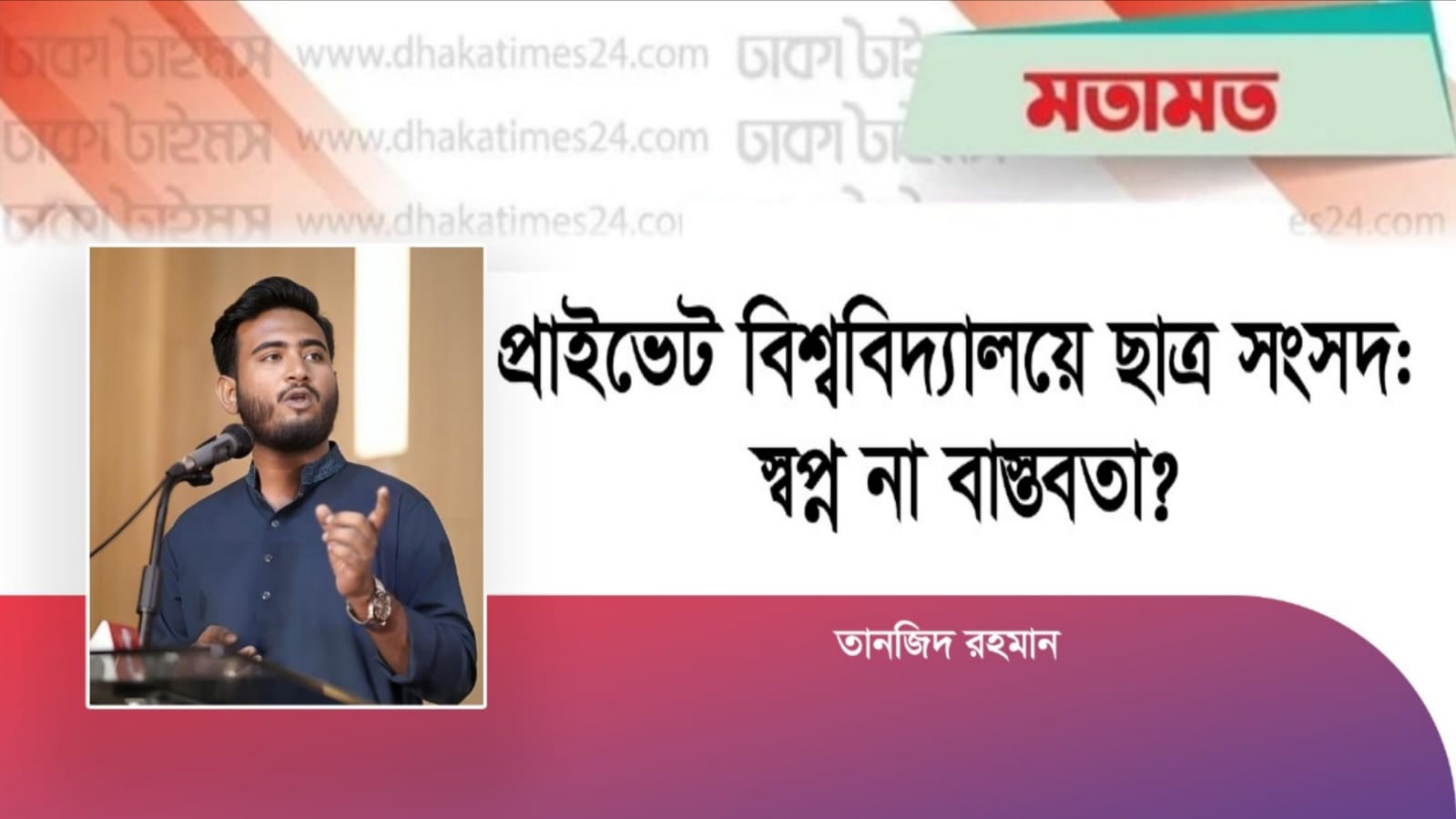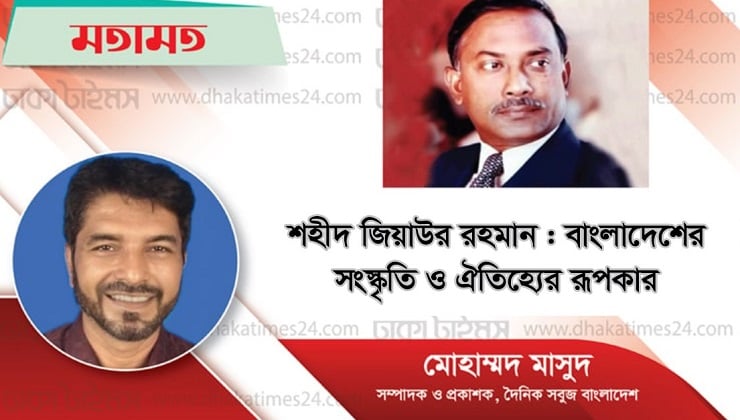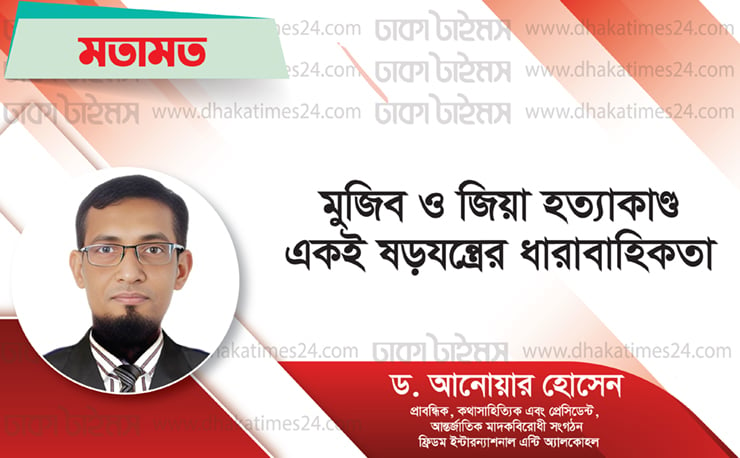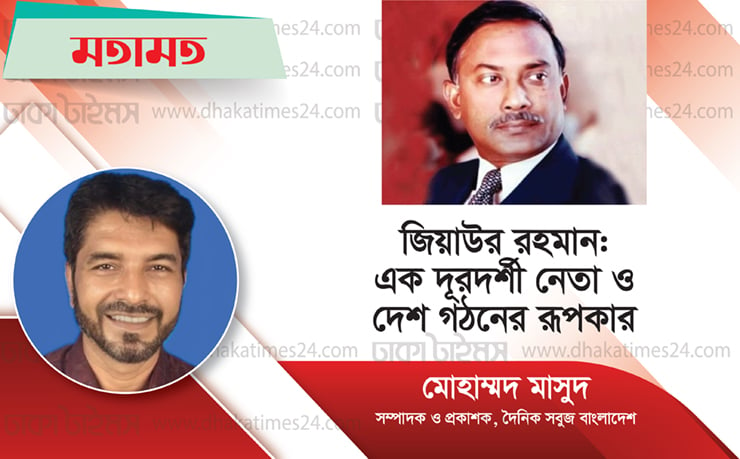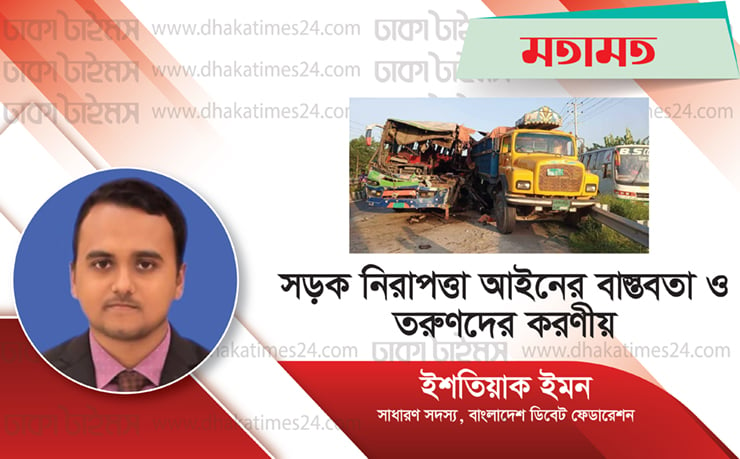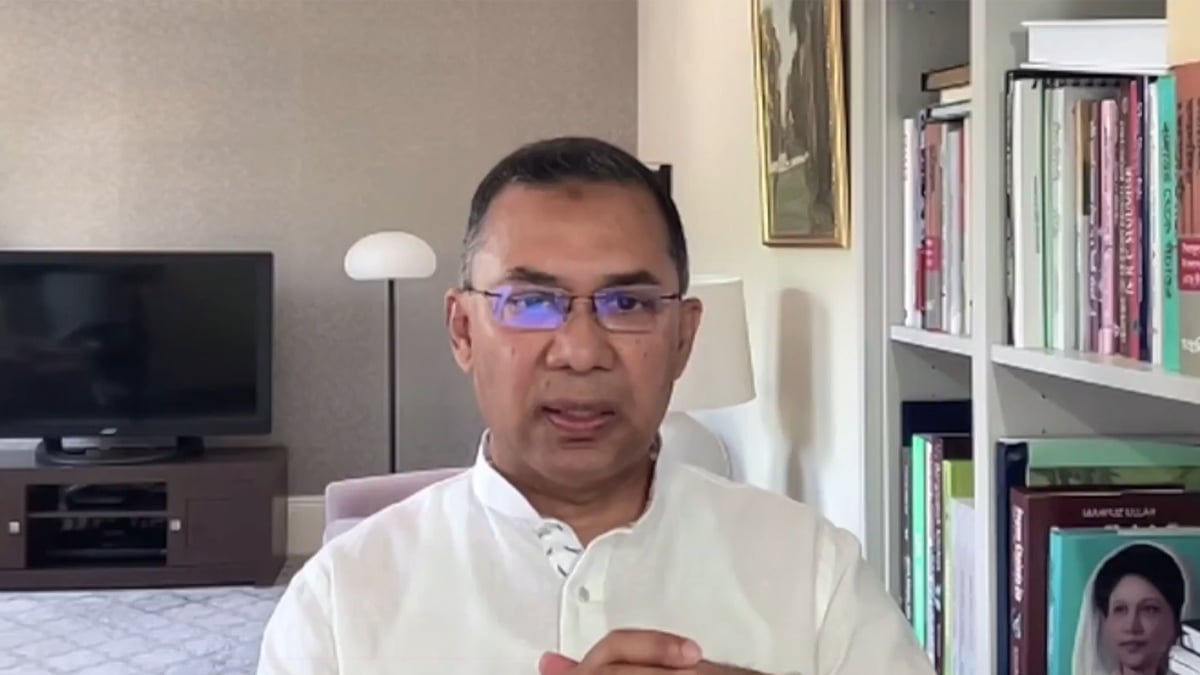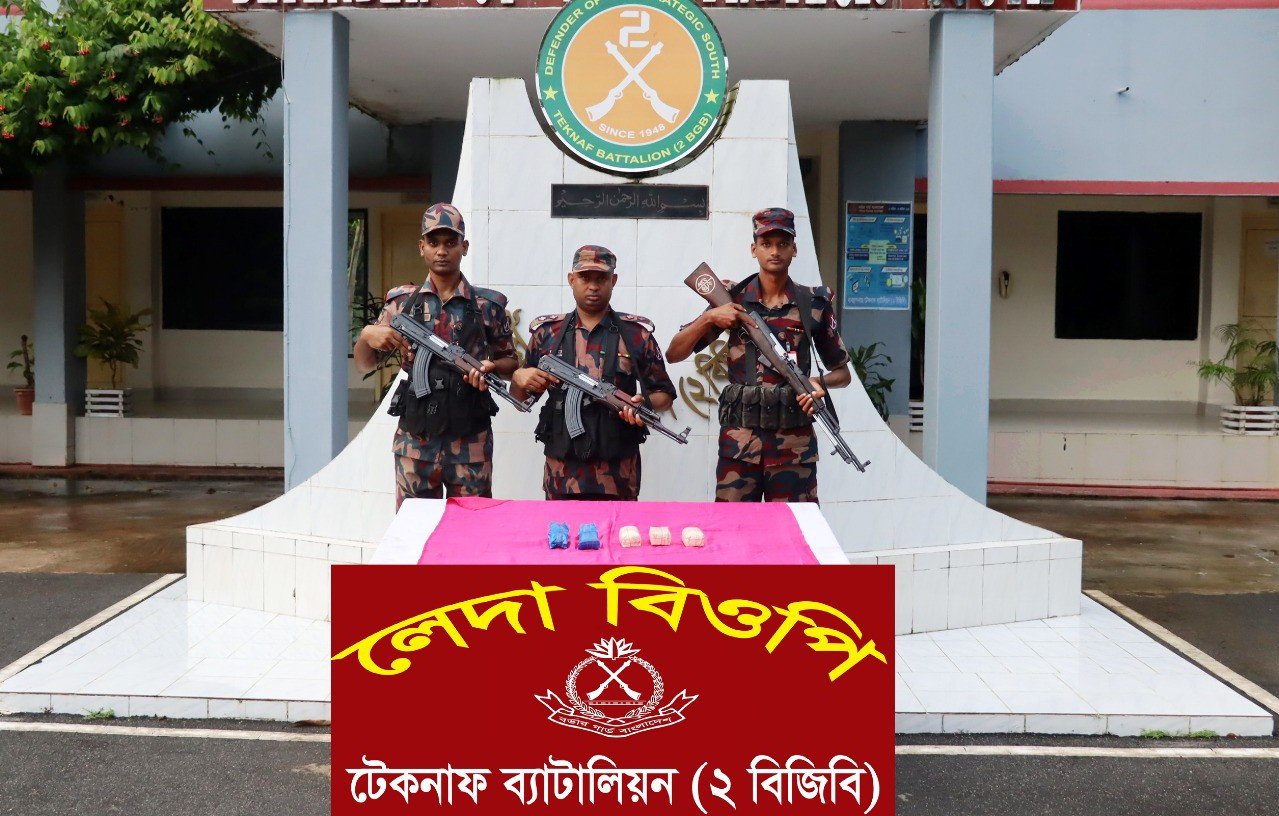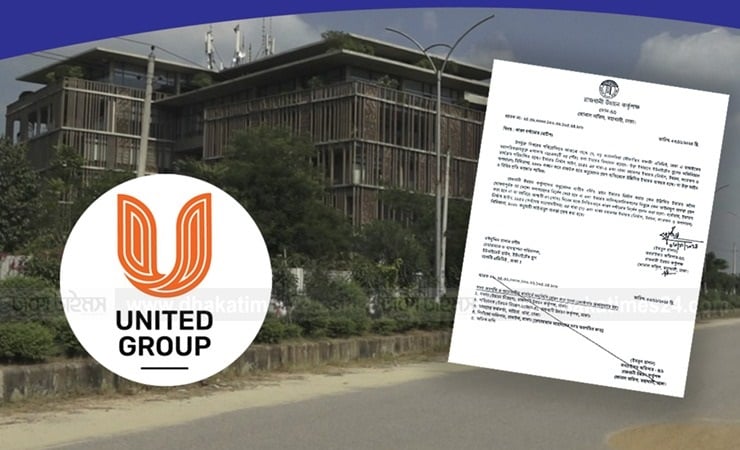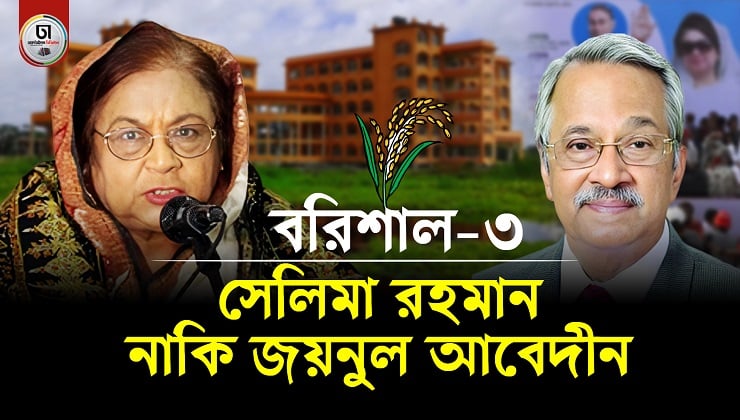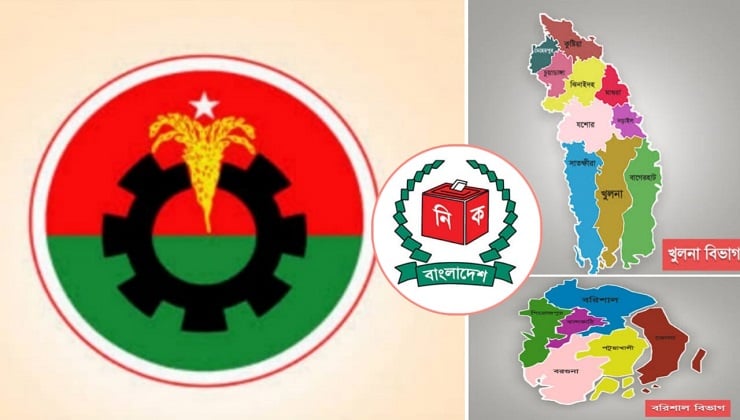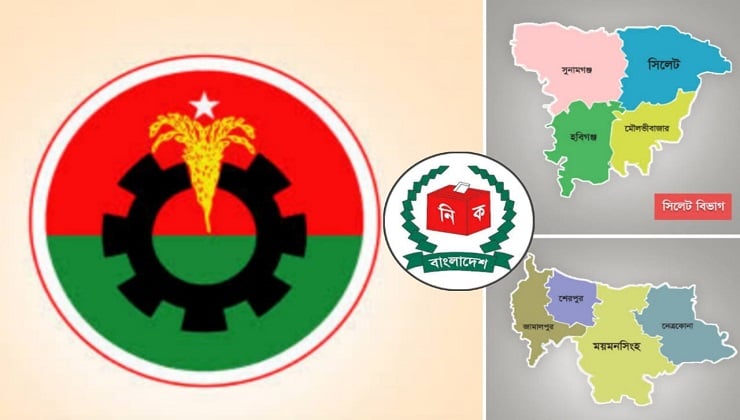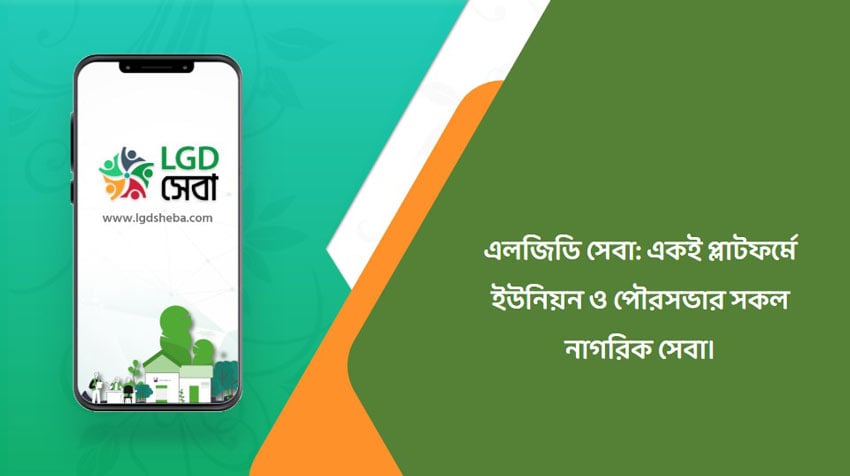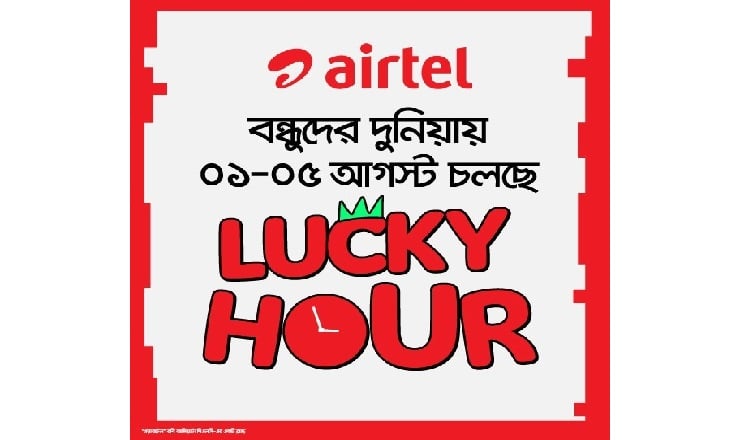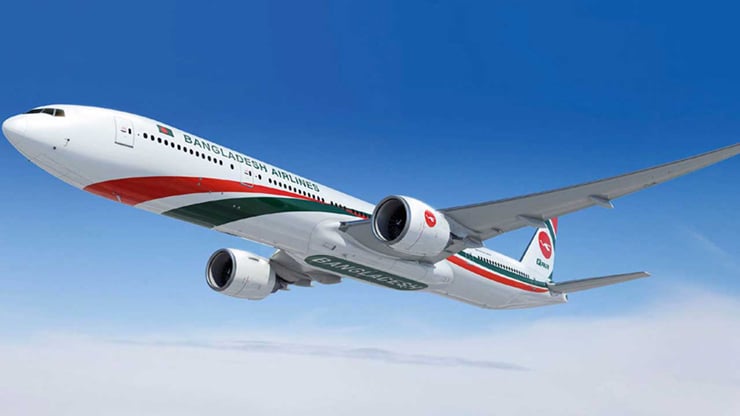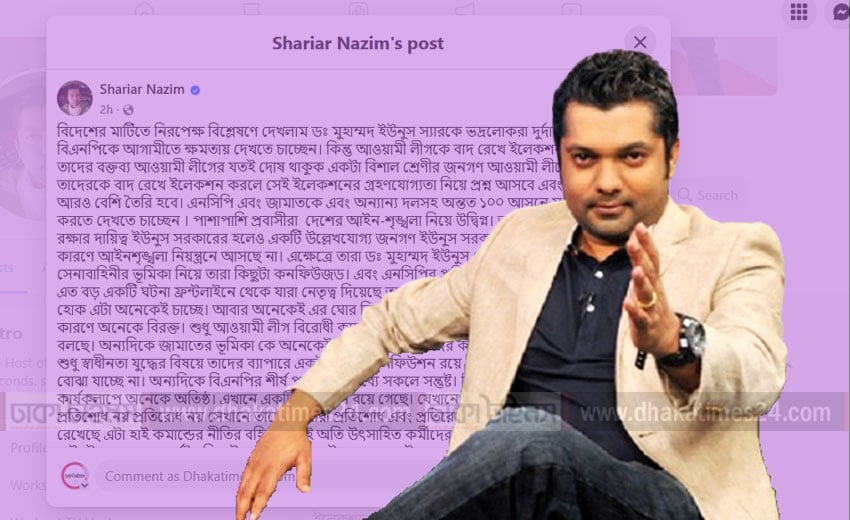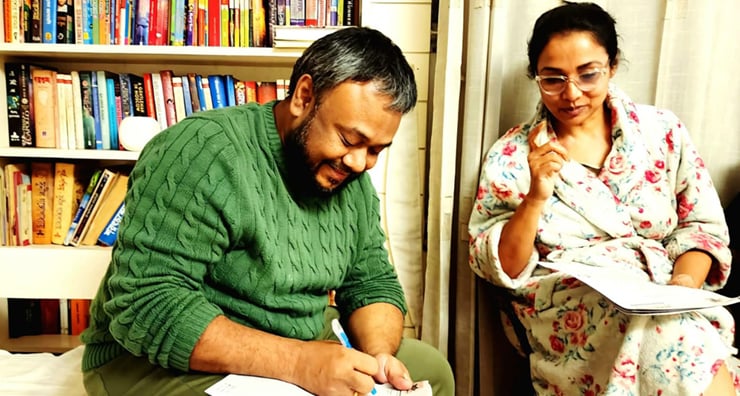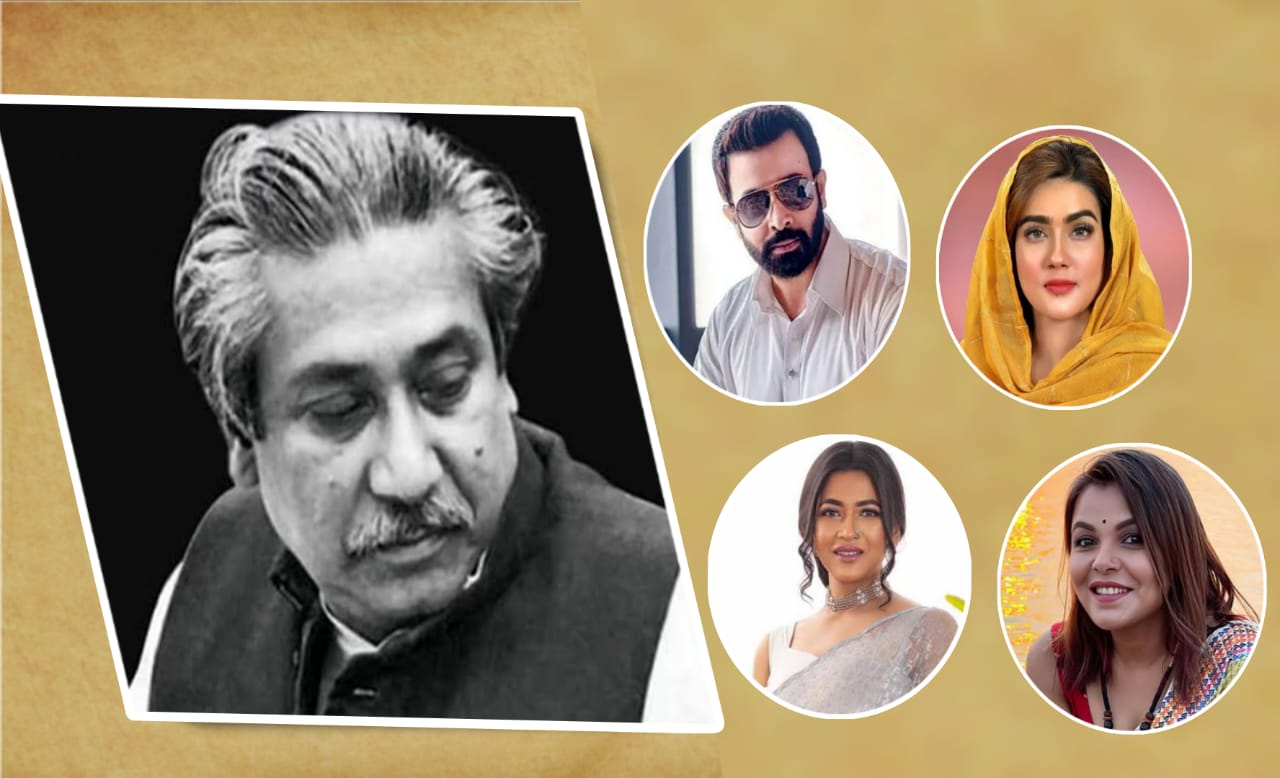জেলা পরিষদ : কাজটা কী
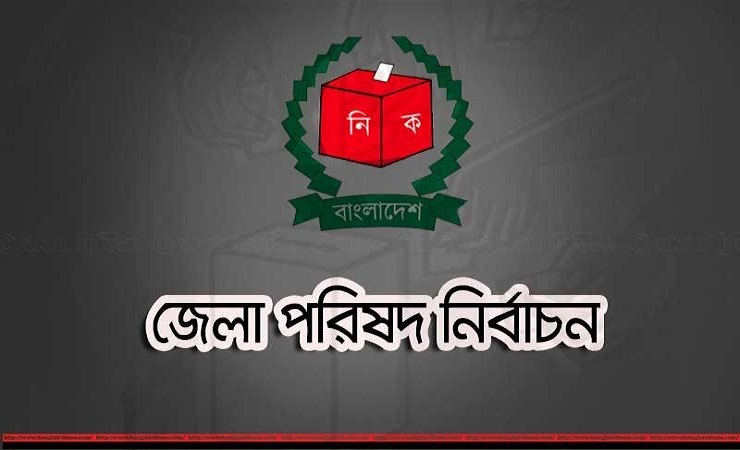
বাংলাদেশের রাজনীতিবিদদের কথাবার্তা আমি প্রায়ই বুঝি না। এরা কখন কি বলেন, কেন বলেনÑ সেটা আমরা আমজনতা তো দূরের কথা, তারা নিজেরাই কতটা বোঝেন, তা নিয়েও আমার সন্দেহ আছে। কেবল কথার ক্ষেত্রেই নয়, কাজের ক্ষেত্রেও তাদের অনেক আচরণ দুর্বোধ্য মনে হয়। আমার এই উপলব্ধির প্রমাণ যেন আরও একবার মিলল সদ্য শেষ হওয়া জেলা পরিষদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে।
নির্বাচন একটা হয়ে গেল, অথচ সে নির্বাচনে জনগণ নেই। প্রার্থী আছে, ভোটার আছে, কিন্তু সাধারণ মানুষ নেই। যে ভোটের মাধ্যমে জেলা পরিষদের নেতৃবৃন্দ নির্বাচিত হবেন, সেই ভোট দেওয়ার অধিকার জেলার আপামর মানুষের নেই। নির্বাচিত চেয়ারম্যান বা সদস্যরা কি কেবল, যারা তাদের ভোট দিয়েছেন সেই ইউপি বা উপজেলা চেয়ারম্যান মেম্বার কমিশনারদের উপর কর্তৃত্ব করবেন, নাকি পুরো জেলার মানুষের উপরই করবেন? তাহলে যিনি আমার জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হবেন, তাকে বেছে নিতে আমি কেন কোনো ভূমিকা রাখতে পারব না? এসব প্রশ্নের জবাব আমরা খুঁজব, তবে তার আগে বরং রাজনীতিবিদদের কথাবার্তার স্ববিরোধিতার বিষয়টা একটু বলে নিই।
বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী এই নির্বাচন বর্জন করেছে। সরকারের গৃহপালিত বিরোধীদল জাতীয় পার্টিও এতে অংশ নেয়নি। অংশ না নেওয়ার কারণ হিসাবে এরা সবাই বলেছে এই নির্বাচনের নৈতিক এবং আইনগত বৈধতার কথা। অর্থাৎ তাদের এই নির্বাচন বর্জন নিতান্তই হুজুগে বা আবেগের বশবর্তী হয়ে নয়। রীতিমতো যুক্তি দেখিয়ে, সাংবিধানিক অসংগতির কথা বলে বর্জন করেছে তারা এই নির্বাচন। কোথাও তারা কোনো প্রার্থীও দেয়নি। প্রার্থী দেয়নি, কিন্তু ভোটও কি দেয়নি? শুরুতেই বলে নিয়েছি, জেলা পরিষদ নির্বাচন সরাসরি জনগণের ভোটে হয়নি, হয়েছে পরোক্ষ ভোটে। অর্থাৎ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, মেম্বার, পৌরসভার চেয়ারম্যান, কাউন্সিলর; উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, কাউন্সিলর; সিটি করপোরেশন থাকলে তার মেয়র, কাউন্সিলরÑ এরাই ছিলেন ভোটার। এদের ভোটেই হয়েছে এই নির্বাচন।
এই যে চেয়ারম্যান, মেম্বার, কাউন্সিলর এদের মধ্যে কি বিএনপি, জামায়াত বা জাতীয় পার্টির কোনো নেতা-কর্মী নেই? তারাও কি দলীয় সিদ্ধান্ত মেনে ভোট বর্জন করেছেন? না, করেননি। তারা মহানন্দে ভোট দিয়েছেন। অনেকে টাকার বিনিময়ে দিয়েছেন, অনেকে আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থীকে ভোট দিয়ে বিজয়ী করে এক ধরনের আমোদ অনুভব করেছেন। একে কৌশলগত বিজয় বলেও দাবি করেছেন। এই যে কাজটা করেছেন তারা, প্রকাশ্যে ভোট দিয়েছেন, এটা কি তাদের দলের কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তের সঙ্গে সাংঘর্ষিক নয়? সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক দাবি করে বিএনপি জেলা পরিষদের নির্বাচনকে বর্জন করেছেন। এখন কি তাদের দলের সিদ্ধান্তের সঙ্গে সাংঘর্ষিক বিবেচনা করে তারা স্থানীয় পর্যায়ের ওই ভোট দেওয়া নেতা-কর্মীদের দল থেকে বহিষ্কার করবে? তা যে করবে না, এটা সকলেরই জানা।
এবারে আসি জেলা পরিষদ বিষয়ে। এ নির্বাচনটি হলো নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশন নির্বাচনের মাত্র ছয়দিনের মাথায়। দুটি নির্বাচনই হয়েছে শান্তিপূর্ণভাবে। যারা হেরে গেছেন, তাদেরও কেউ নির্বাচন নিয়ে কোনো অভিযোগ বা প্রশ্ন তোলেননি। এর অর্থ হচ্ছে, দুটি নির্বাচনই হয়েছে অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে। এই যে সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন করতে পারা এ নিয়ে নির্বাচন কমিশনের গর্বের শেষ নেই। এটি ছিল এই কমিশনের শেষ নির্বাচন। নারায়ণগঞ্জের নির্বাচন নিয়ে এর আগে অনেক কথা হয়েছে। তাই সেটা নিয়ে আর বলতে চাই না। তবে জেলা পরিষদ নির্বাচন নিয়ে নির্বাচন কমিশনের বাহাদুরিটা ঠিক বোধগম্য নয়। ৬১ জেলায় হওয়া এই নির্বাচনে মোট ভোটার ছিল ৬৩ হাজার ১৪৩ জন। এদের মধ্যে পুরুষ ভোটার ৪৮ হাজার ৩৪৩ জন। আর নারী ভোটার ১৪ হাজার ৮০০। পরোক্ষ ভোটই নারী-পুরুষের এই বৈষম্যের মূল কারণ। ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা, সিটি করপোরেশনে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে নারীর অনুপাত যে কত কম, সেটাই প্রতিফলিত হয়েছে এখানে।
গত কয়েক বছর ধরে তবুও সংরক্ষিত আসন থাকায় কিছুটা রক্ষা, নয়ত নারীর সংখ্যা আরও কম হতো। মাত্র ৬৩ হাজার ভোটারের এই নির্বাচনকে শান্তিপূর্ণ রাখতে বিভিন্ন নিরাপত্তা বাহিনীর প্রায় ২৩ হাজার সদস্যকে মোতায়েনের কথা প্রথমে বলা হয়। বিভিন্ন বাহিনী বলতে পুলিশ, আর্মড পুলিশ ব্যাটেলিয়ন, আনসার ও ভিডিপিকে বোঝানো হয়েছিল। পরে অবশ্য এর সঙ্গে বিজিবিও যোগ হয়। সব মিলিয়ে অবস্থাটা এমন দাঁড়ায় যে, কোনো কোনো কেন্দ্রের ভোটারের চেয়ে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যই বেশি হয়ে যায়। তাছাড়া এই যে ৬৩ হাজার ভোটার, এরা সবাই বিভিন্ন এলাকার জনপ্রতিনিধি, সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। এদের ভোটকে শান্তিপূর্ণ করতে এত বেশি নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যকে মোতায়েন কেন করতে হলো, সেটাই তো বিস্ময়কর। আর উল্লেখ করার মতো শেষ তথ্যটি হচ্ছে এই নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য কমিশনের ব্যয় হচ্ছে পাঁচ কোটি টাকারও বেশি।
এই যে বিপুল আয়োজনের নির্বাচন, এর নীট ফলটা কি? প্রতিটি জেলা পরিষদে একজন চেয়ারম্যান আর ২০ জন কাউন্সিলর অবশ্য পাওয়া গেছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছেÑ এদের দিয়ে আমরা করবটা কি? জাতীয় উন্নতির প্রশ্নে বর্তমানে কি এমন সংকট চলছিল, যা নিরসনে এই লোকগুলোর নির্বাচন অতীব জরুরি ছিল? কেউ কেউ হয়ত বলবেন, স্থানীয় সরকার পদ্ধতিকে পূর্ণতা দিতে এই নির্বাচন অপরিহার্য ছিল। সেটাই যদি হয়, তাহলে জেলা পরিষদ আইন প্রণয়নের পর গত ১৬টি বছর কি করেছে সরকার? ২০০০ সালে এই আইন করা হয়েছে, তারপর এই প্রথম হচ্ছে এর নির্বাচন।

নির্বাচন পদ্ধতি নিয়েও প্রশ্ন ওঠেছে। অনেকেই বলেছেন, যে পদ্ধতিতে এই নির্বাচন হলো, সেটা আমাদের সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। তাদের মতে, সংবিধানে নির্বাচনে জনগণের অংশগ্রহণকেই বোঝানো হয়েছে, পরোক্ষ নির্বাচনের কোনো অপশন নেই। এই প্রশ্ন তুলে এরই মধ্যে আদালতে তিনটি আবেদনও করা হয়েছে। সেসব অভিযোগ এখনো নিষ্পত্তির অপেক্ষায় রয়েছে। সর্বোচ্চ আদালতে বিচারাধীন থাকা অবস্থাতেই অনুষ্ঠিত হলো এই নির্বাচন। এখানে একটা হাইপোথেটিক্যাল প্রশ্ন কিন্তু করাই যায়। আচ্ছা, সুপ্রিম কোর্ট যদি শেষ পর্যন্ত ওই আবেদনকারীদের পক্ষেই রায় দেয়, তখন এই নির্বাচনের কি হবে। আদালত যদি তার রায়ে বলে, পরোক্ষ পদ্ধতিতে জেলা পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠান আসলেই সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক, তাহলে হয়ে যাওয়া এই নির্বাচনের কি হবে ভবিষ্যৎ? আইন প্রণয়নের পর যদি আপনি প্রথম নির্বাচনটি অনুষ্ঠানের জন্য ১৬টি বছরই অপেক্ষা করতে পারলেন, তাহলে সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ের জন্য আর কয়েকটা দিন অপেক্ষা করলে কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত?
লাখ টাকার একটা প্রশ্ন কিন্তু রয়েই গেছে। আসলে এই আলোচনাটিই আসা দরকার ছিল সকলের আগে। প্রশ্ন হচ্ছে, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান-কাউন্সিলরদের আসলে কাজটা কী? জেলা পরিষদের সদর দপ্তর হবে কোনো না কোনো জেলা শহরেই। সেখানে একটা করে সিটি করপোরেশন বা মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন রয়েছে। সেগুলোতে নির্বাচিত প্রতিনিধিও রয়েছেন। এই প্রতিনিধিরা সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত। জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান-কাউন্সিলররা কি তাহলে এসব এলাকার উন্নয়ন কাজ সমান্তরালভাবে করবেন? নাকি ইউপি, উপজেলা, মিউনিসিপ্যালটির কাজগুলোর দেখভাল করবেন? কিন্তু জনগণ দ্বারা সরাসরি নির্বাচিতরা কেন মানতে চাইবে পরোক্ষ ভোটে নির্বাচিতদের খবরদারি?
জেলা পরিষদের কর্মকর্তারা তো নির্বাচিত হয়ে গেছেন। এই নির্বাচিত কর্মকর্তাদের বেশ কয়েকজনের প্রতিক্রিয়া এরই মধ্যে দেখার সুযোগ হয়েছে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে। সেসব যত দেখেছি, তত বেশি হতাশ হয়েছি। কারণ, নির্বাচিতরা নিজেরাই জানেন না কী তাদের কাজ, কী তাদের দায়িত্ব। এ বড় অদ্ভুত এক ব্যাপার। অনেক দামে একজনের কাছে গরু বিক্রি করেছেন, তার হাতে গরুর দড়িও ধরিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু ক্রেতা এখনো দড়ির অপর প্রান্তে থাকা প্রাণীটি দেখেননি। সেটি কি ষাঁড়, গাভী নাকি বলদ তাও জানেন না। সেটি কি দুধ দেয়, নাকি কেবলই গুতায়, সে সম্পর্কেও কোনো ধারণা নেই।
জেলা পরিষদের যারা চেয়ারম্যান নির্বাচিত হলেন, তাদের পদমর্যাদাটাই বা কেমন? তারা কার উপরে, কার নিচে? জেলার ডিসিগণ কি এদের কথা অনুযায়ী কাজ করবেন, নাকি এরাই গিয়ে ডিসি অফিসে বসে থাকবেন কোনো কাজের ধরনা দিতে? সরকারের একটা ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্স আছে। তাতে সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তাদের তুলনামূলক অবস্থানের একটা বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। দু-তিনবার সেখানে নজর বুলালাম। জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের নামটাই সেখানে নেই। তাহলে তাদের অবস্থান কী জাতীয় সংসদের সদস্যদের উপরে নাকি নিচে? কেউ কেউ বলছেন, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানরা নাকি উপমন্ত্রীর মর্যাদা চাচ্ছেন। ঢাকা মহানগরীতে দুটি সিটি করপোরেশন, এর মেয়ররা প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদার। ঢাকা জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচনে এই দুই মেয়রও ভোট দিয়েছেন। দুই প্রতিমন্ত্রী ভোট দিয়ে যাকে নির্বাচিত করলেন, তিনি কি করে উপমন্ত্রীর মর্যাদার হন? ঢাকার দুই মেয়র প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদার হলেও নারায়ণগঞ্জের মেয়র কিন্তু উপমন্ত্রীর মর্যাদার। তাহলে ঢাকা জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের পদমর্যাদা কি নারায়ণগঞ্জের চেয়ারম্যানের চেয়ে বেশি হবে? জটিল সব প্রশ্ন। কিন্তু উত্তর দেওয়ার কাউকে তো খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।
উত্তর পেতে কিংবা নতুন নির্বাচিতদের সম্ভাব্য কাজকর্ম বা দায়িত্ব সম্পর্কে ধারণা পেতে ২০০০ সালে করা জেলা পরিষদ আইনটিতে এক চোখ বুলালাম। সত্যি কথা বলতে কি, খুব বেশি কিছু যে বুঝলাম তা বলা যাবে না। যতটুকু বুঝলাম, এই যে ১৫ জন সদস্য নির্বাচিত হলো, তাদের কাজের জন্য পুরো জেলাটিকে ১৫টি ওয়ার্ডে ভাগ করা হবে। এ পর্যন্ত কোনো জেলাকেই এরকম ওয়ার্ডে ভাগ করা হয়েছে কী? না, হয়নি। তাহলে তারা কাজটা শুরু করবেন কোথা থেকে? আর কাজের যে ফিরিস্তি পেলাম, তা তো আমাদের চলমান পদ্ধতির সঙ্গে আরও বেশি সাংঘর্ষিক। সেসব কাজ তো জেলা প্রশাসন, জেলা পর্যায়ের সরকারের বিভিন্ন বিভাগ এখনই করে থাকে। তাহলে জেলা পরিষদ করবেটা কী?
তাহলে এই পুরো বিষয়টিই কি নিছক রাজনৈতিক? দলে যারা এরই মধ্যে নিজেদের বড় নেতা মনে করছেন, অথচ সেই অনুপাতে প্রাপ্তি কিছু কম হয়ে গেছে বলে মনে করছেন, তাদেরকে আরও কিছু পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করতেই এই আয়োজন? এই ধারণাকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। হাতের সামনে উদাহরণ তো রয়েছেই। যেমন ধরা যাক, নারায়ণগঞ্জ সিটি নির্বাচনের কথাই। সেখানে জোরালো প্রার্থী ছিলেন আনোয়ার হোসেন। এলাকার প্রতাপশালী এমপি শামীম ওসমান তাকে সমর্থন দিলেন। কিন্তু শেখ হাসিনা তাকে পাল্টে প্রার্থী করলেন ডা. সেলিনা হায়াৎ আইভীকে। নিজের প্রার্থিতা বাতিল হয়ে যাওয়ার পর রীতিমতো অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলেন আনোয়ার হোসেন। এরপর তাকে যখন জেলা পরিষদে মনোনয়ন দেওয়া হলো এবং বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিতও করা হলো, অসুখ ভালো হয়ে গেল তার! বিভিন্ন জেলায় এরকম আরও অনেক আনোয়ার হোসেনের কথা মাথায় রেখেই কি তাহলে এই নির্বাচন?
আন্তরিকভাবেই কামনা করি, আমার এই চিন্তা মিথ্যা প্রমাণিত হোক। আসলেই কায়েম হোক দেশের সকল স্তরে স্থানীয় সরকার পদ্ধতি। সরকার পৌঁছে যাক মানুষের দরজার কাছে।

মাসুদ কামাল : জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ও লেখক
ঢাকাটাইমস/৩১ডিসেম্বর/এমকে/টিএমএইচ
 ঢাকা টাইমস অনলাইন এর সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিডটি ফলো করুন
ঢাকা টাইমস অনলাইন এর সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিডটি ফলো করুন
মন্তব্য করুন