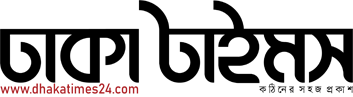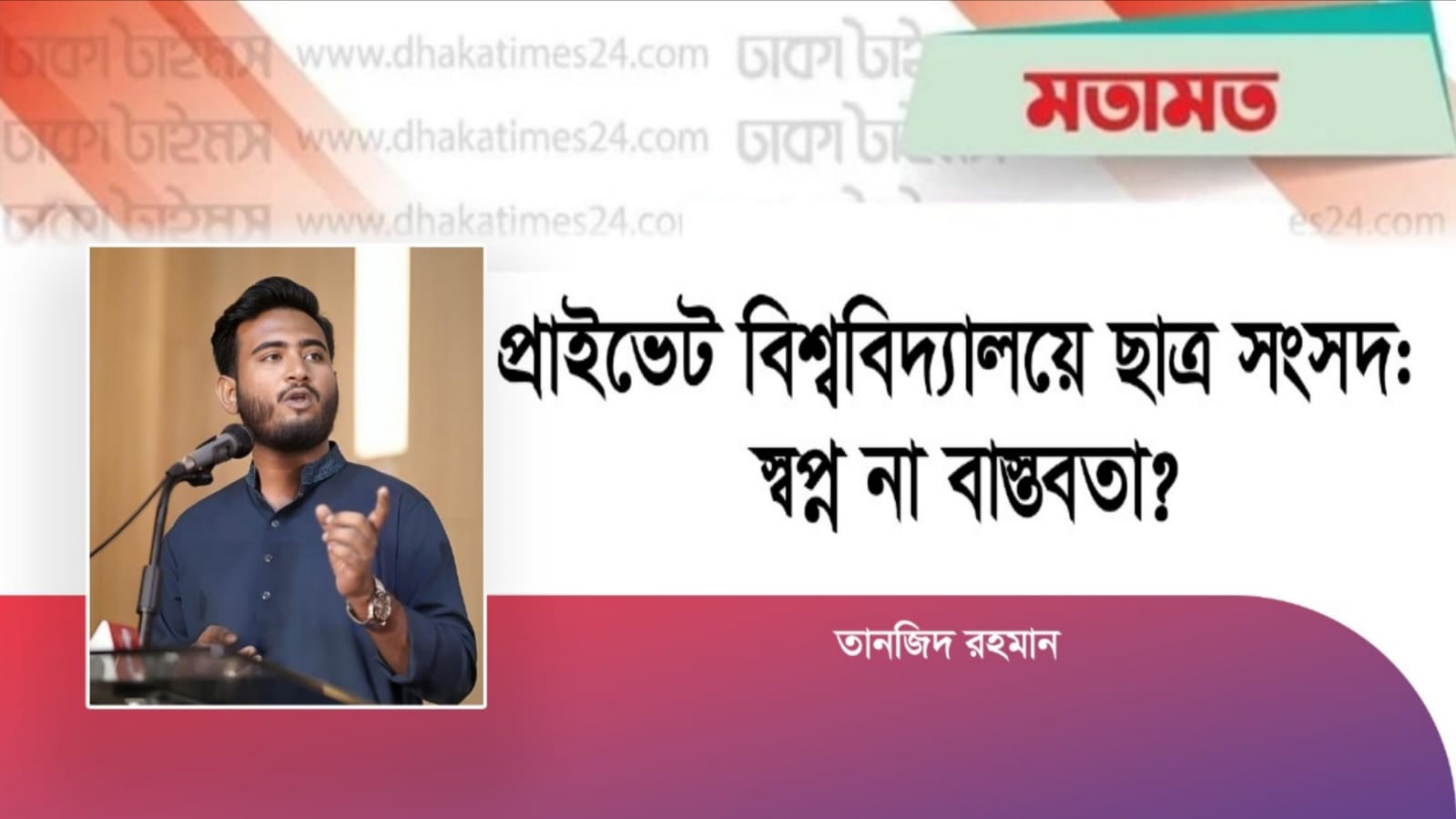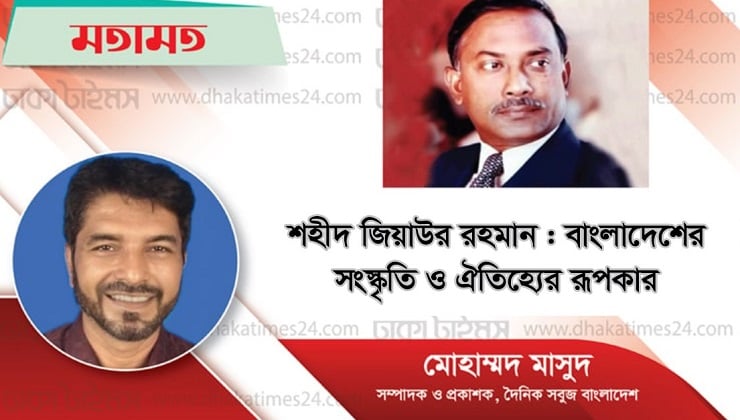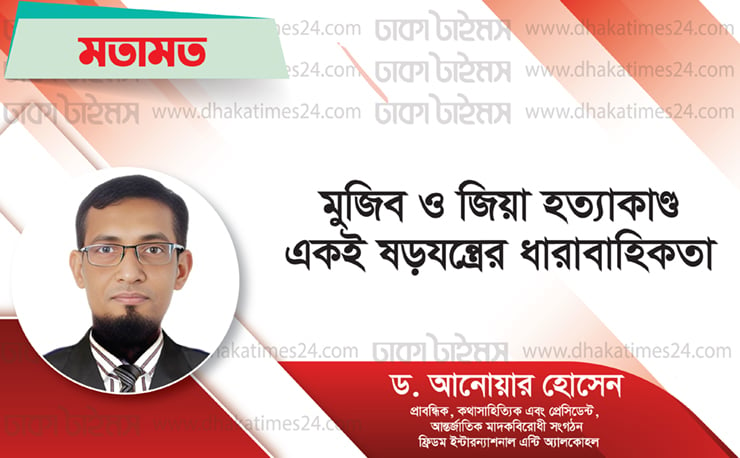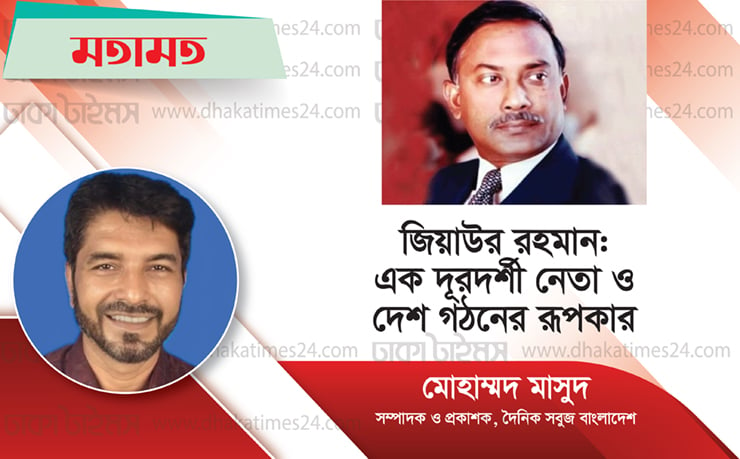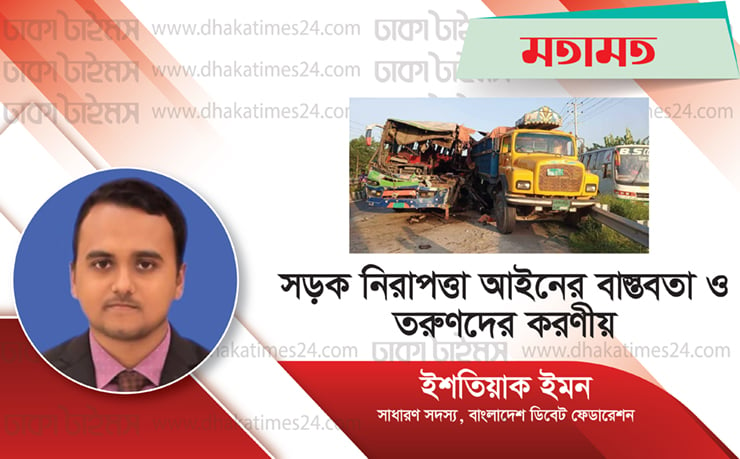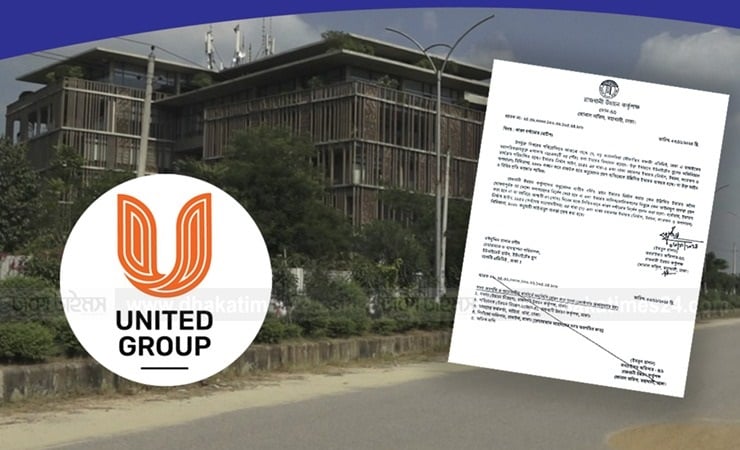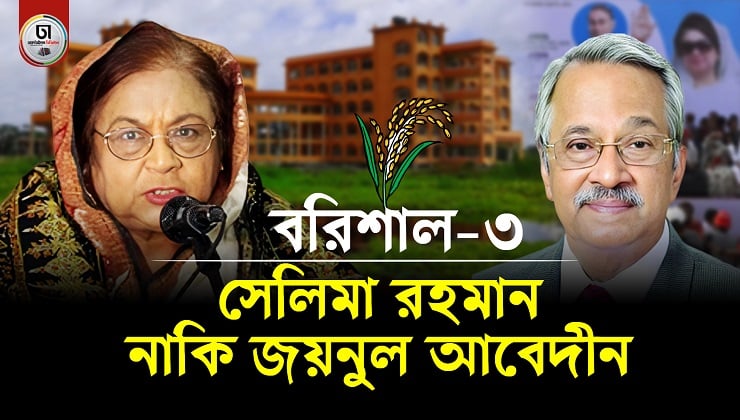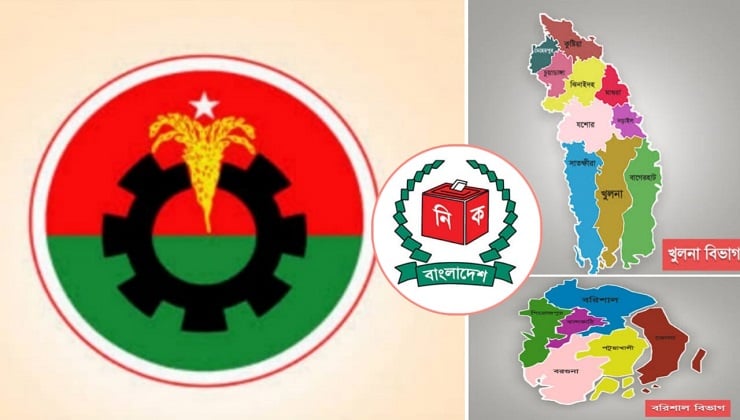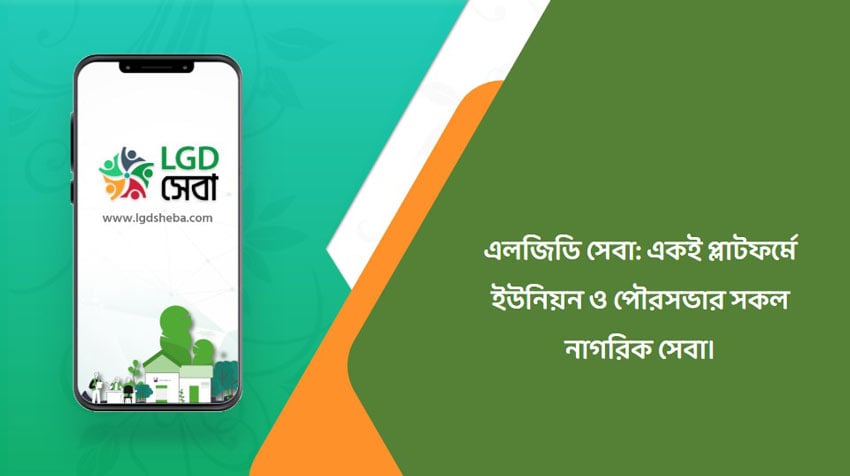রাষ্ট্রের স্তম্ভ এবং আমলাতন্ত্রের প্যাঁচ

সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী আনা হয়েছিল সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের অপসারণ ক্ষমতা সংসদের হাতে ন্যস্ত করতে। পরে তা অবৈধ ঘোষণা করে উচ্চ আদালত। এ রায়ের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষ আপিল করে। তা ৩ জুলাই খারিজ করে দিয়েছেন আপিল বিভাগ।
রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ তিনটি স্তম্ভ আইন বিভাগ, বিচার বিভাগ ও শাসন বিভাগ। এগুলোর ভারসাম্যের মাধ্যমেই নিশ্চিত হয় সুশাসন। দূরত্ব তৈরি হলে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে সব ক্ষেত্রেই। এ দেশে কিছুটা দেখাও যাচ্ছে। সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টের সামনে ভাস্কর্য স্থাপন এবং তা সরিয়ে নেওয়ার উপরিতলে হেফাজতের দাবির বিষয়টি এলেও নেপথ্যে সুপ্রিম কোর্টের সঙ্গে নির্বাহী বিভাগের শীতল সম্পর্কের দিকেও ইঙ্গিত দিচ্ছেন সংশ্লিষ্টরা। ঝি এবং বউ নিয়ে শিক্ষাবিষয়ক বাগধারা ধার করে কেউ কেউ আরো বাড়তি কিছু খুঁজে পাচ্ছেন থেমেসিসের স্থান বদলে। লেডি জাস্টিসকে সাধারণের দৃষ্টি সীমার একটু বাইরে নিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নির্বাহী বিভাগের সঙ্গে বিচার বিভাগের দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা দ্বন্দ্বকেও একটু আড়াল করার চেষ্টা চোখে পড়ে।
বর্তমান প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহা দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই বিচার বিভাগের স্বাধীনতার প্রশ্নে বেশ উচ্চ কণ্ঠ। বরাবরই তিনি অভিযোগ করছেন বিচার বিভাগ যে স্বাধীনতা ভোগ করছে তা আরো প্রসারিত করার সব সুযোগ থাকা সত্ত্বেও নির্বাহী বিভাগের অসহযোগিতায় তা হয়ে উঠছে না। প্রধান বিচারপতি যে কয়েকটি বিষয়ে বারবার প্রকাশ্যে সরকারের প্রতি অসহযোগিতার কথা বলছেন তার মধ্যে বিচার বিভাগ পৃথককরণে মাসদার হোসেন মামলার আলোকে বিচার বিভাগের নিজস্ব সচিবালয় প্রতিষ্ঠা, বিচারকদের শৃঙ্খলাবিধি অর্থাৎ তার নিয়োগ, বদলি ইত্যাদি বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টকে দায়িত্ব দিয়ে গেজেট প্রকাশ। মামলা বিচারাধীন থাকায় কখনো সুপ্রিম কোর্টের পক্ষ থেকে বলা না হলেও সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনীর মাধ্যমে বিচারকদের পদচ্যুতির ক্ষমতা সংসদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া নিয়েও বিচার বিভাগে অসন্তোষ আছে।
বিচার বিভাগের এ ধরনের অসন্তোষ নতুন না হলেও তা নিয়ে সাধারণের মধ্যে কখনো এত কৌতূহল দেখা যায়নি। কারণ আগের কোনো প্রধান বিচারপতিকে এ নিয়ে প্রকাশ্যে খুব বেশি কথা বলতেও দেখা যায়নি। অন্য সময়ের চেয়ে বিচার বিভাগ নিয়ে বিচার বিভাগের প্রধান যে অনেক বেশি সোচ্চার তা নিয়ে আইনমন্ত্রী আনিসুল হকও প্রশ্ন তুলেছেন। আর এটা যে কেবল তার ব্যক্তিগত মত তা কিন্তু নয়, সরকারের ভেতরের অধিকাংশর মতেরই প্রতিফলন।
গত ৩০ এপ্রিল প্রধান বিচারপতি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানে অভিযোগ করেন দেশে আইনের শাসন নেই। প্রতিক্রিয়ায় আইনমন্ত্রী সরাসরি কিছু না বললেও পৃথিবীর অন্য কোনো দেশের প্রধান বিচারপতিকে এত কথা বলতে শোনেন না বলে মন্তব্য করেন। এর পরপরই প্রধান বিচারপতিও তার বক্তব্যের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করে বলেন, পৃথিবীর অন্য অনেক দেশের প্রধান বিচারপতিকে কথা বলতে হয় না কিন্তু তাকে বলতে হয় কারণ বাংলাদেশে এখনো আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা হয়নি।
প্রধান বিচারপতি যে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা নিয়ে কথা বলছেন সেটা সরকার যেভাবে দেখছেন তা তো একদিক। একটু অন্যভাবেও দেখার সুযোগ আছে। ভুললে চলবে না প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রের তিন অঙ্গের একটির প্রধান। বিচার বিভাগের প্রধান হিসেবে তিনি একই সঙ্গে বিচারিক এবং বিচার প্রশাসনের প্রধান। একটু ভালো করে খেয়াল করে তার কথা শুনলে বোঝা যায় প্রধান বিচারপতি এস কে সিনহার প্রায় সব কথাই বিচার প্রশাসন নিয়ে। এক্ষেত্রে প্রধান বিচারপতি বিচার বিভাগের মনের কথা খুলে বলাই ভালো। কেননা শেষ পর্যন্ত জনগণের প্রতি বিচার বিভাগের দায়বদ্ধতা এতে প্রকাশ পায়।
আবার প্রধান বিচারপতির সঙ্গে আমরা পুরোপুরি একমত হতে পারব না যে, দেশে ন্যায়বিচার নেই। তবে অবশ্যই বিচারের পরিবেশ, বিচার প্রশাসনের আরো বেশি স্বাধীনতা নিশ্চিত করার সাংবিধানিক দায়িত্ব সরকার বরাবরই ঢিলেতালের বাস্তবায়ন করতে চায়। আমাদের মতো রাষ্ট্র যেখানে প্রাতিষ্ঠানিক গণতন্ত্র তার নির্মাণ পর্যায়ে আছে, সেখানে নির্বাহী বিভাগ বিচার বিভাগকে পুরো স্বাধীন দেখতে চায় না। কেননা প্রশাসন বিশেষ করে আমলাতন্ত্র তাতে স্বস্তিবোধ করে না। এটা ক্ষমতার ধর্ম সে কোনো ধরনের জবাবদিহিতা পছন্দ করে না। সে আপনি যে বিভাগেই থাকুন না কেন। বিচারকদের শৃঙ্খলাবিধির গেজেট তাই আমলাতন্ত্রের অস্বস্তি আবার সেই একই কারণে বিচারকদের স্বস্তি নেই ষোড়শ সংশোধনীতে।
বাংলাদেশের সংবিধানের এখানেই বৈশিষ্ট্যম-িত যে সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর মধ্যেই রাষ্ট্রের তিন অঙ্গ নির্বাহী, আইন ও বিচার বিভাগ সম্পূর্ণ স্বাধীন হলেও একে অপরের মধ্যে একটা প্রয়োজনীয় সমন্বয় নিশ্চিত করেছে। প্রতিটি অঙ্গ স্বাধীন এবং অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এমন একটা জায়গায় যাওয়াই গণতন্ত্রের মূল লক্ষ্য। সেখানে আমরা পৌঁছে গেছি তা মনে করার সুযোগ নেই। বরং গণতন্ত্রকে যারা খুব দুর্বল মনে করছেন তাদের জন্য আশার কথা হওয়া উচিত যে, বিচার এবং নির্বাহী বিভাগের মধ্যে দ্বন্দ্ব। কেননা আমরা বিশ্বাস করতে চাই এই দ্বন্দ্ব পেছনের দিকে যাওয়ার নয় বরং সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য।এপ্রিল মাসে দুই বিভাগের দ্বন্দ্ব আরো বেশি প্রকট হলো ২৫ এপ্রিল প্রধান বিচারপতি সব সরকারের প্রতিই দোষারোপ করলেন যে কোনো সরকারই বিচার বিভাগ স্বাধীন হোক তা চায়। অবশ্য এজন্য তিনি আমলাতন্ত্রকেই দায়ী করেন। দুদিন পর ২৭ এপ্রিল বিচারকদের জন্য নতুন আবাস উদ্বোধন করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বললেন, পারস্পরিক দোষারোপের পথে না হেঁটে সংসদ, বিচার বিভাগ ও নির্বাহী বিভাগকে সবঝোতার মাধ্যমে আরও সচেতনতার সঙ্গে কাজ করতে হবে।
প্রধানমন্ত্রী বলেন, ক্ষমতা কারও কম নয়। কে কাকে সম্মান করবে, কে কার সিদ্ধান্ত নাকচ করবে এই দ্বন্দ্বে যদি আমরা যাই তাহলে একটি রাষ্ট্র সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে না। একই মঞ্চে প্রধান বিচারপতি এস কে সিনহা বলেন, একটি মহল সব সময় সরকার ও বিচার বিভাগের মধ্যে দূরত্ব তৈরির অপচেষ্টায় লিপ্ত। এ রকম ভুল বোঝাবুঝির কারণে জনগণের মধ্যে ভুল বার্তা চলে যায়। দুজনের কথার সূত্র ধরে আমরা বলতে পারি দ্বন্দ্ব যে একটা তৈরি হয়েছে তার স্বীকৃতি পাওয়া যায়।
এই দ্বন্দ্বকে আমি পজেটিভ হিসেবে দেখছি। কারণ এটা গণতন্ত্রের চর্চার একটা ভালো লক্ষণ। কিন্তু আবার অন্যদিকে এটা দীর্ঘস্থায়ী হয়ে যাওয়া গণতন্ত্র, মানুষ এবং সর্বোপরি দেশের জন্য অশুভ লক্ষণ। তাই এ অবস্থা থেকে বের হয়ে আসার জন্য পথ খুঁজতে হবে। সেক্ষেত্রে আমাদের মনে হয়, নির্বাহী বিভাগকেই এগিয়ে আসতে হবে। অনেক বিষয়ে বিচার বিভাগের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হয়েছে। বিচার বিভাগ পৃথককরণের শর্ত হিসেবে বিচারকদের শৃঙ্খলা বিধি এবং আলাদা সচিবালয় দ্রুত স্থাপন করার মধ্য দিয়ে নির্বাহী বিভাগ উদ্যোগ নিতে পারে।আগেও আমরা দেখেছি মাসদার হোসেন মামলার রায় বাস্তবায়নে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর সরকার সুপ্রিম কোর্টের কাছে সময় নিয়েছে। বিচারকদের শৃঙ্খলাবিধির গেজেট প্রকাশ নিয়ে এই তৎপরতা দেখা যাচ্ছে। তাহলে আমরা দেখব বিচার বিভাগের ক্ষোভ অনেক কমে আসবে। বাকি যেসব বিষয়ে দূরত্ব দেখা যাচ্ছে তা ধীরে ধীরে কমিয়ে আনা সম্ভব হবে।
আদালত কোনো কোনো সময় সংবিধানের সংশোধনী বা প্রণীত আইন বাতিল করে দেয়। এ নিয়ে আইন বিভাগ ও নির্বাহী বিভাগ প্রায়ই মনোক্ষুন্ন হয়। কিন্তু একটি বিষয় মনে রাখতে হবে, আদালত কেবল তখনই একটি আইন বাতিল করতে পারে যখন তা সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। পাল্টা প্রশ্নটাও তো বিবেচনায় নেওয়া দরকার। সরকারের বিশাল আমলাতন্ত্র এবং মহান জাতীয় সংসদে সদস্যদের চোখকে কিভাবে ফাঁকি দিয়ে সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক আইন তৈরি হয়?
সবশেষে একটা কথাই বলতে চাই। আইন তার নিজের গতিতে চলছেÑ সরকার এবং সরকারি দলই একথা সবসময় সব আমলে বলেন। কিন্তু আমরা এই দাবির পক্ষে প্রমাণ যতটা দেখতে পাই বিপরীতটাই বেশি চোখে পড়ে। আদালতের নির্দেশে ইটিভি বন্ধ করে দিতে বিএনপি সরকার কিংবা হালের মওদুদ আহমদের বাড়ি খালি করার নির্দেশ যে গতিতে বাস্তবায়ন হতে আমরা দেখি আদালতের অধিকাংশ নির্দেশই কিন্তু এতটা সুপারসনিক না। তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিলের নির্দেশের ক্ষেত্রে আদালতের নির্দেশ বাস্তবায়নের সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা বাস্তবায়নে সরকার যতটা আন্তরিক বিচারকদের শৃঙ্খলাবিধি প্রকাশে একই আন্তরিকতা দেখাতে পারলে হয়তো দুই বিভাগের দ্বন্দ্ব কোনো সুযোগ তৈরি হবে না।
নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের বিচারিক ক্ষমতা হারানো এবং সর্বশেষ ভ্রাম্যমাণ আদালতে হোঁচট খাওয়ায় আমলাতন্ত্র কোনোভাবেই চায় না বিচার বিভাগ পুরো স্বাধীন হোক। তবে সিদ্ধান্তটা নির্বাহী বিভাগকেই নিতে হবে। দেশের জনগণের জন্য তারা কেমন বিচার বিভাগ চান, সেই পথ তাদেরই দেখাতে হবে। কেননা আমলাতন্ত্র আদালতের নির্দেশ পালন করতে চাইবে না যতক্ষণ রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত তাদের বাধ্য করে।
এদিকে সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের অপসারণের ক্ষমতা সংসদের হাতে ন্যস্ত করে আনা সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী অবৈধ ঘোষণার রায় আপিল বিভাগ বহাল রাখায় হতাশ হয়েছেন অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম। ৩ জুলাই আপিল বিভাগের সিদ্ধান্তের পর পর তিনি গণমাধ্যমে জানিয়েছেন, আইন মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আলোচনা করে রিভিউর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিবেন। তবে তিনি ব্যক্তিগতভাবে মনে করেন, সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল পুনর্বহাল হয়নি, এখানে এক ধরনের শূন্যতা বিরাজ করছে।
সাংবিধানিক ও আইনি কাঠামোর মধ্যে আমরা সবার জন্য কল্যাণকর একটি সমাধান দেখতে চাই বিষয়টিতে।
জাহিদ হোসেন: জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক
 ঢাকা টাইমস অনলাইন এর সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিডটি ফলো করুন
ঢাকা টাইমস অনলাইন এর সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিডটি ফলো করুন
মন্তব্য করুন